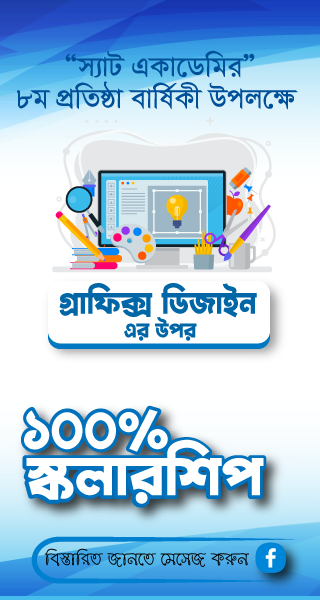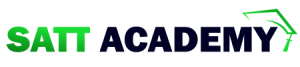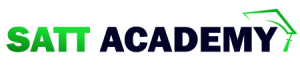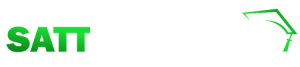- ওপরের ছবিগুলো ভালো করে দেখি। ছবিতে কী ঘটছে তা কয়েকটি শব্দে ছবির নিচের ঘরগুলোয় লিখি। ছবিতে যেরকম দেখছি, আমরাও সেরকম অনেক কাজ করি। আমরা প্রত্যেকে নিজের জীবনের এ রকম একটি বাস্তব চিত্রের কথা 'অপরের জন্য আমি' শিরোনামে গল্প আকারে লিখে সবার সামনে উপস্থাপন করি।
ছক ৩.১: অপরের জন্য আমি
|
প্রত্যেক প্রাণী যে-রূপে জন্মগ্রহণ করে সেরূপেই বেড়ে ওঠে, সেভাবেই জীবন পার করে। হাঁসের বাচ্চা হয় হাঁস আর ঘাসের বীজ থেকে জন্মায় ঘাস। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে বিষয়টা অন্যরকম। 'মানুষ' হিসেবে পরিচয় পাওয়ার জন্য তাকে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয়। এই মনুষ্যত্ব হলো কতকগুলো সদগুণের সমষ্টি। সেগুলোর মধ্যে একটি হলো মূল্যবোধ। আর যে মূল্যবোধের মাধ্যমে মানুষ ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিতের বিচার করে তার আলোকে আচরণ করতে পারে তাকে নৈতিক মূল্যবোধ বলে। আমরা ছবিতে এরকম কিছু নৈতিক মূল্যবোধের উদাহরণ দেখেছি। সত্যকামের গল্পে 'সত্যবাদিতা', রাম-লক্ষ্মণের গল্পে 'ভ্রাতৃপ্রেম', কর্ণের গল্পে 'গুরুজনে ভক্তি' ইত্যাদি নৈতিক মূল্যবোধগুলোর কথা জেনেছি। মানুষের ভেতরে এ রকম আরও অনেক নৈতিক মূল্যবোধ থাকে, যেমন: উদারতা, ক্ষমাশীলতা, দায়িত্ববোধ, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি।
- আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এ রকম অনেক নৈতিক মূল্যবোধ কাজ করে। আমার নিজের ভেতরে থাকা তিনটি নৈতিক মূল্যবোধের কথা লিখে 'আমার নৈতিক মূল্যবোধ' তালিকাটি সম্পূর্ণ করি।
ছক ৩.২: আমার নৈতিক মূল্যবোধ
১.
|
২.
|
৩.
|
- চলো, আমরা প্রত্যেকে সহপাঠীদের নৈতিক মূল্যবোধ এবং নিজের জানা আরও মূল্যবোধের নামের তালিকা লিখে 'আমাদের মূল্যবোধ' ছকটি পূরণ করি।
ছক ৩.৩: আমাদের মূল্যবোধ
|
|
হিন্দুধর্মেও এ রকম অনেক নৈতিক মূল্যবোধের গল্প রয়েছে। এখানে আমরা আত্মশ্রদ্ধা, ধর্মনিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং পিতামাতার প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে জানব।
আত্মশ্রদ্ধা
একজন ছাত্রের গণিতে ভীষণ ভয় ছিল। তাই সে পরীক্ষায় ভালো করত না। একদিন শিক্ষক তাকে ডেকে নিয়ে ছোট ছোট গাণিতিক সমস্যা দিলেন। অনেকগুলো সমস্যার সমাধান সে করে ফেলল। শিক্ষক তাতে খুশি হয়ে বললেন, তুমি তো ভালোই গণিত পারো! চাইলেই কিন্তু গণিতে আরও ভালো করতে পারো। শিক্ষকের উৎসাহে সে গণিতের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠল। শিক্ষকও তাকে মাঝে মাঝে গণিত দেখিয়ে দিতেন। অল্প দিনের মধ্যে ছাত্রের ভয় কেটে গেলা। সে দেখল, এইতো আমি পারছি! এতে নিজের প্রতি তার ভালো লাগা তৈরি হলো। এটাই হলো আত্মশ্রদ্ধাবোধ। ছাত্রটি ভাবল, তাহলে আর একটু চেষ্টা করি। এভাবে ছাত্রটি গণিতে পারদর্শী হয়ে উঠল। তার এই যে পারদর্শিতা, তা আত্মশ্রদ্ধারই ফলাফল। আসলে গণিতে ভালো করার দক্ষতা তার ভেতরেই ছিল। কিন্তু 'আমি পারি' নিজের প্রতি এই শ্রদ্ধাটুকু জাগিয়ে তুলতে শিক্ষকমহাশয় তাকে সাহায্য করেছেন। তবে আত্মশ্রদ্ধা জাগাতে যে সবসময়ে কারোর সাহায্য লাগবে, ব্যাপারটা এমনও নয়। আত্মশ্রদ্ধা জাগাতে হলে নিজের প্রকৃত পরিচয় জেনে নিজের শক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগানো প্রয়োজন।
'আত্মশ্রদ্ধা' কথাটির মানে নিজেকে শ্রদ্ধা করা। এর জন্য প্রয়োজন নিজের প্রতি ভালো ধারণা রাখা। প্রত্যেক মানুষেরই কিছু না কিছু সহজাত বিশেষ ক্ষমতা, কর্মকুশলতা ও বৈশিষ্ট্য থাকে। আত্মশ্রদ্ধা জাগাতে হলে নিজের এই সামর্থ্যগুলো স্পষ্ট করে জানতে হয়। সেইসঙ্গে নিজের সীমাবদ্ধতাগুলোও বুঝতে হয়। আত্মশ্রদ্ধাবান মানুষ সাময়িক ব্যর্থতা দিয়ে নিজের মহিমাকে খাটো করে দেখে না। অন্যের মতো নয় বলে নিজেকে কখনও সামান্য বলে মনে করে না। এমন মানুষ নিজেকে ভালোবাসে। গীতায় বলা হয়েছে-
উদ্ধরেৎ আত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।
(গীতা- ৬/৫)
সরলার্থ: নিজেই নিজেকে উদ্ধার করবে। নিজেকে কখনো অবসন্ন ভাববে না। তাহলে নিজেই নিজের বন্ধু হবে। বিপরীতে নিজে শত্রুতে পরিণত হবে।
অর্থাৎ, আত্মশ্রদ্ধার বলে নিজেকে উদ্ধার করতে হয়। কখনো নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হারাতে নেই। আত্মশ্রদ্ধাই মানুষের বন্ধু। আত্মশ্রদ্ধাহীনতাই মানুষের শত্রু। আত্ম-অবমাননা কখনও করতে নেই। আমি পাপী, আমি অধম, আমি পতিত, আমি অসহায়- এ রকম বলতে নেই বা মনে করতে নেই। আত্মশ্রদ্ধাবান আত্মশ্রদ্ধাকেই পরম অবলম্বন বলে মনে করেন। কুসঙ্গ, কুকথা ইত্যাদি থেকে নিজেকে সযত্নে দূরে রাখেন।
কেবল ব্যক্তি জীবনে নয়, জাতীয় জীবনেও আত্মশ্রদ্ধার প্রয়োজন আছে। নইলে একটি জাতি যথার্থ স্বাধীনতা পায় না। নিজ জাতির ইতিহাস জানতে হবে। নিজেদের সমষ্টিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে। জাতীয় জীবনদর্শন সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। এরই ওপরে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে। এভাবেই একটি আত্মশ্রদ্ধাবান জাতি সামনে এগিয়ে যায়।
আত্মশ্রদ্ধার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে রামায়ণে আমরা সীতাকে পাই। আমরা এখন সীতার কাহিনি জানব।
রাজা দশরথ বড় ছেলে রামকে রাজা করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু বাধ সাধেন কৈকেয়ী। তার কূটকৌশলে রামকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে যেতে হয়। সঙ্গে গেলেন স্ত্রী সীতা আর ভাই লক্ষ্মণ। তের বছর বনবাসে থাকার পর একদিন ছদ্মবেশে লঙ্কার রাজা রাবণ সীতার কাছে এলেন। সীতা তখন বনের কুটিরে একা ছিলেন। সীতা অতিথি সৎকারের আয়োজন করেন। রাবণ তখন নিজের পরিচয় দিয়ে সীতাকে বনবাস জীবন ছেড়ে তার সঙ্গে লঙ্কায় যাওয়ার প্রস্তাব দেন। সীতা ঘৃণাভরে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। রাবণ তখন সীতাকে জোর করে মায়ারথে তুলে নিয়ে নিজ রাজ্য লঙ্কায় চলে যায়।
রাবণ সীতাকে বশে আনার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করে। কিন্তু কোনোভাবেই না পেরে তাঁকে অশোকবনে রা- ক্ষসীদের মাঝে বন্দি করে রাখেন। এদিকে সীতাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন রাম। একদিন হনুমান লঙ্কা থেকে সীতার খবর আর একটা আংটি নিয়ে রামের কাছে আসেন। তারপর রাম আর লক্ষ্মণ লঙ্কায় উপস্থিত হন। রাম-রাবণের ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত রাবণ সবংশে নিহত হয়। হনুমান অশোকবন থেকে সীতাকে নিয়ে রামচন্দ্রের কাছে আসেন। কিন্তু রাম সীতাকে গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। অপমানিত সীতা আগুনের চিতায় প্রবেশ করলেন। বললেন, যদি আমি সতী হই এবং রামের প্রতি একনিষ্ঠ থাকি, তবে স্বয়ং অগ্নিদেব আমাকে রক্ষা করবেন। অগ্নিদেব স্বয়ং সীতাকে রক্ষা করেন। রামের কাছে সীতাকে গ্রহণ করার অনুরোধ করেন। রাম সীতাকে গ্রহণ করেন। তারপর রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ অযোধ্যায় ফিরে আসেন।
রামচন্দ্র রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। আনন্দেই কাটছিল দিন। এরই মধ্যে সীতা অন্তঃসত্ত্বা হন। রাম নিঃসন্দেহ হলেও তিনি জানতে পারেন যে, প্রজাদের মনে সীতার চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ আছে। তাই প্রজাদের সন্তুষ্টির জন্য রাম সীতাকে বনবাসে পাঠান। সীতা বাল্মীকি মুনির আশ্রমে আশ্রয় পান। সেখানে সীতার লব ও কুশ নামে যমজ ছেলের জন্ম হয়। বাল্মীকি তাদের নিজের রচিত রামায়ণ কণ্ঠস্থ করান। এদিকে রাজা রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। নিমন্ত্রিত বাল্মীকি মুনির সঙ্গে কুশ ও লব এই যজ্ঞে এসে রামায়ণ গান করেন। তাঁদের গান শুনে
রাম বাল্মীকি মুনির কাছে তাঁদের পরিচয় জানতে চাইলেন। বাল্মীকি মুনি বলেন, এঁরা তোমারই পুত্র।
বাল্মীকি মুনি লব ও কুশকে নিয়ে আশ্রমে ফিরে যান। সীতাকে পুনরায় গ্রহণ করার জন্য রাম বাল্মীকির কাছে সংবাদ পাঠান- সীতা যদি নিষ্পাপ হয়, সে যেন বাল্মীকির আদেশ নিয়ে আত্মশুদ্ধি করে এবং সকলের সামনে শপথ করে। বাল্মীকি এই প্রস্তাবে সম্মত হন। বাল্মীকি মুনির আদেশে সীতা লব ও কুশকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে আসেন। পরদিন সকলের সামনে সীতার শুদ্ধতার পরীক্ষা। কিন্তু তিনি নিজেকে আর অপমানিত হতে দিতে রাজি নন। আত্মশ্রদ্ধাশীল সীতা সর্বসমক্ষে বললেন, আমি যদি সচ্চরিত্রের অধিকারী এবং রাম ভিন্ন অন্য কাউকে মনে মনে চিন্তা না করে থাকি, তবে ধরিত্রী যেন বিদীর্ণ হয়ে আমাকে আশ্রয় দেন। তখন মাটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। মাটির নিচ থেকে নাগবাহিত এক আশ্চর্য রথে দেবী বসুমতী উঠে আসেন। তিনি সীতাকে দুহাতে ধরে সিংহাসনে বসান। তারপর সীতাকে নিয়ে তিনি পাতালে প্রবেশ করেন। সীতা পাতালে প্রবেশ করলে রাজা রামচন্দ্রসহ প্রজারা শোকে হাহাকার করতে থাকেন।
এই কাহিনিতে আমরা দেখতে পাই, সীতা রামের প্রতি একনিষ্ঠ থাকার পরও বারবার তাঁকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে, পরীক্ষা দিতে হয়েছে, এমনকি শাস্তিও পেতে হয়েছে। সেখানে আমরা তাঁর সহনশীলতা আর ধৈর্যশী- লতার পরিচয় পেয়েছি। শেষ পর্যন্ত যখন তিনি আর অপমান সহ্য করতে পারলেন না, তখন তিনি আত্মশ্রদ্ধার পরিচয় দিলেন। নিজের প্রতি সম্মানবোধ থেকে তিনি অসম্মানজনক পরিস্থিতি থেকে সরে গেলেন।
ধর্মনিষ্ঠা
যা আমাদের কল্যাণের পথে ধরে রাখে তাই ধর্ম। আর 'ধর্মনিষ্ঠা' কথাটির মানে ধর্মের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ, গভীর আস্থা, অটল বিশ্বাস। ধর্মনিষ্ঠ মানুষ সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের চেতনা এবং বিশ্বাসকে হৃদয়ে ধারণ করে সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও পবিত্র জীবন-যাপন করে। আমরা কেন ধর্ম পালন করি, সে সম্পর্কে হিন্দুধর্মে বলা হয়েছে: 'আত্মমোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ।'- নিজের চিরমুক্তি, আর জগতের কল্যাণসাধনের জন্য। ধর্মনিষ্ঠা সবরকমের নৈতিক মূল্যবোধের সমষ্টি। যা নৈতিক তাই ধর্ম, যা অনৈতিক তা অধর্ম। ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিকে ধার্মিক বলা হয়।
ধার্মিক ব্যক্তি জগতে সাময়িকভাবে দুঃখভোগ করলেও পরিণামে শান্তি পান। এখানে একজন ধর্মনিষ্ঠ রাজার উপাখ্যান জানব।
অতি প্রাচীনকালে কোশল নামে একটি জনপদ ছিল। সেখানে হরিশ্চন্দ্র নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি প্রজাদের খুব ভালোবা- সতেন। ধর্মনিষ্ঠা, সত্য- বাদিত্য, দান, ধ্যান ও ন্যায়বিচারের জন্য তিনি ছিলেন বিখ্যাত। তাঁর কাছে যে যা চাইত তাই পেত। এই কারণে তিনি দানবীর হিসেবে খ্যাত হন। তাঁর সুনাম স্বর্গ ও মর্ত্যে ছড়িয়ে পড়ে। একদিন ইন্দ্রের সভায়, বশিষ্ট মুনির মুখে ঋষি বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের দানের সুখ্যাতি শুনলেন। ঋষির ইচ্ছা হলো, হরি- শ্চন্দ্র কেমন দানবীর, তা পরীক্ষা করে দেখবেন।
এদিকে দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় পাঁচজন অব্ন্স- রার নাচের তালভঙ্গ হয়। দেবরাজ ইন্দ্র রেগে গিয়ে তাদের অভিশাপ দেন, তোমরা বিশ্বামিত্রের তপোবনে বন্দিনী হয়ে থাকবে। তখন অব্দরাগণ হাতজোড় করে দেবরাজের কাছে তাদের মুক্তির উপায় জানতে চান। দেবরাজ ইন্দ্র বললেন, রাজা হরিশ্চন্দ্রের হাতে তোমাদের মুক্তি হবে। তারা মানুষরূপে বিশ্বামিত্রের তপোবনে বাস করতে থাকে। মানুষরূপী এই অপ্সরা প্রতিদিন তপোবনে ফুল তুলতে গিয়ে গাছের ডালপালা ভেঙে ফেলত। ঋষি বিশ্বা- মিত্র এই ঘটনায় ভীষণ রেগে পাঁচ কন্যাকে গাছের ডালে বেঁধে রাখেন। একদিন রাজা হরিশ্চন্দ্র শিকারের জন্য তপোবনে আসেন। তাঁকে দেখে বন্দী অপ্সরারা আর্তনাদ করতে লাগল। রাজা হরিশ্চন্দ্র তাদের বন্ধনমুক্ত করে দিলেন। তারা মুক্ত হয়ে স্বর্গে চলে গেল।
এভাবে কিছুদিন কাটল। একদিন ফুল তোলার সময়ে একটি কালসাপ রোহিতাশ্বকে দংশন করল। সেখানেই রোহিতাশ্বের মৃত্যু হয়। মৃত পুত্রকে দেখে শৈব্যার জীবনে অন্ধকার নেমে এল। যার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি সমস্ত দুঃখকষ্ট ভুলে ছিলেন, সেই স্নেহের পুত্রও আজ চলে গেল। তিনি পুত্রশোকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। বলতে লাগলেন, কোথায়, কোথায় রাজা হরিশ্চন্দ্র। একবার এসে দেখে যাও তোমার সন্তানের মৃতদেহ। মরা ছেলেকে কোলে নিয়ে শৈব্যা গেলেন শ্মশানঘাটে।
সেদিন ছিল ভয়ানক দুর্যোগ। ঘোর অন্ধকার রাত। আকাশ মেঘে ঢাকা। ঘাটের কড়ি আদায় করার জন্য হরিশ্চন্দ্র শ্মশানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শৈব্যা মৃত পুত্রকে নিয়ে শ্মশানে উপস্থিত হলেন। হরিশ্চন্দ্র তাঁকে বললেন, ঘাটের কড়ি পঞ্চাশ কাহন না পেলে আমি মড়া পোড়াতে পারবো না। তুমি অন্য ঘাটে চলে যাও। শৈব্যা অপরের কেনা দাসী, তিনি পয়সা কোথায় পাবেন! মনের দুঃখে তিনি হরিশ্চন্দ্রের নাম ধরে কাঁদতে লাগলেন। এই সময়ে একবার বিদ্যুৎ চমকাল। সেই আলোতে হরিশ্চন্দ্র শৈব্যা ও মৃত পুত্র রোহিতাশ্বকে চিনতে পেরে কেঁদে উঠলেন। শৈব্যাও ডোমের পোশাক পরা রাজাকে চিনে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। মৃত পুত্র রোহিতাশ্বকে নিয়ে দুজনেই অঝর নয়নে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁরা দুজনেই বললেন, হে প্রভু আমরা সর্বস্ব দান করেছি। বিনিময়ে আজ আমাদের এই দিন দেখালে। তাই এই জীবন আমরা আর রাখব না। এই পুত্রের চিতায় আমরা দুজন প্রাণত্যাগ করব। তাই চন্দনকাঠের চিতা সাজিয়ে তাতে মৃত পুত্র রোহিতাশ্বকে রাখেন। দুই পাশে পিতা-মাতা শুয়ে পড়লেন। এবার চিতাতে আগুন দিতে যাবেন, এমন সময় স্বয়ং ধর্মরাজ সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে রাজন! ধর্ম ও সত্যের প্রতি তোমার অনুরাগে দেবতারাও তুষ্ট হয়েছেন। তুমি প্রকৃতই ধার্মিক ও সত্যবাদী। ধর্মরাজ রোহিতাশ্বের গায়ে হাত বোলাতে সে বেঁচে উঠল'। বিশ্বামিত্রও তখন সেখানে এসে বললেন, 'হরিশ্চন্দ্র, তোমার পরীক্ষা শেষ হয়েছে। তুমি সত্যই দানবীর। ধন্য তোমার জীবন। তোমার এই দান ও ত্যাগের মহিমা স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে। তোমার রাজ্য তুমি ফিরিয়ে নাও। রাজ্যে ফিরে গিয়ে স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে রাজ্যসুখ ভোগ করো এবং প্রজাদের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করো'।
- এসো আমরা প্রত্যেকে তিনটি পয়েন্টে 'ধর্মনিষ্ঠার বৈশিষ্ট্য' লিখি।
ছক ৩.৫: ধর্মনিষ্ঠার বৈশিষ্ট্য
১.
|
২.
|
৩.
|
- ধর্মনিষ্ঠার কারণে আজও রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনি সকলের মনে জায়গা করে আছে। তিনি রাজ্যসুখ, স্ত্রী-পুত্র সব ত্যাগ করেও ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত হননি। ধর্মনিষ্ঠার গুণে তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।
অধ্যবসায়
জীবনে চলার পথে আছে বাধা, আছে বিঘ্ন। এসব বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করে কোনো কাজে সাফল্য লাভের জন্য বারবার চেষ্টা করার নামই অধ্যবসায়। চেষ্টা, উদ্যোগ, আন্তরিকতা, পরিশ্রম, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, একাগ্রতা ইত্যাদি গুণের সমন্বয়ে অধ্যবসায় নামক নৈতিক গুণটি গড়ে ওঠে। পৃথিবীতে যা কিছু মহৎ, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু কল্যাণকর সবই অধ্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। তাই মানব সভ্যতার অগ্রগতির চাবিকাঠি হলো অধ্যবসায়। অধ্যবসায়ের গুণেই মানুষ বড় হয়। অসাধ্য সাধন করতে পারে। কবি কালীপ্রসন্ন ঘোষ বলেছেন।
পাঁচজনে পারে যাহা,
তুমিও পারিবে তাহা
পার কিনা পার কর যতন আবার
একবার না পারিলে দেখ শতবার।
অধ্যবসায়ের গুণে মানুষ কেমন করে অসাধ্যকে সাধন করে তা এখানে আমরা বোপদেব গোস্বামীর অধ্যবসায়ের গল্পের মাধ্যমে জানব।
প্রায় হাজার বছর আগেকার কথা। তখনকার দিনে প্রাচীনভারতে বিদ্যালয়কে টোল বলা হতো। মহারাষ্ট্রের অধিবাসী বোপদেব গোস্বামী টোলে পড়ালেখা করতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন ক্লাসের সবচেয়ে অমনোযোগী ছাত্র। পণ্ডিত মহাশয় ক্লাসে ব্যাকরণের যেসব সূত্র শেখাতেন, বোপদেব সেসব কিছুই বুঝতে পারতেন না। মনেও রাখতে পারতেন না। এ কারণে তিনি প্রতিনিয়ত টোলে অপমানিত হতেন। পণ্ডিত মহাশয় তাঁর মূর্খতায় খুবই বিরক্ত ছিলেন। তিনি রেগে গিয়ে বোপদেবকে বলতেন, এমন আপদ টোলে আসার চেয়ে টোল বন্ধ হয়ে যাওয়া বরং ভালো। একদিন পণ্ডিত মহাশয় বোপদেবকে টোল থেকে বের করে দেন। বলে দেন, সে যেন আর টোলে না আসে। মনে একরাশ দুঃখ নিয়ে মাথা নিচু করে টোল থেকে বেরিয়ে যান বোপদেব। টোল থেকে বিতাড়িত হওয়ার কারণে হতাশা ঘিরে ধরে তাঁকে। তিনি ভাবতে থাকেন, আমি সত্যিই খুব খারাপ ছাত্র। আমার বি- দ্যাবুদ্ধি কিছুই নেই। আমাকে দিয়ে আর লেখাপড়া হবে না। কিন্তু আমিতো ব্যাকরণের সব সূত্র মনে রাখতে চাই। ক্লাসের পড়া বুঝতে চাই। অথচ কিছুতেই মনে থাকে না! কিছুই বুঝি না। মনের দুঃখে বোপদেব বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান। একদিন তাঁর খুব পিপাসা পেয়েছিল। তিনি একটি সানবাঁধানো পুকুরঘাটে যান। জলপান শেষে তিনি পুকুরের ঘাটে বসে থাকেন। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল ঘাটের পাথরের উপর একটি গোল গর্ত। পুকুরের সানবাঁধানো ঘাটের পাথরগুলো সব ঠিকঠাকই আছে। শুধু একটি নির্দিষ্ট জায়গাতেই গোল চাকতির মতো ঐ গর্ত। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল, শক্ত পাথরের গায়ে কেমন করে এ রকম গর্ত হলো? মনে মনে তিনি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে লাগলেন। এমন সময়ে একজন মহিলা ঐ পুকুর-ঘাটে এল। তার কাঁখে একটি মাটির কলসি। কলসিতে জল ভরে তিনি নামিয়ে রাখেন গর্ত হওয়া পাথরের উপর। তারপর জলভরা কলসি নিয়ে মাহিলাটি বাড়ি চলে যান।
বোপদেব তখন বুঝলেন, দিনের পর দিন সানবাঁধা- নো ঘাটে জলভরা মাটির কলসি নির্দিষ্ট স্থানে বারবার রাখার ফলে কলসির ঘষায় ঘষায় কঠিন পাথরের উপর কলসির মাপে গর্ত হয়েছে। এই দৃশ্য দেখে তিনি চিন্তা করলেন, কী আশ্চর্য! মাটির কলসির অবিরাম ঘর্ষণে পাথরও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। নিরেট পাথরের বুকে দিনের পর দিন মাটির কলসির রাখার ফলে যদি গর্ত হতে পারে তাহলে বারবার পাঠ করলে আমিইবা পড়া মনে রাখতে পারব না কেন! কেনইবা বারবার চেষ্টা করেও বুঝতে পারব না! নিজেকে প্রশ্ন করলেন, আমি কি পাথরের চেয়েও নিরেট? তিনি বুঝলেন, বারবার চেষ্টা করলে আমি নিশ্চয়ই ব্যাকরণশাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হব। তিনি হতাশা ত্যাগ করে ছুটে গেলেন পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে। গিয়ে বললেন নিজের উপলব্ধির কথা।
পণ্ডিত মহাশয় অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন বোপদেবের দিকে। এইতো, এইতো তাঁর চোখ খুলেছে। মনের বিস্তার ঘটেছে। মন ভাবতে শিখেছে! এতদিন তিনি তো বারবার বোপদেবকে ভাবাতেই চেয়েছিলেন। সেই চিন্তনের পাঠ বোপদেব পেয়েছেন প্রকৃতির কাছ থেকে। যে পুত্রসম ছাত্রকে তিনি টোল থেকে বের করে দিয়েছিলেন, তাঁকেই পরমস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরেন।
এরপর বোপদেব ব্যাকরণশাস্ত্রে জ্ঞান অর্জনের জন্য কঠোর সাধনা করতে লাগলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের সহা- য়তায় তিনি দুর্বোধ্য ব্যাকরণ আয়ত্ত করতে সক্ষম হলেন। একসময়ে বোপদেব নিজেই সংস্কৃত ব্যাকরণকে সূত্রায়িত করেন। যে ব্যাকরণশাস্ত্র ছিল একসময়ে একেবারেই দুর্বোধ্য, সেই শাস্ত্রের সূত্রগুলো নিয়েই বোপদেব রচনা করেন একটি আধুনিক ব্যাকরণগ্রন্থ। বোপদেবের এই বিখ্যাত ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ'। এমন সহজবোধ্য ব্যাকরণ সেকালে আর দ্বিতীয়টি ছিল না। ব্যাকরণশাস্ত্রকে সরলতম করাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁর লেখা এই ব্যাকরণ বই ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। বোপদেব কবিকল্পদ্রুম ও তার কামধেনু টাকা, মুক্তাফল ও হরিলীলা বর্ণনা, শতশ্লোকী ও ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন।
অপমান থেকে আত্মজিজ্ঞাসা, ক্ষণিকের দেখা থেকে দর্শন বোপদেবের চোখ খুলে দিয়েছিল। কঠোর সংকল্প ও অধ্যবসায়ের এক অনবদ্য নজির স্থাপন করেন ক্লাসের সবচেয়ে নির্বোধ পড়া-না-পারা ছাত্রটি। কঠোর অধ্যবসা- য়ের বলে মানুষ কী করে সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারে, বোপদেব গোস্বামীর গল্পটি তার অনবদ্য উদাহরণ।
- আমরা প্রত্যেকে নিজের জীবনের কোনো একটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করি যেখানে অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সাফল্য লাভ করতে চাই। কীভাবে কাজটি করব, বুঝিয়ে 'সাফল্য-সূত্র' ঘরে লিখি।
ছক ৩.৬: সাফল্য-সূত্র ছক
|
মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য
মাতা ও পিতা আমাদের পরম গুরু। হিন্দুধর্ম মতে, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। অর্থাৎ জননী ও জন্ম- ভূমি স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।
পিতা সম্পর্কে হিন্দুধর্মে বলা হয়েছে-
পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতাঃ।।
অর্থাৎ পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতাই পরম তপস্যা। পিতা প্রীত হলে সকল দেবতা তুষ্ট হন।
যা কিছু করা হয় তাই কর্ম। আর যেসব কর্ম অনুশীলন করা আবশ্যক তাই কর্তব্য। কর্তব্যের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবোধকে বলে কর্তব্যবোধ। পৌরাণিক কাহিনিতে আমরা মাতাপিতার প্রতি কর্তব্যবোধের অনেক উদাহরণ দেখেছি। রাম পিতৃসত্য পালনের জন্য চৌদ্দ বছর বনবাস করেছিলেন, ভীম মায়ের আজ্ঞায় রাক্ষসের মুখে যেতেও কুণ্ঠিত হননি। শাস্ত্র অনুযায়ী, মাতাপিতার প্রতি ভক্তিমান নয় এমন সন্তান কাম্য নয়। মাতা-পিতার সঙ্গে সবসময়ে নম্রতা ও বিনয়ের সঙ্গে কথা বলা প্রত্যেকটি সন্তানের একান্ত কর্তব্য। তাদের জীবনে যখন বা- র্ধক্য আসে, কর্মজীবন থেকে অবসর নিতে হয়, তখন অনেকেই অন্যের ওপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। শৈশবে সন্তান যেমন মাতাপিতার প্রতি একান্তভাবে নির্ভর করত, ঠিক তেমনিভাবে বৃদ্ধাবস্থায় তাদের দায়িত্ব নেওয়া প্রত্যেকটি সন্তানের জন্য আবশ্যক। যে সন্তান পরিণত বয়স পর্যন্ত মাতাপিতার সেবা করার সুযোগ পান তিনি ভাগ্যবান। নিজের কর্ম এবং চরিত্র দ্বারা মাতাপিতাকে তুষ্ট করা প্রত্যেকটি সন্তানের অবশ্য কর্তব্য।
- আমরা প্রত্যেকে মাতাপিতার প্রতি নিজে পালন করি এ রকম তিনটি কর্তব্যের কথা 'আমার কর্তব্যবোধ' ছকে লিখি।
ছক ৩.৭: আমার কর্তব্যবোধ
১.
|
২.
|
৩.
|
এখানে আমরা মাতাপিতার প্রতি কর্তব্যপরায়ণ এক পুত্রের কাহিনি জানব। রামায়ণে এই গল্প আছে।
সিন্ধুমুনি ছিলেন অত্যন্ত মাতৃপিতৃভক্ত। তাঁর পিতা ও মাতা দুজনেই ছিলেন অন্ধ। মুনি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে মা- তাপিতার সেবা করতেন। তাঁর পিতা অন্ধকমুনি নামে পরিচিত ছিলেন। সিন্ধুমুনি তাঁর অন্ধ পিতামাতাকে একটা ভারে করে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যেতেন। একবার তাঁর মাতা-পিতার তীর্থযাত্রার ইচ্ছে হলো। পুত্র সিন্ধুমুনি তাঁদের ভারে তুলে কাঁধে করে রওনা হলেন। পথে মাতা-পিতা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েন।
সিন্ধুমুনি তাঁদের জন্য জল আনতে কলসি নিয়ে সরযূ নদীতে যান। এসময়ে অযোধ্যার রাজা দশরথ সেই বনে শিকার করতে আসেন। শিকার খুঁজে খুঁজে তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। দশরথ তখন সেই জলাশয়ের তীরে একটি গাছের নিচে বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন। সিন্ধুমুনি যখন কলসিতে জল ভরছিলেন, রাজা দশরথের কানে সে শব্দ পৌঁছায়। তিনি চোখে না দেখে কেবল শব্দ শুনেই তীর ছুঁড়ে শিকার করতে পারতেন। একে বলে শব্দভেদী বাণ। রাজা দশরথ কলসিতে জল ভরার শব্দকে হরিণের জল খাওয়ার শব্দ বলে ভাবলেন। তিনি শব্দের দিকে লক্ষ করে বাণ ছুঁড়ে মারেন। সেই বাণ সিন্ধুমুনিকে বিদ্ধ করে। বাণবি- দ্ধ মুনি সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়েন। হরিণ শিকার করেছেন ভেবে রাজা দশরথ সেটি আনতে যান। কিন্তু এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে দশরথ ভীষণ অনুতপ্ত হন। তিনি শুশ্রুষা করে সিন্ধুমুনির জ্ঞান ফিরিয়ে আনেন। দশরথের অনুতাপ দেখে মুমূর্ষু সিন্ধুমুনি তাঁকে আর কোনো অভিশাপ দেননি। মৃত্যুকালে তিনি নিজের জীবনের জন্য কোনো দুঃখও করেননি। কেবল অন্ধ মাতাপিতার আসন্ন কষ্টের কথা ভেবে তাঁর হৃদয় ব্যথায় ভরে উঠল। মুনি গভীর দুঃখে বললেন, আমার বৃদ্ধ মাতাপিতার শুশ্রুষা আর ভরণ-পোষণের সমস্ত দায়িত্ব ছিল আমার ওপরে। আমাকে ছাড়া তাঁরা কী করে বাঁচবেন! তাঁরা কী করে পুত্রশোক সহ্য করবেন! মৃত্যুর আগে সিন্ধুমুনি দশরথের কাছে বললেন, আমাকে মাতাপিতার কাছে নিয়ে চলো। এদিকে সিন্ধুমুনির মাতাপিতা ছেলের দেরি দেখে দুশ্চিন্তা করছিলেন। পাতার মচমচ শব্দ শুনে তারা ভাবলেন, এই বুঝি ছেলে এল! কিন্তু দশরথের কোলে সন্তানের মৃতদেহ রয়েছে বুঝতে পেরে তাঁরা হাহাকার করে উঠলেন। অন্ধকমুনি রাজা দশরথকে পুত্রহারা হওয়ার অভিশাপ দিলেন।
সিন্ধুমুনি মৃত্যুকালে রাজা দশরথকে নিজের মাতাপিতার দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেছিলেন। অন্ধকমুনির অভিশাপ সত্ত্বেও দশরথ তাঁদের দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন।
প্রত্যেক মানুষেরই সবটুকু সাধ্য দিয়ে মাতাপিতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করা উচিত। সিন্ধুমুনির জীবন তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই কর্তব্যবোধের কারণে তিনি আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর এই দৃষ্টান্ত সকলের জন্য অনুকরণীয়।
- চলো, আমরা প্রত্যেকে ধাপে ধাপে 'মঙ্গলময় উদ্যোগ' কাজটি করি।
নিজের মা/ বাবা/ অভিভাবক- যে-কোনো একজনের সারাদিনের কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করে তালিকাটি তৈরি করি।
তাঁর কাজের ফলে আমার যেসব মঙ্গল/ভালো হয় সেগুলোর তালিকা করি।
ছক ৩.৯: আমাদের মঙ্গলের তালিকা
|
বাবার/ মায়ের/ অভিভাবকের প্রয়োজন বুঝে তাঁর জন্য নিজের হাতে একটি উপহার তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে এনে সবাইকে দেখাই।
উপহারটি পেয়ে মা/ বাবা/ অভিভাবকের অনুভূতি মন্তব্য হিসেবে লিখে আনি।
যে উপহারটি দিয়েছি
|
যে কারণে এটি দিয়েছি
|
মা/ বাবা/ অভিভাবকের মন্তব্য
|
|
|
|
- চলো, আমরা সবাই মিলে নৈতিক মূল্যবোধ চর্চার জন্য 'ইথিক্স ক্লাব' গঠন করি। সকলের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে 'ইথিক্স ক্লাব কার্যক্রম' এর তালিকা করে প্রত্যেকে লিখে রাখি। (তিনটি দেওয়া আছে আরও নতুন তিনটি লিখি।
ছক ৩.১০: ইথিক্স ক্লাব কার্যক্রম তালিকা
১. নিজেদের করা ভালো কাজগুলো এবং নিজেদের অনুভূতি সদস্যদের সামনে নিয়মিতভাবে উপস্থাপন করব। ২. নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হওয়ার জন্য আমাদের করণীয় সম্পর্কে আলাপ করব। ৩. ব্যক্তিগত এবং দলীয়ভাবে ভালো কাজ করার পরিকল্পনা করব এবং তা বাস্তবায়ন করব। 8. ৫. ৬.
|
ইথিক্স ক্লাব-কার্যক্রমের শুরুতে আমরা প্রত্যেকে প্রথমে নিচের কাজদুটো করি।
- 'আমার মূল্যবোধ' তালিকাটি ব্যবহার করে, ফুলের ছবিটির প্রত্যেক পাঁপড়িতে একটি করে নৈতিক মূল্যবোধের নাম লিখি। (প্রয়োজনে আরও কিছু পাঁপড়ি এঁকে নিই।) যদি তালিকাটি তৈরির পরে আমি নতুন কোনো মূল্যবোধের নাম জানতে পারি, সেগুলোর নামও লিখি।
মূল্যবোধের ফুল
- আমরা প্রত্যেকে প্রতি সপ্তাহে মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায় এ রকম অন্তত একটি কাজ করব। মোট পাঁচ সপ্তাহে পাঁচটি কাজের কথা লিখে 'চেতনার পরিচয়' ছকটি পূরণ করব।
ছক ৩.১১: চেতনার পরিচয়
নৈতিক মূল্যবোধের নাম | তারিখ | কাজের বর্ণনা | আমার অনুভূতি |
|
|
|
|
আরও দেখুন...
Promotion