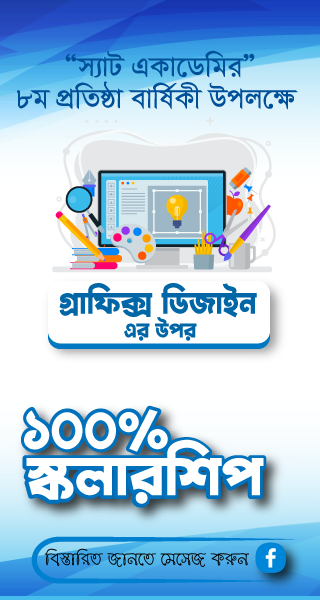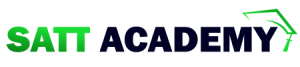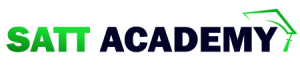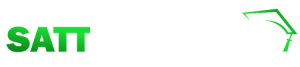কল্পনাতে ভ্রমণ করি, নিজের মনে স্বদেশ ঘুরি' পঞ্চরয়ের কল্পনায় স্বদেশ ঘোরার কার্যক্রম খুব আনন্দের সাথে চলমান আছে। এরই ধারাবাহিকতায় পঞ্চরত্ন এসে পৌঁছেছে পদ্মাতীরের জনপদ রাজশাহীতে। সেখানে থাকে আকাশের চাচাতো বোন মৃত্তিকা আপু আর রায়হান দুলাভাই। স্টেশনে পঞ্চরত্নকে নিতে এলো আপু আর দুলাভাই। স্টেশন থেকে বাসায় পৌঁছে সকালের নাস্তা খেতে খেতে মৃত্তিকা আপু আর রায়হান ভাই পঞ্চরত্রের বিস্তারিত ভ্রমণ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাইল। পরিকল্পনা শুনে তিনি বললেন আগে রাজশাহী সম্পর্কে তোমাদের একটা ধারণা দিই।
রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, জয়পুরহাট এই আটটি জেলা নিয়ে গঠিত হয় রাজশাহী বিভাগ। বিভাগের প্রতিটি জেলা প্রাচীন ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। তাছাড়া সিল্কের কাপড় আর রাজশাহীর আম 'এই দুই পণ্য বিশ্বে অনন্য' বললেন রায়হান ভাই।
পরিকল্পনা অনুসারে এবার তারা পদ্মাতীরের জেলা রাজশাহীকে ঘুরে দেখার জন্য বেরিয়েছে। প্রথমে তারা গেল পদ্মার পাড়ে, সেখানে নদী তীরে জেগে ওঠা চরে মাসব্যাপী মেলা চলছে। মেলায় ঘুরতে ঘুরতে নানা রকমের সামগ্রী তাদের চোখে পড়ল। যেমন- তাঁত, বাঁশ-বেত, মাটি, কাঁসা-পিতল, কাঠসহ বিভিন্ন উপকরণে তৈরি সামগ্রী। তাছাড়া খাবারের মধ্যে রয়েছে নানা রকমের মিষ্টি, পিঠা-পুলি, কলাইয়ের তৈরি রুটি ও নানা রকমের ভর্তা।
মৃত্তিকা আপু আর রায়হান ভাইয়ের সাথে মেলায় ঘুরতে ঘুরতে তারা দেখতে পেল, তাদের বয়সী আরোও অনেকেই মেলায় এসেছে। তাদের কয়েকজন মেলার একপ্রান্তে থাকা বড় বট গাছের নিচে বসে গান করছে। কয়েকজন আবার তার সাথে মিলে হাতে তালি দিয়ে সহপাঠীকে গান গাইতে উৎসাহ দিচ্ছে। কেউ কেউ গানের সাথে হাত-পা নেড়ে নানারকম ভঙ্গিতে নাচার চেষ্টাও করছে। মেলায় আসা দর্শনার্থীরা বিষয়টিকে বেশ উপভোগ করছে। পঞ্চরত্নও দেরি না করে সেখানে গিয়ে গানের আসরে যোগ দিল। সেখানে কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাটিয়ালি সুরের একটি গান হচ্ছিল।
মেলা
গানটি হলো-
পদ্মার ঢেউরে
মোর শূন্য হৃদয়-পদ্ম নিয়ে যা,
যা রে এই পদ্মে ছিল রে যার রাঙা পা
আমি হারায়েছি তারে।
মোর পরান-বঁধু নাই,
পদ্মে তাই মধু নাই, (নাই রে)
তাস কাঁদে বাইরে,
সে-সুগন্ধ নাই রে মোর রূপের সরসীতে আনন্দ-মৌমাছি নাহি ঝংকারে রে।।
ও পদ্মারে-
ঢেউয়ে তোর ঢেউ উঠায় যেমন চাঁদের আলো
মোর বঁধুয়ার রূপ তেমনি ঝিলমিল করে কৃষ্ণ-কালো।
সে প্রেমের ঘাটে ঘাটে বাঁশী বাজায়
যদি দেখিস তারে, দিস এই পদ্ম তার পায়
বলিস, কেন বুকে আশার দেয়ালী জ্বালিয়ে
ফেলে গেল চির-অন্ধকারে।।
সবার সাথে হাতে তালি দিয়ে গান করতে করতে ইরা খেয়াল করল সবার হাতের তালি একই সময়ে হচ্ছে না। গানের শেষে ইরা সমীরকে জিজ্ঞাসা করল আচ্ছা, গান গাওয়ার সময় আমাদের সবার ভালি একসাথে শেষ হলো না কেন? ইরার কথা শুনে সমীর বলল ভাল আর লয়ের সঠিক সমন্বয় হয়নি তাই।
পঞ্চরত্রের মধ্যে সমীর আগে থেকেই গান শেখে। মায়ের কাছে গান ও গানের তাল সম্পর্কে সে জেনেছে। বিষয়টি জানা থাকার ফলে সমীর তার বন্ধুদেরকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলল, এই যে সবাই মিলে হাততালি দিচ্ছি, নির্দিষ্ট সময় পরে তালির শব্দ করছি একে বলে 'তাল' যা আমরা আগের শ্রেণিতে জেনেছি। এখানে গানটি যে তালে চলছে সেটি হলো ৬ মাত্রার বা ৬ সংখ্যার। এই ভালকে বলা হয় 'দাদ্রা' তাল। 'দাদৃরা' তালের সংখ্যা এবং বোল সম্পর্কেও আমরা আগে জেনেছিলাম।
আকাশ জানতে চাইল, আগের ক্লাসে তারা 'দাদরা' তালটি শিখেছে। কিন্তু এই গানের সাথে সেটি মিলছে না কেন?।
একথা শুনে সমীর বলল, আমরাতো আগের শ্রেণিতে জেনেছি প্রত্যেকটি তালের তিনটি লয় আছে। সে অনুযায়ী দাদরা তালের চলন অনুসারে এটির তিনটি 'নয়' আছে। যথা- ১. বিলম্বিত লয় ২. মধ্য লয় ৩. দ্রুত লয়। গানের ধরন অনুসারে তার তাল এবং লয় নির্ধারিত হয়। কোনো গান বিলম্বিত লয়ে হয়, কোনোটি মধ্য অথবা দ্রুত লয়ে গাওয়া হয়। যেকোনো তালের বিলম্বিত গতিকে দ্বিগুণ কিংবা তিনগুণ করলেই তালের লয় বা গতি বেড়ে যায়।
এই পাঠে আমরা হাতে ভালি দিয়ে দ্রুত দাদরা তাল অনুশীলন করব
এবার সবাই মিলে হাতে তালি দিয়ে দাদরা তালের দ্রুত চলন শিখে নিল। গানের তালটি সম্পর্কে জানবার পর কোরাসে গানটি গাইতে সবার বেশ ভালোই লাগল।
এরই মধ্যে মেলা অঙ্গনে মাইকের ঘোষণা থেকে তারা জানতে পারল আজ বিকেলে মেলার মঞ্চে রাজশাহী আঞ্চলের লোক গান পরিবেশিত হবে। যার মধ্যে রয়েছে আলকাপ গান, বারাসিয়া গান, কান্ডির গান এবং গম্ভীরা গান।
এই ঘোষণা শুনেই পঞ্চরত্ন খুব আনন্দিত হলো। মৃত্তিকা আলু আর রায়হান ভাইয়ের সাথে কথা বলে তারা আজকের সময়গুলো এই মেলাতেই কাটানোর সিদ্ধান্ত নিল। এসব গান সম্পর্কে তারা আগে সামান্য জেনেছে কিন্তু কখনও তারা পরিবেশন দেখেনি বা শোনেনি। এখানকার জনপ্রিয় গান আঞ্চলিক গীতরীতি নামে পরিচিত হলেও সারাদেশে তার সমাদর রয়েছে। এই সুযোগে তারা পদ্মাপাড়ের বিভাগ রাজশাহী অঞ্চলের জনপ্রিয় সংগীত রীতি সম্পর্কে জানতে পারবে।
এরমধ্যে রাজশাহীর বিখ্যাত কলাইয়ের রুটি ও রসুন ভর্তা, বেগুন ভর্তা, শুটকি ভর্তাসহ বিভিন্ন রকমের ভর্তা সাথে জিলাপি, গরম মিষ্টি দিয়ে দুপুরের খাবার পর্ব শেষ করল।
বিকেল হতেই তারা আবারও মেলায় পৌঁছে গেল। সংগীত পরিবেশনার তালিকা তৈরির কাজ শুরু করলো। এদিন বিকেলে গান শোনার পাশাপাশি বিভিন্ন গানের দলের শিল্পীদের সাথে কথা বলে তারা স্থানীয় গান ও নাচের একটা তালিকা তৈরি করেছে। তাছাড়া তারা দুটি দলে ভাগ হয়ে মেলায় আগত স্থানীয় মানুষের সাথে কথা বলে লোকক্রীড়া, লোকশিল্প, লোকনৃত্য, লোকনাটোরও একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করেছে। এই সব তথ্য সংগ্রহে মৃত্তিকা আপু আর রায়হান ভাই তাদের অনেক সহযোগিতা করলেন। রাতে তারা বাসায় ফিরে দুদলের তৈরি করা তালিকাগুলো মিলাল। তালিকাগুলো মিলানোর পর তারা দেখল 'গম্ভীরা গান' এর বিষয়ে তারা সবাই বেশ গুরুত্বের সাথে তথ্য নিয়েছে। এটির পরিবেশনাও তারা উপভোগ করেছে।
আগুন বলল, গম্ভীরা গান কে বা কারা সৃষ্টি করেছেন, কেন সৃষ্টি করেছেন, এ গানের বিষয়বস্তু কি, কোথায়, কখন, কিভাবে এটি গাওয়া হয়, এ বিষয়ে কিভাবে আমরা আরোও বিস্তারিত জানতে পারি?
আগুনের এই কথা শুনে রায়হান ভাই বললেন আমি তোমাদের এই সব তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করতে পারি। কারণ আমি চাঁপাইনবাবগঞ্জসহ সমগ্র রাজশাহী বিভাগের প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুরে শিল্পীদের সাথে কথা বলে বছর দুই আগে একটা গবেষণাপত্র তৈরি করেছিলাম।
গম্ভীরা পান
এবার রায়হান ভাই গম্ভীরা সম্পর্কে বলতে লাগলেন। গম্ভীরা গানের আদি উৎপত্তিস্থল পশ্চিমবঙ্গের মালদহ অঞ্চলে। তবে আধুনিক গম্ভীরা গানের সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়। আধুনিক এই গম্ভীরা গানের প্রবর্তক কিংবদন্তী শিল্পী 'ওস্তাদ শেখ সফিউর রহমান ওরফে সুফি মাস্টার'। দেশভাগের পর তিনি গোমস্তাপুর উপজেলার রহনপুর বাজার এলাকায় পরিবারসহ স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে গম্ভীরা গানের 'নানা-নাতি' চরিত্রের সৃষ্টি করে তিনি এ গানের নবনির্মাণ করেন। মূলত তিনি স্বভাবকবি ছিলেন। অসংখ্য গম্ভীরা ও আলকাপ গান রচনা করেছেন। শুধু গান রচনাই নয়, গম্ভীরার নিজস্ব সুর, নাচের ভঙ্গি, অভিনয় এবং ছন্দভঙ্গির প্রবর্তকও তিনি। নতুন নতুন বিষয়ে উপর গম্ভীরা লিখে এ গানকে সবার কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছেন।
গ্রাম বাংলায় প্রচলিত কাহিনি, সাধারণ মানুষের জীবনাচার, সামাজিক সমস্যা, আঞ্চলিক ভাষার সুনিপুণ প্রয়োগে লোকনাট্যগীতের এই ধারাটি বিকশিত হয়েছে। গানের সুরটি বিশেষ গঠনের হওয়ার কারণে এটি 'গম্ভীরা সুর' নামেই পরিচিতি পেয়েছে। তবে গম্ভীরা গানকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে জনপ্রিয় করে তোলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জেরই আরও দুজন কৃতীসন্তান। তাঁরা হলেন 'রকিবউদ্দীন' এবং 'কুতুবুল আলম' জুটি। বাংলাদেশের সবার কাছে তাঁরা গম্ভীরার নানা-নাতি হিসেবেই পরিচিত।
নানার মুখে সাদা রঙের পাকা দাড়ি, মাথায় মাথাল, পরনে লুঙ্গি, হাতে পাচনি বা ছোট লাঠি আর নাতির পোশাক হলো গায়ে ছেড়া গেঞ্জি, কখনো কাঁধে লাঙল, পরনে লুঙ্গি ও কোমরে গামছা, পায়ে যুক্তর, সেই গামছার আঁচলে কলাইয়ের রুটি অথবা ছাতু বাঁধা। বেশিরভাগ সময়ে ঢোল, হারমোনিয়াম, বাঁশি, তবলা, জুড়ি বাদ্যযন্ত্রগুলোর সাহায্যে গম্ভীরা গাইতে দেখা যায়। সাধারণত বছরের শেষ দিনে অর্থাৎ চৈত্র মাসে এবং নতুন বছরের শুরুতে অর্থাৎ বৈশাখ মাসে এ গান পরিবেশন করবার রীতি প্রচলিত আছে।
এরমধ্যে সমীর প্রকৃতি ও পরিবেশ নিয়ে বিভিন্ন শিল্পীর রচিত গম্ভীরা গানের সাথে নিজের মতো করে নতুন কথা সংযোজন করে গম্ভীরা গান রচনার চেষ্টা শুরু করে দিল। পরের দিন 'সমীর' বেশ আগ্রহের সাথেই গম্ভীরা গানের যে অংশগুলো সে লিখেছে তা সুর-সহযোগে গেয়ে শুনাল।
গান
বন্যা-খরা ঝড়-জলোচ্ছ্বাস প্রাকৃতিক দুর্যোগ যত হয়
বৃক্ষছাড়া চারপাশের এই পরিবেশ বাঁচানোর উপায় নাই- নানা হে....
খাল-বিল আর জলাধার যত
নদী-নালা শত শত
পাহাড়-জঙ্গল-বন-বনানীর সঠিক রক্ষা করা চাই- নানা হে.......
ঘূর্ণিবাতাস, বজ্রঝড়ে কতজনার প্রাণ যায়
আম-কাঁঠাল, ক্ষেতের ফসল সবকিছুরই ক্ষতি হয়- নানা হে.......
ফল-ফলাদির গাছ লাগাও, দেশের পরিবেশকে বাঁচাও
আশের-পাশের পতিত জমি রেখোনারে আর ফেলি, নানা হে
সমীরের গানটা সবাই আনন্দের সাথে উপভোগ করল। এরপর অবনী বলল শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে আমি একটা গম্ভীরা গান লিখার চেষ্টা করেছি। এবার সে তার লেখা ও সুর করা গানটি গেয়ে শুনাল।
লেখাপড়া খেলাধুলা খাওয়া দাওয়া যা করি
গান বাজনা, আলকাপ, কবি, গম্ভীরা, জারি সারি, নানা হে-
লুঙ্গি-সার্ট-পাঞ্জাবি-শাড়ি এগুলাই হারণে সংস্কৃতি
কীর্তন, পদাবলী, বেহুলা লাচি, মেয়েলি গীত গায় এখন, নানা হে-
হে নানা শিল্প সংস্কৃতিই হলো এই বাঙালির পরিচয়, নানা হে-
সমীর আর অবনীর গানগুলো সবাই দলীয়ভাবে গাওয়ার চেষ্টা করল। এরমধ্যে ইরা বলল আমরা স্কুলে ফিরে শ্রেণির সবাইকে নিয়ে গম্ভীরা পরিবেশনার একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারি। প্রকৃতি ও পরিবেশ বিপর্যয় এবং শিক্ষা বিষয়ে সচেতনতা তৈরির জন্য আমরা নিজেদের রচিত এই গানগুলো গম্ভীরা ভঙ্গির সাথে মিলিয়ে পরিবেশন করব।
পরের দিন পঞ্চরত্র রাজশাহীর বিখ্যাত সিল্ক তৈরির প্রক্রিয়াটা দেখতে চাইল। রেল স্টেশনে নেমেই তারা দেখেছে রেশম কারখানা ও সেরিকালচার বোর্ডের সাইনবোর্ড। তারা রায়হান ভাইকে বিষয়টা জানালে তিনি পরের দিন তাদের কারখানা দেখাতে নিয়ে যাবার কথাটি জানালেন।
রাজশাহী সিল্ক
পরদিন সকালে সবাই সরকারি সিল্ক ফ্যাক্টরি দেখতে গেল। রায়হান ভাইয়া পঞ্চরত্নদের দেখাল কীভাবে ধৃত গাছের পাতা খেয়ে রেশম পোকা বড় হয়। পর্যায়ক্রমে পোকা রেশম গুটিতে পরিণত হয়ে সিল্ক সুতায় রূপান্তর হয়। গুটি সেদ্ধ করে সুতার মুখ বের করা হয়। চরকা ঘুরিয়ে সুতা সংগ্রহ করে তাঁতের সাহায্যে সিল্ক কাপড় বুনন দেখে সবাই তো অবাক! সেই কাপড় থেকে শাড়ি, নানান রকম জানা, ওড়না, পাঞ্জাবি, ফতুয়া, টাইসহ কতোকিছু তৈরি হচ্ছে।
রাজশাহীতে বেসরকারি পর্যায়েও বেশকিছু ফ্যাক্টরিতে এভাবে সিল্ক কাপড় বুনন, ডিজাইন, রং করা, প্রিন্ট, পলিশ, ফিনিশিং ও বাজারজাতের ব্যবস্থা আছে। এই অঞ্চলের নারীরা সিল্ক কাপড়ে বাটিক, টাই-ডাই, হ্যান্ডপ্রিন্ট, রাশপ্রিন্ট, ব্লকের মধ্য দিয়ে হরেক রকমের প্রাকৃতিক ও জ্যামিতিক নকশা ফুটিয়ে তুলে রাজশাহী সিঙ্ককে জনপ্রিয় করে তুলেছে। তাঁর সাথে সাথে নিজেরাও স্বাবলম্বী হচ্ছে। বিদেশেও এই সকল সিল্ক পণ্যের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। ফলে এই সব সামগ্রী দেশের বাইরে রপ্তানি করে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হচ্ছে।
এরপর সিল্ক কাপড়ে নকশা সম্পর্কে জানতে পঞ্চরত্ন রাজশাহী চারুকলা অনুষদের কারুকলা বিভাগে গেল। সেখানে তারা কাপড়ের উপর টাই-ডাই, বাটিক, হ্যান্ডপ্রিন্ট, স্ক্রিনপ্রিন্ট, ব্লকপ্রিন্ট, অ্যাপ্লিক ইত্যাদি মাধ্যমে নকশা করার পদ্ধতি দেখল। কারুকলা বিভাগের একজন শিক্ষকের কাছে নকশা তৈরি সম্পর্কে জানতে চাইলে শিক্ষক বললেন, ছবি আঁকার গুরুত্বপূর্ণ নিয়মনীতির একটি হলো ছন্দ (rhythm)। সমীর বলল নাচে এবং গানেওতো ছন্দ আছে। তিনি বললেন শিল্পকলার সবখানেই ছন্দ আছে। আকাশ ছবি আঁকার ছন্দ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন-
ছবি আঁকার উপাদানগুলোর নান্দনিক গতিময়তাকে ছন্দ (rhythm) বলে। ছবি আঁকায় প্রধানত তিন রকমের ছন্দের বেশি ব্যবহার দেখা যায়। যেমন-পুনরাবৃত্তিক ছন্দ, ধারাবাহিক ছন্দ, ক্রমবর্ধমান ছন্দ।
পুনরাবৃত্তিক ছন্দে ব্যবহৃত আকৃতিগুলো সমান মাপে এবং সমান দূরত্বে থাকে। ধারাবাহিক ছন্দে সমান মাপে আকৃতিগুলো একই দূরত্বে থাকে না। ক্রমবর্ধমান ছন্দে আকৃতিগুলো এবং দূরত্ব কম থেকে বেশি হয়ে থাকে। এই তিনটি ছন্দের নিয়মনীতি অনুসরণ করে তোমরা খুব সহজে নতুন নতুন নকশা তৈরি করতে পার। তোমাদেরকে ছবি আঁকার ছন্দ ব্যবহার করে নকশা তৈরির একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা দেই।
এই পাঠে আমরা কাগজ কেটে ছবি আঁকার ছন্দ ব্যবহার করে নকশা করব
এই তিন রকমের ছন্দের মধ্য হতে পুর্নাবৃতিক ছন্দ এবং ক্রমবর্ধমান ছন্দের সাহায্যে খুব সহজে নকশা করা যায়। এক্ষেত্রে তোমরা প্রাকৃতিক বা জ্যামিতিক আকৃতি ব্যবহার করতে পার। এই নকশা তৈরিতে তোমরা সহজলভ্য যেকোনো দু'রঙের পোস্টার পেপার ব্যবহার করতে পার। পোস্টার পেপার পাওয়া না গেলে সেক্ষেত্রে বিভিন্ন রঙের পরিত্যক্ত কাগজের প্যাকেট কেটে তা ব্যবহার করা যাবে। এছাড়া কাগজ কাটার জন্য লাগবে ছোট একটি কাঁচি আর কাগজ জোড়া লাগানোর জন্য অল্প আঠা।
- প্রথমে দৈর্ঘ্যে ৬ ইঞ্চি এবং প্রন্থে ৬ ইঞ্চি একটা বর্গক্ষেত্র আঁকব।
- বর্গক্ষেত্রটি ১ ইঞ্চি করে ছক করে নেব।
- এবার দুটি আলাদা রঙের কাগজ থেকে ১ ইঞ্চি থেকে একটু ছোট মাপের ত্রিভুজ এবং বৃত্ত এঁকে কাঁচি দিয়ে কেটে নিতে হবে। তবে চাইলে ১ ইঞ্চি মাপের ফুল এবং পাতাও ব্যবহার করা যায়।
- এবার ছক আঁকা কাগজের প্রতিটি ছকের একটিতে ত্রিভুজ পরেরটিতে বৃত্ত এভাবে আঠা দিয়ে লাগিয়ে পুনরাবৃত্তিক ছন্দের নকশা তৈরি করতে পারি। এই ক্ষেত্রে ত্রিভুজ এবং বৃত্তের পরিবর্তে
- চাইলে ১ ইঞ্চি থেকে একটু ছোট মাপের ফুল এবং পাতাও ব্যবহার করতে পারি।
- একইভাবে কাগজে ছোট থেকে ক্রমন্বয়ে বড় বৃত্তে এঁকে তা প্যাঁচানো (spiral) ভাবে সাজিয়ে খুব সহজে ক্রমবর্ধমান ছন্দের নকশা তৈরি করা যায়।
এই নকশাগুলো পরে নিয়মনীতি অনুসরণ করে কাপড়সহ যেকোনো উপকরণের উপর স্থানান্তর করে নতুন নতুন পণ্যের নকশা করা যায়।
এই বাস্তব অভিজ্ঞতার পর চারুকলা অনুষদের শিক্ষকের সাথে তাদের অনেক কথা হলো। তিনি বললেন শিল্পীরা যখন কোনো পণ্যের গায়ে তার নান্দনিকতার পরশ বুলিয়ে দেন সাথে সাথে তা হয়ে ওঠে অনন্য সুন্দর। এবার তোমাদের তেমন একজন শিল্পীর কথা বলব। তিনি চিত্রশিল্পী হলেও তার তুলির ছোঁয়ায় নান্দনিকতা পেয়েছে আমাদের দেশের তৈরি পোশাক, পোস্টার, বইয়ের প্রচ্ছদ থেকে শুরু করে আরোও অনেক শিল্প। তিনি হলেন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী।
শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী ১৯৩২ সালে ফেনী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৯ সালে আর্ট ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন এবং ১৯৫৪ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে শিক্ষা সমাপন করেন। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, পটুয়া কামরুল হাসান এবং সফিউদ্দীন আহমেদের মতো দিকপাল শিল্পীদের তিনি পেয়েছিলেন শিক্ষক হিসেবে। তীদের কাছ থেকে কাইয়ুম চৌধুরী অর্জন করেছিল 'দেখবার' এবং 'দেখাবার' যোগ্যতা। এই শৈল্পিক দৃষ্টি শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীকে করেছে চিত্রশিল্পীর সাথে সাথে এক অনন্য নকশাবিদ। ১৯৫৭ সালে কাইয়ুম চৌধুরী আর্ট কলেজে শিক্ষকতায় যোগ দেন।
দেশীয় উপকরণে তৈরি পোশাক তাঁর হাতের নকশায় রূপ নিয়েছে এক অনন্য শিল্পকর্মে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ থেকে শীত, বসন্ত বাংলাদেশের ষড়কতুর প্রত্যেকটি রূপকে তিনি তার নকশা করা পোশাকে প্রকাশ করেছেন এক অপূর্ব নান্দনিকতায়। আমাদের প্রতিটি জাতীয় দিবস যেমন-আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসসহ সকল দিবসকে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী রাঙিয়েছেন তাঁর নকশা করা পোশাক দিয়ে। সিল্ক অথবা সুতিতে তৈরি শাড়ি থেকে গায়ের চাদর সবকিছু তার তুলির আঁচড়ে এক অনন্য চিত্রমালা হয়ে উঠেছে। আধুনিক ফ্যাশনসচেতন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী তরুণ প্রজন্মের কাছে দেশের তৈরি পোশাকে জনপ্রিয় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।
পঞ্চাশের দশকে পটুয়া কামরুল হাসানের হাত দিয়ে শুরু হয়েছিল দেশের তৈরি পোশাকে শিল্পের প্রকাশ ঘটানোর কাজ। সে কাজকে আরও বেশি এগিয়ে নিয়ে দেশীয় ফ্যাশনকে ব্র্যান্ডিংয়ে রূপ দিয়েছেন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী। দেশীয় ফ্যাশনের সাথে সাথে তিনি বাংলাদেশের প্রকাশনী শিল্পের রূপকে করে তুলেছিলেন নান্দনিক। তাঁর হাত দিয়ে বাংলাদেশের পোষ্টার পেয়েছিল এক অপূর্ব শৈল্পিক দিক। বইয়ের প্রচ্ছদ অঙ্কনে তিনি অনন্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তাঁর করা টাইপোগ্রাফিই ছিল এসব পোস্টার আর প্রচ্ছদের প্রাণ।
বাংলাদেশের চিত্রকলার সম্ভারকে তিনি করেছেন সমৃদ্ধ। চিত্রে তাঁর নিজস্ব রচনা শৈলির কারণে তিনি বাংলাদেশের সমসাময়িক শিল্পীদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী হিসেবে বিবেচিত। গ্রাম বাংলার প্রকৃতি, নদী, নৌকা, কৃষান, কৃষানী, পশু-পাখি সবকিছু প্রকাশিত হয়েছে পরম মমতায়। উজ্জ্বল প্রাণবন্ত রঙের ব্যবহার তাঁর শিল্পকর্মের বিশেষ দিক।
শিল্পকলায় বিশেষ অবদানের জন্য শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী ১৯৮৬ সালে একুশে পদক লাভ করেন। এছাড়া ২০১০ সালে তিনি সুফিয়া কামাল পদক এবং ২০১৪ সালে স্বাধীনতা পদক লাভ করেন। ২০১৪ সালে ৩০শে নভেম্বর তিনি মৃত্যু বরণ করেন।
শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর কিছু শিল্পকর্ম
এরপর পঞ্চরর একে একে দেখতে গেল পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার, মহাস্থানগড়, বাংলাদেশের তথা প্রাচীন বাংলার অন্যতম পুরাতন স্থাপত্য পুরাকীর্তি সোনা মসজিদ। গেল মহারানী হেমন্ত কুমারী দেবীর বাসভবন পুঠিয়া রাজবাড়ী। বাংলার প্রাচীন স্থাপত্যশিল্পের এক বিশেষ নিদর্শন জোড়বাংলা মন্দির এসব নিদর্শন দেখে তারা আসল উত্তরা গণভবনে।
উত্তরা গণভবন
১৯৭২ সনে দিঘাপাতিয়া রাজবাড়িটির নাম 'উত্তরা গণভবন' নামকরণ করে প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাঞ্চলীয় বাসভবন হিসেবে সংরক্ষন করা হয়। ঢাকার বাইরে এটিই প্রধানমন্ত্রীর একমাত্র বাসভবন।
ভবনটির পিরামিড আকৃতির চারতলার প্রবেশদ্বারের উপরে রয়েছে বিশাল ঘড়ি। যা ইতালি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। প্রধান ভবন, কুমারপ্যালেস, কাচারি ভবন, তিনটা কর্তারানী বাড়ি, রান্নাঘরসহ মোট ১২টি ভবন আছে। প্যালেসের দক্ষিণে গার্ডেনে রয়েছে নকশা করা মার্বেল পাথরের ভাস্কর্য। ভবনের সামনে দুটিসহ মোট ৬টি কামান আছে। হালকা হলুদ ও রেড অক্সাইড বা ইট কালার মিশ্রিত ভবনটি পুরনো স্থাপত্যের অনন্য নিদর্শন। ভবনের চূড়ায় গোলাকৃতি নকশার মাঝে বিশাল ঘড়ি সবার নজর কাড়ে।
রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য নিদর্শনসমূহ দেখে পঞ্চরত্ন তাদের বন্ধুখাতায় অনেক নকশা এঁকে নিল। তার সাথে সাথে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ লিখে নিল।
এবার তারা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ভাস্কর্য দেখার জন্য উপস্থিত হলো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গেইটের কাছে, সিনেট ভবনের দক্ষিণ পাশে। লালচে রঙের অপূর্ব ভাস্কর্যটি দেখে তারা ভাস্কর্যের তথ্য সংগ্রহে আগ্রহী হয়ে উঠল।
সাবাস বাংলাদেশ
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সারণে যতগুলো স্মারক ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে "সাবাস বাংলাদেশ" ভাস্কর্য অন্যতম। এটির রং, রূপ, আকার গঠনশৈলি ও প্রকাশের বৈচিত্রতা লক্ষ্যণীয়।
১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রখ্যাত ভাস্কর শিল্পী নিতুন কুণ্ডুকে দিয়ে নির্মাণ করান সাবাস বাংলাদেশ ভাস্কর্যটি।
ভাস্কর্যটিতে রয়েছে দুজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। একজন গ্রামীণ যুবক, পরনে লুঙ্গি। অপরজন প্যান্ট পরা শহরে যুবক। উভয়েরই গায়ে জামা নেই। রাইফেল হাতে নিয়ে তারা শত্রুর মোকাবেলায় সামনের দিকে দৌড়াচ্ছে। ভাস্কর্যটিতে সারা দেশের মানুষের অংশগ্রহণকে উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্রামীণ যুবকের এক হাতে রাইফেল, আরেক হাত মুষ্টিবদ্ধ ভাবে উপরে উঠানো। মাথায় তার গামছা বাঁধা। প্যান্ট পরিহিত শহরের যুবকটি দুই হাত দিয়ে রাইফেল ধরে সামনে ধাবমান। কোমরে গামছা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল বাতাসে উড়ছে। কংক্রিটের তৈরি ভাস্কর্যের পিছনে রয়েছে মুক্তমঞ্চ। ৪০ বর্গফুট বেদির উপর নির্মিত হয়েছে ভাস্কর্যটি। পিছনে ৩৬ ফুট উচ্চতার স্তম্ভ। স্তম্ভের গায়ে ৫ ফুট ব্যাসের গোলাকার ছিদ্র বা খালি অংশ আছে। এই গোলাকার অংশ দিয়ে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার বৃত্তকে বোঝানো হয়েছে।
মঞ্চের পিছনের দেয়ালে খোদাই করা রিলিফ ভাস্কর্য। তাতে উপস্থাপন করা হয়েছে নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতীসহ আপামর জনতার পতাকা মিছিল। গ্রাম-বাংলার চিরায়ত দৃশ্য, একতারা হাতে বাউল, ইত্যাদি চিত্র ফুটিয়ে ভোলা হয়েছে এই রিলিফ ভাস্কর্যে।
ভাস্কর্যের বেদিতে লেখা আছে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের বিখ্যাত কবিতা-
'সাবাস বাংলাদেশ
এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়
জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়'
এই কবিতা সংযোজনের মাধ্যমে ভাস্কর্যের থিমকে আরও সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।
এই অধ্যায়ে আমরা যা করব-
- বইয়ের মতো করে কাগজ কেটে পুনরাবৃত্তিক ছন্দের নকশা এবং ক্রমবর্ধমান ছন্দের নকশা তৈরি করে নকশা করব।
- বইয়ের মতো করে হাতে তালি দিয়ে দ্রুত দাদরা তালের সাথে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের পদ্মার ঢেউরে- গানটি গাওয়ার চেষ্টা করব।
- বিভিন্ন মাধ্যমে গম্ভীরা গান শুনে এবং দেখে বইয়ে দেওয়া গম্ভীরা গানটি ভঙ্গি করে গাওয়ার চেষ্টা করব।
- নিজেদের এলাকায় যদি কোনো শৈল্পিক পোশাক সামগ্রী বিক্রয় প্রতিষ্ঠান থাকে, সেখানে গিয়ে পোশাকের নকশা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে পারি।
- শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর জীবন ও তাঁর শিল্পকর্ম সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব।
রাজশাহী বিভাগ থেকে পক্ষ রত্নের এবার গন্তব্য খুলনায় সমীরের দিদির বাড়ি। রূপসা ও ভৈরব নদীবিধৌত
Promotion