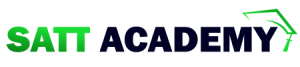মোলার দ্রবণ বা মোলারিটি বলতে কী বুঝ?
নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় 1 লিটার দ্রবণে 1 মোল দ্রব দ্রবীভূত থাকলে, তাকে ঐ তাপমাত্রায় ঐ দ্রবের মোলার দ্রবণ বলে।
নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় প্রতি লিটার দ্রবণে দ্রবীভূত দ্রবের মোল সংখ্যাকে ঐ দ্রবণের মোলারিটি বলে। একে M দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এর একক হল molL−1
মোলারিটি, S = লিটার দ্রবণের আয়তন মোল এককে দ্রবের ভর
S=Vn=M×VWn=MW(এখানে V লিটার এককে)
বা, S=M×VW×1000 [ এক্ষেত্রে V এর আয়তন mL এ বসানো হয় ]
ডেসিমোলার, সেমিমোলার এবং সেন্টিমোলার দ্রবণ বলতে কি বুঝ?
নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় –
1L দ্রবণে 1 mol বা 98g H2SO4 থাকলে তাকে 1M বা মোলার দ্রবণ বলে।
1L দ্রবণে 0.5 mol বা 49g H2SO4 থাকলে তাকে 0.5M বা সেমিমোলার দ্রবণ বলে।
1L দ্রবণে 0.1 mol বা 9.8g H2SO4 থাকলে তাকে 0.1M বা ডেসিমোলার দ্রবণ বলে।
1L দ্রবণে 0.01 mol বা 0.98g H2SO4 থাকলে তাকে 0.01M বা সেন্টিমোলার দ্রবণ বলে।
প্রমাণ দ্রবণ বলতে কী বুঝ?
নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট আয়তনের দ্রবণে দ্রবীভূত দ্রবের পরিমাণ জানা থাকলে তাকে ঐ দ্রবের প্রমাণ দ্রবণ বলে। যেমন– 0.1M Na2CO3 দ্রবণ একটি প্রমাণ দ্রবণ। কারণ নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় দ্রবণে কী পরিমাণ দ্রব আছে তা জানা যায়। যেমন – নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় প্রতি লিটার দ্রবণে 0.1mol বা 10.6 gm Na2CO3 দ্রবীভূত আছে।
ডেসিমোলার Na2CO3দ্রবণ একটি প্রমাণ দ্রবণ কেন?
মোলার দ্রবণ একটি প্রমাণ দ্রবণ – ব্যাখ্যা কর।
মোলার দ্রবনে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় 1L দ্রবণে 1mol Na2CO3 দ্রব দ্রবীভূত আছে। যেহেতু নির্দিষ্ট আয়তনে দ্রবীভূত দ্রবের পরিমাণ জানা আছে, তাই এটি একটি প্রমাণ দ্রবণ হবে। এর মোলার দ্রবণ অর্থাৎ 1L দ্রবণে 1mol বা 106 gm Na2CO3 দ্রবীভুত আছে।
মোলাল দ্রবণ এবং মোলালিটি বলতে কী বুঝ?
প্রতি kg দ্রাবকে 1mol পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত থাকলে দ্রবণটিকে ঐ দ্রবের মোলাল দ্রবণ বলে। তাছাড়া প্রতি kg দ্রাবকে দ্রবীভূত দ্রবের মোল সংখ্যাকে ঐ দ্রবণের মোলালিটি বলে। একে m দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
এর একক হল molkg−1
m=kg এককে দ্রাবকের পরিমাণ মোল এককে দ্রবের পরিমাণ
মোলারিটি ও মোলালিটির মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর। বা, এদের মধ্যে কোনটি তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল/কোনটি ব্যবহার সুবিধাজনক?
মোলারিটি হল দ্রবের ভর ও দ্রবণের আয়তন সম্পর্কিত রাশি। তাপমাত্রা পরিবর্তনের ফলে দ্রবণের আয়তন পরিবর্তিত হয়, তাই আয়তন ভিত্তিক দ্রবণের ঘনমাত্রা মোলারিটি পরিবর্তিত হয়। কিন্তু তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে বা তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে বস্তুর ভরের কোন পরিবর্তন হয় না। তাই দ্রাবক ও দ্রব উভয়ে গ্রাম এককে প্রকাশিত দ্রবণের ঘনমাত্রা মোলালিটির পরিবর্তন ঘটে না। অর্থাৎ তাপমাত্রা পরিবর্তনের ফলে মোলারিটির পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু মোলালিটির কোন পরিবর্তন ঘটে না। তাই মোলারিটির চেয়ে মোলালিটির ব্যবহার সুবিধাজনক বেশি।
প্রাইমারী স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ বলতে কী বুঝ?
যে সকল পদার্থ প্রকৃতিতে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়, যারা বস্তুর উপাদান O2 ও CO2 এর সাথে কোন বিক্রিয়া করে না, তারা পরিবাহী বা পানিগ্রাসী নয়, যারা রাসায়নিক নিক্তির উপাদানের সাথে বিক্রিয়া করে না বলে সঠিকভাবে ওজন করে সঠিক ঘনমাত্রায় দ্রবণ তৈরি করা যায় এবং যাদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত দ্রবণের ঘনমাত্রা দীর্ঘদিন ধরে অপরিবর্তিত থাকে তাদেরকে প্রাইমারী স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ বলে। যেমন– অনার্দ্র Na2CO3, K2Cr2O7, অক্সালিক এসিড (H2C2O4.2H2O),Na2C2O4,2H2O ইত্যাদি।
সেকেন্ডারী স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ বলতে কী বুঝ?
যে সকল পদার্থ প্রকৃতিতে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না। যারা বায়ুর উপাদানের সাথে বিক্রিয়া করে। যারা পানিগ্রাহী বা পানিগ্রাসী, যার রাসায়নিক নিক্তির উপাদানের সাথে বিক্রিয়া করে বলে সঠিকভাবে ওজন পরিমাপ করা যায় না যাদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত দ্রবণের ঘনমাত্রা কিছুসময় পর পরিবর্তন হয়ে যায় তাদেরকে সেকেন্ডারী স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ বলে।
HCl,H2SO4,NaOH,KMnO4,Na2 S2O3.5H2O
গাঢ় H2SO4 এসিড সেকেন্ডারী স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ কেন?
এটি একটি পানিগ্রাহী তরল পদার্থ, একটি ক্ষয়কারক এবং রাসায়নিক নিক্তির সংস্পর্শে আসলে এটি নিক্তির ক্ষয় করে। এর ফলে গাঢ় H2SO4 কে রাসায়নিক নিক্তিতে সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না। তাই H2SO4একটি সেকেন্ডারী স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ।
KMnO4 সেকেন্ডারী স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ কেন?
এটি বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না, এর দ্বারা প্রস্তুতকৃত দ্রবণ কিছু সময় রেখে দিলে দ্রবণের ঘনমাত্রা ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। কারণ KMnO4 বিযোজিত হয়ে MnO2 এ পরিণত হয়। তাছাড়া সূর্যালোকের সংস্পর্শে KMnO4 পানিকে জারিত করে O2 এ পরিণত করে। তাই এটি একটি সেকেন্ডারী স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ।
NaOH সেকেন্ডারী স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ কেন?
এটি একটি পানিগ্রাহী পদার্থ এবং ক্ষয়কারক বলে সঠিকভাবে এর ওজন পরিমাপ করা যায় না। তাছাড়া কাচপাত্রে রাখা হলে এটি কাচের উপাদান। সিলিকার সাথে বিক্রিয়া করে ঘনমাত্রা পরিবর্তন করে বা ঘনমাত্রা পরিবর্তিত হয়।
PPM বলতে কী বুঝ? (106)
PPM এর পূর্ণরূপ হলো Parts Per Million. প্রতি 10 লক্ষ ভাগ দ্রবণে বা মিশ্রণে যত ভাগ দ্রব দ্রবীভূত থাকে, তাকে ppm এককে দ্রবণটির বা মিশ্রণটির ঘনমাত্রা বলে। একে 3 ভাবে প্রকাশ করা যায়।
১/ কঠিন মিশ্রণের ক্ষেত্রে (vw)
এক্ষেত্রে 1 ppm = 1 mg/kg = 1µg/g
২/ দ্রবণের ক্ষেত্রে (vw)
এক্ষেত্রে 1 ppm =1µg/mL
= 1mg/L
= 1mg/dm3
=1g/m3
এক্ষেত্রে সাধারণত দ্রাবক হিসেবে বিশুদ্ধ পানি ব্যবহৃত হয়। বিশুদ্ধ পানির ক্ষেত্রে 1mL পানির ভর 1gm ধরা হয়।
৩/ তরল মিশ্রণের ক্ষেত্রে (vw)
এক্ষেত্রে 1ppm=1μL/L(10−6=1μg)
1ppm=1061=1 g10−6 g=1 g1μg=1 mL1μg(1μg/mL)
=1 kg10−6 g×103 g
=1 kg10−3 g
=1 kg1mg=1 L1mg
=103 L103mg=1 m31 g( g/m3)
1 ppb বলতে কী বুঝ?
প্রতি 100 কোটি ভাগ দ্রবণে বা মিশ্রণের মধ্যে যত ভাগ দ্রব দ্রবীভূত আছে, সে পরিমাণকে ppb এককে দ্রবণটির ঘনমাত্রা বলে। এর পূর্ণ নাম হল– Parts Per Billion.
( 1 ppb = 1 µg/L )
PPM , PPb, PPt এককে প্রকাশের পদ্ধতি বা মোলারিটিকে ppm, ppb তে প্রকাশ।
মোলারিটি ( C ) =M×VW×1000
W = gm এককে দ্রবের ভর
V = দ্রবের আয়তন
M = মোলার ভর
C=M×1000W×10−3×1000
W = ppm এককে দ্রবের ভর
V = 1000mL
W=C×M×103PPm
C=M×1000W×1000V=1000mLW=Cmol−1×Mgmol−1W=CMgL−1=C×M×103mgL−1=C×M×103PPmW=C×M×103PPm=C×M×106PPb=C×M×109PPt (Parts per trillion)
কতিপয় সূত্র জেনে রাখা ভালোঃ
1. PPm = নমুনার ভর ( গ্রাম ) দ্রবের ভর ( গ্রাম ) ×106
2. PPm = নমুনার আয়তন (মিলিলিটার) দ্রবের ভর ( গ্রাম ) ×106
3. PPb = নমুনার ভর ( গ্রাম ) দ্রবের ভর ( গ্রাম ) ×109
4. PPb = নমুনার আয়তন (মিলিলিটার) দ্রবের ভর ( গ্রাম ) ×109
5. মোলারিটি থেকে PPM: W = C×M×103 PPm
6. মোলারিটি থেকে শতকরায় রূপান্তর : x=1000CM%
Cx=M×VW×1000=M×V10x×1000=1000CM%
6. শতকরা পরিমাণকে PPM এ প্রকাশঃ PPM এর পরিমাণ x=W%×106 ( W% = শতকরার পরিমাণ )
7. PPM কে শতকরা পরিমাণে প্রকাশ, 1 PPM = 0.0001%
# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন
নরমলিটি
মোলালিটি
মোলারিটি
কোনটিই নয়
Read more