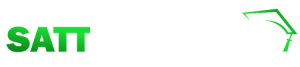ফল আমাদের দেশের একটি জনপ্রিয় উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল । মানুষের খাদ্য তালিকায় ফল একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে । কিন্তু বাংলাদেশে ফলের উৎপাদন যথেষ্ট নয় বলে এর গুরুত্ব সেভাবে বিবেচনা করা হয় না । তবে কোনো দেশের জীবন যাত্রার মান নির্ভর করে সে দেশের মানুষের দৈনিক মাথাপিছু ফল খাওয়ার পরিমাণের ওপর । মরণাতীত কাল হতেই ফল আবাল বৃদ্ধবনিতা সকল মানুষের নিকট সুখাদ্য হিসেবে পরিচিত ও সমাদৃত । খ্রিষ্টপূর্ব ৭০০০ বছর পূর্বে খেজুর চাষ এর সাক্ষ্য বহন করে । মুঘল সম্রাট আকবর কর্তৃক এক লক্ষ আম গাছের বাগান তৈরি, পর্তুগিজদের দ্বারা ভারতীয় উপমহাদেশে আনারস ও পেঁপে চাষের প্রবর্তন ইত্যাদি হতে বোঝা যায় যে ফলের প্রতি মানুষের আগ্রহ অতীত কাল থেকেই ছিল । বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থে ফলকে বেহেস্তি খাবার হিসেবে চিহ্নিত করা হয় । ফলের স্বাদের প্রতি আমরা সবাই অনুরাগী হলেও অনেকে এর পুষ্টি মূল্য এবং ফল খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল নই। ফল মানুষের পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থে ভরপুর । অন্যান্য খাবারের পরিপূরক হিসেবে ফল খাওয়া যায়। অধিকাংশ ফল দেখতে আকর্ষণীয়, সুস্বাদু এবং সকলের কাছে পছন্দনীয়। ফল রান্না ছাড়া সরাসরি খাওয়া যায় বলে এর পুষ্টিমান নষ্ট হয় না । তাই ফলের ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সবটুকুই শরীর গ্রহণ করতে পারে । ফল প্রচুর পরিমাণ খেলেও তেমন কোন অসুবিধা হয় না এবং পুষ্টিতে কোন সমস্যা থাকে । ফলে বিশেষ করে ক্যারোটিন (যা ভিটামিন 'এ' তে রূপান্তরিত হয়), ভিটামিন 'সি', ক্যালসিয়াম, লৌহ ও অন্যান্য উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে আছে । তাই মানব দেহের পুষ্টিতে ফলের অবদান অনেক বেশি। খাদ্য ঘাটতি পূরণেও ফল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে । উন্নত দেশের মানুষ আমাদের তুলনায় বেশি পরিমাণে ফল খায় বলে তাদের স্বাস্থ্য অনেক ভালো, সুঠাম দেহের অধিকারী এবং তারা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে।
পুষ্টিহীনতা দূরীকরণে, চিকিৎসা কাজে, খাদ্য ঘাটতি পূরণে, নুতন শিল্প স্থাপনে, কাজের সুযোগ সৃষ্টিতে, আয় বৃদ্ধিতে, জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে, সামাজিক কর্মকাণ্ডে, রুচির পরিবর্তনে এবং পরিবেশ সংরক্ষণে ফল বিভিন্ন ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে ।
আমাদের প্রতিদিন মাথাপিছু কমপক্ষে ১১৫ গ্রাম করে ফল খাওয়া উচিত। কিন্তু সেখানে আমরা পাই প্ৰায় ৩৮ গ্রাম । বাংলাদেশে ফল চাষের আওতায় জমির পরিমাণ এবং মোট উৎপাদনের পরিমাণ খুব ধীরগতিতে বৃদ্ধি পাছে । অপরদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি হওয়ায় মাথাপিছু ফল খাওয়ার পরিমাণ বাড়ার চেয়ে কমে যাচ্ছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ ফলই ব্যবসায়িক বা বাজার চাহিদার ভিত্তিতে বেশি করে চাষাবাদ করা যায় না । যার ফলে প্রকৃতপক্ষে চাষের আওতায় জমির পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন । মনে করা হয় বাংলাদেশের মোট চাষভুক্ত জমির মধ্যে ফলের আওতায় ১ - ২ % জমি আছে। অথচ জাতীয় অর্থনীতিতে মোট ফলভিত্তিক আয়ের ১০% আসে ফল থেকে। বর্তমান বিশ্বে ফলের পুষ্টি মূল্য ছাড়াও ফলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব যথেষ্ট । বাজারে ফলের চাহিদা ছাড়াও মূল্য বেশি বিধায়, এটি চাষাবাদে অতিরিক্ত আয় নিশ্চিত হয়। যার ফলশ্রুতিতে ফল উৎপাদনের সাথে জড়িত সম্প্রদায়ের আর্থিক সচ্ছলতা আসে ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় । অধিক ফল উৎপন্ন করে এবং তা রপ্তানি করে দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা করা সম্ভব ।
বিভিন্ন ফলের পরিচিতি ও তালিকা তৈরি
ফলের সংজ্ঞা ও প্রকার ভেদ
উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের মতে ফল হলো ফুলের নিষিক্ত এবং পরিণত ডিম্বাধার । ফল গঠনে নিষেক উদ্দীপকের কাজ করে । আর সে জন্যই নিষেকের পর হতেই ফুলের গর্ভাশয় বা ডিম্বাশয়টি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে ধীরে ধীরে পরিপূর্ণতা লাভ করে পূর্ণাঙ্গ ফলে পরিণত হয় । ডিম্বাশয়টি বীজ ধারন করে । নিষিক্তকরণ ছাড়াও ফুলের ডিম্বাশয় বা অন্য কোন অংশ বর্ধিত ও পরিপষ্ট হয়ে ফলে পরিণত হতে পারে। কলা, আপেল, চালতা, হলো এমন ধরনের ফলের উদাহরণ । নিষেক ক্রিয়া ছাড়া সৃষ্ট ফলে বীজ হয় না। সচরাচর ফল একটি মাত্র ফুল হতে উৎপন্ন হয় । কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ফুলের সমপূর্ণ অংশ যেমন – বৃত্তি, পাপড়ি, পুপাক্ষ, সম্পূর্ণ পুষ্প মঞ্জুরী - ফল গঠনে অংশগ্রহণ করে ।
ফুলের পুংকেশরের পরাগধানী হতে তৈরি পরাগরেণু পুংজনন কোষ উৎপন্ন করে। অন্যদিকে স্ত্রীকেশরের ডিম্বাশয়ের ভেতরে অবস্থিত ডিম্ব থেকে উৎপন্ন হয় স্ত্রীজনন কোষ । উপযুক্ত পুং এবং স্ত্রী জননকোষ একত্রে মিলিত হওয়াকে নিষেক বলে। নিষেকের পূর্বে পুংকেশরের পরাগ রেণু স্ত্রীকেশরের গর্ভমুন্ডে বিভিন্ন উপায়ে পতিত হয় । এ পতিত হওয়াকে পরাগায়ন বলে । ফুল হতে ফল গঠনে নিষেক প্রক্রিয়ায় ফুলের বিভিন্ন অংশের অংশগ্রহণের ওপর ভিত্তি করে ফলকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় । যথা – ক) প্রকৃত ফল ও খ) অপ্রকৃত ফল ।
ক) প্রকৃত ফল: নিষেকের পর ফুলের শুধু ডিম্বাশয়টি ফলে পরিণত হলে তাকে প্রকৃত ফল বলে । এতে ফুলের অন্য কোন অংশ ফল গঠনে অংশগ্রহণ করে না। যেমন – আম, জাম, নারিকেল, লিচু, পেঁপে, পেয়ারা ইত্যাদি ।
খ) অপ্রকৃত ফল: নিষেকের পর ফুলের সাহায্যকারী অংশসমূহ ফল গঠনে অংশগ্রহণ করে যে ফল গঠন করে তাকে অপ্রকৃত ফল বলে । এতে ফুলের সাহায্যকারী অংশসমূহ যেমন— — বৃতি, দলমণ্ডল ইত্যাদি ফল গঠনে অংশগ্রহণ করে । যেমন – আপেল, কাঁঠাল, চালতা, আতা ইত্যাদি। এছাড়াও আর এক ধরনের ফল পাওয়া যায় । যথা পারথেনাকোরপিক ফল ।
গ) পারথেনোকারপিক ফল: এ ফলে ডিম্বাশয় নিষিক্ত না হয়ে ফলে রূপান্তরিত হয় । এতে কোন বীজ থাকে না । যেমন—আনারস, আঙ্গুর, কলা ইত্যাদি ।
সাধারণত একটি আদর্শ ফলের দুটি অংশ থাকে । যেমন – ক) ফলত্বক ও খ) বীজ
ক) ফলত্বক ও এটি ফুলের গর্ভাশয়ের প্রাচীর বা বহিরাবরণ । আদর্শ ফলের ফলত্বক সাধারণত দু'ধরনের । (১) পুরু ও রসালো এবং (২) পাতলা ও শুস্ক
১। পুরু ও রসালো
এ ফলত্বককে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। উদাহরণ- আম, জাম, কুল ইত্যাদি এ ধরনের ফল। ভাগ গুলো হলো- (ক)- বহিত্বক (খ)- মধ্যত্বক ও (গ) - অন্তত্বক
ক) বহিত্বকঃ এটি ফলের সবচেয়ে বাইরের স্তর । এ স্তর মসৃণ ও চামড়ার ন্যায় ।
(খ) মধ্যত্বক: এ স্তর বহিত্বকের নিচের স্তর। এ তর মাংসল ও রসালো। তবে ফলভেদে এই মাংসল স্তরের পুরুত্ব কম বা বেশি হতে পারে।
(গ) অন্তত্বক: এ স্তর ফলের সবচেয়ে ভেতরের স্তর। পরিপুষ্ট ফলে এ স্তর বেশ গুরু ও শক্ত হয়। এ স্তর বীজপত্রকে আবৃত করে রাখে ।
২। পাতলা ও শুস্ক ত্বক
ফলের এ ত্বক পাতলা ও এ এবং বীত্বক ফলত্বকের সাথে লেগে থাকে। বীজত্বক ও ফলত্বক বাদে বাকি অংশ অন্তবীজ বা শস্য । উদাহরণ- ধান, গম, ভুট্টা, সরগাম, চিনা, কাউন ইত্যাদি ।
ক) বীজঃ এটি অন্তত্বক দ্বারা আবৃত থাকে। বীজে দুটি পুরু ও মাংসল বীজপত্র থাকে। কিন্তু বীজপত্র কিছুটা শক্ত।
ফলের শ্রেণিবিন্যাস
ফলের পরিচিতি ও ফল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জনের জন্য ফলের শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে কিছুটা জানা আবশ্যক। কেননা ফলকে বিভিন্নভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—
১। ফলের বীজপত্রের (Cotyledon) সংখ্যার ভিত্তিতে
ক) একবীজপত্রী ফল ভাল, নারিকেল, সুপারী, খেজুর ইত্যাদি ।
খ) দ্বিবীজপত্রী ফল: আম, গাব, কাঁঠাল ইত্যাদি ।
গ) বহু বীজপত্রী ফল পেঁপে, কাঁঠাল, পেয়ারা, তরমুজ ইত্যাদি ।
পরাগায়ণের ভিত্তিতে
ক) স্ব - পরাগী ফল ও আমলকী, পেয়ারা, আংগুর, সফেদা, ডুমুর ইত্যাদি
খ) পর পরাগী ফল আম, জাম, লিচু, পেঁপে, তাল, সুপারী খেজুর, আনারস, কূল, অ্যাভোকেডো ইত্যাদি ।
গ) স্ব ও পর পরাগী ফল কাঁঠাল, নারিকেল, লেবু জাতীয় ফল, কাজুবাদাম, ডালিম ইত্যাদি ।
৩। জীবনকালের ভিত্তিতে
ক)স্বল্প মেয়াদি ফল: কলা, পেঁপে, আনারস, তরমুজ ইত্যাদি
খ) দীর্ঘমেয়াদি ফল: আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল ইত্যাদি
৪। গাছের ফল প্রদানের প্রকৃতি অনুসারে
ক) মনোকারণিক ফল: কলা, শসা, তরমুজ, বাঙ্গী ইত্যাদি।
খ) পলিকারণিক ফল: আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি।
৫। উৎপত্তি বা উৎস অনুসারে
ক) প্রকৃত ফল আম, জাম, কালোজাম, লিচু, লেবু, পেঁপে ইত্যাদি
খ) অপ্রকৃত ফল: আপেল, নাশপাতি, কাজুবাদাম ইত্যাদি ।
গ) পারথেনোকারণিক ফল: আনারস, আঙ্গুর, কলা ইত্যাদি।
৬। পুষ্পমঞ্জুরীর ভূমিকার ওপর ভিত্তি করে
ক) সরল ফলঃ আম, জাম, নারিকেল, কলা ইত্যাদি ।
খ) যৌগিক ফল: যৌগিক ফল আবার দু'প্রকার
i) এগ্রিগেট বা গুচ্ছ ফল: আতা, শরীফা, রাস্পবেরী, কাঁঠালী চাপা ইত্যাদি
ii) মাল্টিপল ফল কাঁঠাল, আনারস ইত্যাদি।
৭। পেরিকার্পের বুনটের ওপর ভিত্তি করে (Texture of the pericarp)
ক) নীরস বা শুষ্ক ফল : কাঠবাদাম, সুপারি, এপ্রিকট ইত্যাদি ।
খ) সরস ফল: সরস ফল আবার পাঁচ প্রকার
i) ডুপ: আম, কুল, নারিকেল ইত্যাদি
ii) বেরী: কলা, পেয়ারা, কালোজাম, গোলাপজাম ইত্যাদি ।
iii) পামে: আপেল, নাশপাতি ইত্যাদি
iv) পেপো: শসা, তরমুজ, বাঙ্গি ইত্যাদি।
v) হেসপেরিডিয়াম: কমলা লেবু, কাগজী লেবু, বাতাবী লেবু ইত্যাদি ।
৮। জলবায়ুর চাহিদার ওপর ভিত্তি করে
ক) উষ্ণ মণ্ডলীয় ফল খেজুর, অ্যাভোকেডো, কলা, নারিকেল, আম, কাঁঠাল ইত্যাদি
খ) অউষ্ণমণ্ডলীয় ফল: পেয়ারা, ডালিম, কুল, কলা, জলপাই, লেবু জাতীয় ফল, অ্যাভোকেডো ইত্যাদি ।
গ) শীত মণ্ডলীয় ফল: স্ট্রবেরী, রাশবেরী, পীচ, ইউরোপীয় আঙ্গুর ইত্যাদি ।
বাংলাদেশের ফলের তালিকা
বালাদেশে উৎপন্ন ফলগুলোর ধরন ও গোত্র অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ করে নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ তালিকা দেয়া হলো
ক) আম গোত্র ভুক্ত: আম, আমড়া, বিলাতি আমড়া ও কাজু বাদাম।
খ) কাঁঠাল গোত্র ভুক্ত : কাঁঠাল, ভেটরা, ডুমুর, তুতফল, রুটীফল ও ডুরিয়ান ।
গ) লিচু গোত্র ভুক্ত: লিচু, আঁশফল ও রাম্বুটান।
ঘ) পেয়ারা গোত্র ভুক্ত: পেয়ারা, জাম, জামরুল ও গোলাপজাম ।
ঙ) অন্যানো জাতীয়: শরিফা ও আতা।
চ) সফেদা গোত্রভুক্ত: সফেদা, বকুল ও মহুয়া ।
ছ) লেবু জাতীয়: লেবু, কাগজি লেবু, জামির, বাতাবি লেবু, কমলা লেবু ও সাতকরা ।
জ) বেল জাতীয়ঃ বেল ও কদবেল ।
ঝ) টক-প্রধান: কুল, তেঁতুল, আমলকী, কামরাঙা, বিলিম্বি, জলপাই, চালতা, করমচা ও লৌহ ।
ঞ) আপেল জাতীয়: পিচ, নাশপাতি, চেরি ও ও ট্রপিক্যাল আপেল ।
ট) অন্যান্য বৃক্ষ জাতীয় ফল: অ্যাভোকেডো, বইচি, পানিয়াল, কাউফল, গাব, লটকন ও ডালিম ।
ঠ) লতা জাতীয়: প্যাসল ফল ও আঙ্গুর ।
ড) পাম জাতীয়: নারিকেল, তাল ও খেজুর ।
ঢ) অবৃক্ষ জাতীয়: কলা, পেঁপে, আনারস, তরমুজ, ফুটি, স্ট্রবেরি ও পানি ফল ।
এগুলোর মধ্যে ৫-৬টি ফল বিদেশ থেকে সাম্প্রতিককালে আনীত (প্যাকেন, রাম্বুটান, স্ট্রবেরি, অ্যাভোকোডা)
সারণি-১ দেশের মাটিতে সাম্প্রতিক প্রবর্তিত ও চাষযোগ্য বিদেশি ফল ও জাতের নাম
কয়েকটি বিদেশি ফলের পরিচয়
১. পিচ (Prunus persica)
এদেশে সৈয়দপুর, নীলফামারিতে প্রথম এক নার্সারিতে প্রচুর ফল ধরা পিচ ফলের একটি গাছ দেখে বিশ্বাস হয় যে এ দেশে পিচ ফল হওয়া সম্ভব । স্থানীয় বাসিন্দারা পীচ ফলের নাম বলেছিল মাজু ফল । এ নামে পিচ ফলের কোন বাংলা বা থানীয় নাম আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি । কিন্তু এর ইংরেজি নাম Peach, এ নামটাই এ দেশেও পরিচিত হয়ে উঠেছে। পরে অবশ্য সাভার, গাজীপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম ইত্যাদি এলাকায় ফলধরা বেশ কিছু পিচ ফলের গাছ চোখে পড়েছে। তবে প্রকৃতপক্ষে ফলটি শীতপ্রধান এলাকায় ভালো জন্মে । ভারতের সিমলাতে অনেক পীচ ফলের গাছ আছে। পিচ গাছ মাঝারি আকারের বৃক্ষ, পাতা অনেকটা ডালিম বা শরিফা পাতার মতো দেখতে । পাতার গোড়ায় অনেক ছোট ছোট পাতা থাকে । ফুলের রঙ লাল বা গালোপি । ফল দেখতে ডিম্বাকার তবে মুখটা আমের মতো বাকানো ও সুচালো । কাঁচা ফলের রঙ সবুজ পাকলে হালকা হলুদের ওপর লাল আভা সৃষ্টি হয় । কাচা ফল শক্ত, খোসা খসখসে। কিন্তু পাকলে নরম হয়ে যায় ও টিপ দিলে সহজে ভেঙে যায় । পাকা ফলের রসালো শাস হালকা হলুদ ও ভেতরের দিকে লাল, শাসের স্বাদ টক । ফলের মধ্যে খয়েরি রঙের একটা শক্ত বিচি থাকে । পিচ ফল পাকে মে - জুন মাসে । এক কেজি ফল থেকে প্রায় ৪৭০ ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায় । চোখ কলম করে পিচ ফলের বংশবৃদ্ধি সম্ভব ।
২. অ্যাভোকেডো
অ্যাভোকেডো আসলে আমেরিকার ফল । সে দেশে সুপ্রাচীনকাল থেকে অ্যাভোকেডো চাষ হয়ে আসছে । ইনকা সভ্যতার আমলেই অ্যাভোকেডোর পুষ্টি ও খাদ্যমান নির্ণিত হয়েছিল । এখন সারা বিশ্বে অ্যাভোকেডো ইংরেজি নামেই পরিচিত। বাংলা কোন নাম নাই। কিন্তু ফলটি যেভাবেই হাকে সমতল বাংলার মাটিতেও ফলে । গাজীপুরের কালিয়াকৈর, চাপাইনবাবগঞ্জে কল্যাণপুর হর্টিকালচার সেন্টার ও ময়মনসিংহের ভালুকায় লাগানো অ্যাভাকেডো বৃহৎ আকারের গম্বুজ আকৃতির চিরসবুজ গাছ। গাছ ১৮ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয় । পাতা সরল তবে আকার আকৃতিতে ভিন্নতা দেখা যায় । পাতা ১০-৪০ সেন্টিমিটার লম্বা হয়। ছোট ছোট হালকা সবুজ রঙের ফুল ফোটে থাকা ধরে। ছড়ায় ফুল ঝুলতে থাকে। ডালের আগায় সাধারণত ফুল ফোটে। অ্যাডভোকেডোর লাখ লাখ ফুল ফোটে, কিন্তু আমের মতোই ফল হয় খুব কম ফুল থেকেই । ফোটা ফুলের মাত্র ০.১ শতাংশ ফুল থেকে ফল হয় । কারণ দিনের এক সময় ফোটে পুরুষ ফুল, অন্য সময় ফোটে স্ত্রী ফুল । ফুল ফোটে শরতের শেষে এবং ফল পরিণত হতে ৬-১২ মাস লেগে যায়। অ্যাভোকেডো ফল বেশ বড়, প্রতিটি ফলের ওজন ১-৩ কেজি পর্যন্ত হয় । ফলের ভেতরে একটা বড় শক্ত বীজ থাকে বীজের চারদিকে থাকে শাস । শাঁসের ওপরে থাকে চামড়ার মতো খোসা। দেখতে অনেকটা নাশপাতির মতো আকার। তবে গোলাকার জাতেরও আছে । ফলের রং সবুজ বা হলদে সবুজ থেকে হলুদ ।
৩. স্টার আপেল
আজকাল প্রায়শই কিছু নার্সারির লোকেরা একটি গাছকে আপেল গাছ বলে চালিয়ে দিচ্ছে। যে গাছটিকে আপেল গাছ বলা হচ্ছে, সেটি আপেল নয়, তারকা ফলের গাছ। এ দেশে আপেল হবে না। কারণ আপেল জন্মাতে বছরের একটা নির্দিষ্ট সময় বরফ পড়তে হয় । তারকা ফলের নামের সাথে যে আপেল শব্দটা রয়েছে সেটা মুখে মুখে রটতে রটতে স্টার গিয়ে বসেছে আকাশের তারা হয়ে, হয়ে গেছে আপেল । তা ছাড়া তারকা ফল দেখতেও অনেকটা সবুজ আপেলের মতো। তাই, একে আপেলের ভাই বলে। এ দেশে আপেল হয় না সত্য তবে স্টার আপেল হয়। গাজীপুরে বিএআরআইয়ের উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রে স্টার আপেলের বয়সী গাছটাতে যেভাবে ডাল ভেঙে ফল ধরেছে, তাতে অবাক না হয়ে পারা যায় না। তা থেকে আশা করা যায় এ দেশেও ভালো ফল ফলতে পারে । তারকা ফলের গাছ বৃহৎ আকারের শোভাময়ী বৃক্ষ । গাছ ১০ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয় । পাতা দোরঙা । অর্থাৎ ওপরের পিঠ গাড় সবুজ ও নিচের পিঠ মেরুন বাদামি । পাতা কিছুটা ডিম্বাকার, বর্শার ফলার মতো ।
দ্রুত উৎপাদনশীল ফলের তালিকা
পৃথিবীতে শত শত প্রকার ফল জন্মে । এদের মধ্যে কতগুলো গ্রীষ্ম মন্ডলীয় (Tropical), কতগুলো প্ৰায়গ্ৰীষ্ম মন্ডলীয় (Subtropical) এবং কতগুলো নাতিশীতাষ্ণ জলবায়ু (Temperate) উপযোগী । অবশ্য কোন কোন ফল গ্রীষ্ম প্রধান হতে প্রায় গ্রীষ্মপ্রধান পর্যন্ত এবং কোনটি প্রায়গ্রীষ্ম প্রধান হতে নাতিশীতাষ্ণে জলবায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত । বাংলাদেশে গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের প্রায় সকল ফল এবং প্রায় গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলের কোন কোন ফল জন্মে । বাংলাদেশে অনেক ধরনের ফল গাছ জন্মে । তবে যে সব ফলের ব্যাপক চাষ হয় বা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চাষ করা হয় সেগুলো হচ্ছে - আনারস, কলা, পেঁপে, আম, লিচু, কাঁঠাল, পেয়ারা, কুল, তরমুজ, ফুটি, লেবু - জাতীয় ফল, নারিকেল ও স্ট্রবেরী । এগুলোর মধ্যে কলা, পেঁপে, আনারস, তরমুজ, ফুটি, দ্রুত বর্ধনশীল অবৃক্ষ ', জাতীয় ফল । কুল, পেয়ারা ইত্যাদি বৃক্ষ জাতীয় দ্রুত বর্ধনশীল ফল। পরিসংখ্যান অনুযায়ী এদেশের মোট উৎপাদিত ফলের প্রায় ৫০ ভাগের অধিক দ্রুত বর্ধনশীল স্বল্প মেয়াদী গাছ থেকে উৎপন্ন হয় । আবার দ্রুত বর্ধনশীল ফলের শতকরা ৭০ ভাগই হচ্ছে কলা । দ্রুতবর্ধনশীল ফল গুলোর মধ্যে আনারস, কলা, পেঁপে, তরমুজ ও ফুটি স্বল্প মেয়াদী ফল গাছ হিসেবে পরিচিত । কারণ খুব অল্প সময়েই অর্থাৎ কয়েক মাস থেকে শুরু করে এক বা দুবছরের মধ্যেই এগুলো ফল দিয়ে থাকে এবং খুব দীর্ঘস্থায়ী বা দীর্ঘজীবি নয় ।
কয়েকটি দ্রুত বর্ধনশীল ফলের পরিচিতি
১। আনারস (Pineapple )
আনারস টক-মিষ্টি, রসালো যৌগিক ফল যা সরোসিস নামে পরিচিত। এর উৎপত্তি হল দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল বা প্যারাগুয়ে অঞ্চলে । বাংলাদেশের টাঙ্গাইল (মধুপুর), সিলেট ও পাবর্ত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এর ব্যাপক চাষাবাদ হচ্ছে । আনারসের তিনটি জাত হানিকুইন, জায়ান্ট কিউ ও ঘোড়াশাল বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত । গাছ দ্বিবর্ষজীবি এবং একটি গাছ একবার মাত্র একটি ফল দিয়ে থাকে। পাঁচ রকমের সাকার দিয়ে অঙ্গজ পদ্ধতিতে এর বংশ বিস্তার করা হয় । যেহেতু বেশির ভাগ চারা আশ্বিন-কার্তিকে পাওয়া যায় সেহেতু চারাগুলো পৌষ মাঘে রোপণ করতে হয় । আনারসের শেকড় মাটির গভীরে যায় না । সুতরাং বাগানে আগাছা পরিষ্কার রাখা জরুরি । রোপণের পর ১৪-১৬ মাস বয়সের গাছে ফুল আসে । সাধারনত: ৬০ ভাগ গাছে ফল আসে । তবে ইথরেল ৫০০ পিপিএম বা ক্যালসিয়াম কার্বাইড ১০,০০০ পিপি এম প্রয়োগে শতকরা ৮০-৯০ ভাগ গাছে ফল আসে । হেক্টর প্রতি ৩০-৫০ টন ফলন হয় । যথাযথ পরিচর্যা করলে দুটি মুড়ি ফসল পাওয়া যায় ।
২। পেঁপে (Papaya )
পেঁপে উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় ভালো জন্মে । গাছ সারা বছরই ফুল ও ফল দিয়ে থাকে । সামান্য সময়ের জন্য হলেও জলাবদ্ধতা গাছের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে । পুরুষ ও স্ত্রীফুল আলাদা গাছে থাকে । পেঁপে পরপরাগায়িত ১. এবং বীজ দ্বারা বংশ বিস্তার হয়ে থাকে বলে অসংখ্য প্রকারের পেঁপে দেখা যায় । বিশেষ কোনো জাত আবাদ ও সংরক্ষণ করতে হলে নিয়ন্ত্রিত পরাগায়নের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন করা উচিত । প্রতি গর্তে তিনটি পেঁপে চারা রোপণ করা হয় । তাহলে প্রতি গর্তে অন্তত একটি স্ত্রী গাছ পাওয়া যায় । বাগানের শতকরা ন্যূনতম ৫ ভাগ পুরুষ গাছ পরাগায়নের সুবিধার্থে থাকা প্রয়োজন । সেচের ব্যবস্থা থাকলে আশ্বিন মাঘ মাস চারা রোপণের উত্তম সময় । তাছাড়া মৌসুমি বৃষ্টি শুরু হলে জ্যৈষ্ঠ মাস ভালো সময় । রোপণের ৪/৫ মাস পরে ফুল দেখে স্ত্রী বা পুরুষগাছ চেনা যায় । তখন গর্তে একটি স্ত্রী গাছ রেখে বাকিগুলো উপড়ে ফেলতে হয় । ফল ধরার দুমাস পরেই সবজি হিসেবে খাওয়া যায় । পাকা খাওয়ার জন্য গাছে পেঁপের গায়ে একটু হলুদ রং দেখা দিলেই আহরণ করা উচিত । পেঁপের ফলন গাছ প্রতি ১৫-২৫ কেজি এবং হেক্টর প্রতি ৩০--৩৫ টন হতে পারে ।
৩। কলা (Banana )
কলা উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলের ফল । কলা সাধারণত পাকা ফল হিসেবে খাওয়া হয় । কলার অনেক জাত আছে যেগুলো সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। আফ্রিকার অনেক উপজাতির প্রধান খাদ্য কলা। কলাচাষের অনুকূল তাপমাত্রা ১৫-৩৫° সেলসিয়াস। প্রতিমাসে ২০ সে.মি. বৃষ্টিপাত গাছের বৃদ্ধির জন্য উত্তম । কলাগাছ ঝড়াবোতাস সহ্য করতে পারে না। কলার সাধারণত অঙ্গজ পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার হয়ে থাকে । কলার জাতসমূহ তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত যথা-১ । পাকা অবস্থায় ভক্ষণ যোগ্য বীজহীন জাতসমূহ ২। বীচি কলা বা আটি কলার জাতসমূহ ৩। আনাজী বা সবজি হিসেবে ব্যবহৃত কলার জাতসমূহ । সেচের ব্যবস্থা থাকলে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর বা জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে সাকার রোপণের উত্তম সময় । মুড়ি ফসল কলাচাষের একটি বাড়তি সুবিধা । হেক্টর প্রতি সাধারণত ২০-২৫ টন ফলন পাওয়া যায় ।
ফল গাছের বাংলা, ইংরেজি ও উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম
পৃথিবীতে বহু ধরনের ভাষা প্রচলিত থাকায় একই উদ্ভিদ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত । যেমন — আম, গাছকে বাংলায় আম বা আম্র, গুজরাটিতে আমরি, পুর্তুগীজে ম্যাংগা, ফরাসীতে ম্যাংগু, চীনা ভাষায় ম্যাংকে, এবং ইংরেজিতে ম্যাংগো বলা হয় । শুধু তাই নয় দেখা গেছে একই ভাষা ভাষীরাও একই ফলকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করে থাকে। তাই এ অসুবিধা দূর করার জন্য International Code of Binomial Nomenclature (ICBN) নীতি অনুসরণ করে প্রতিটি উদ্ভিদের আন্তর্জাতিকভাবে নামকরণ করা হয়েছে । উক্ত নামটি ল্যাটিন ভাষায় এবং রোমান অক্ষরে লিখতে হয় । অন্য ভাষায় হলে লাটিনের মত করে লিখতে হয় । প্রতিটি নামের দুটি অংশ আছে - একটি জেনেটিক ইপিথেট বা গণের অংশ অপরটি স্পেসিস ইপিথেট বা প্রজাতির অংশ । জেনেটিক অংশ বড় হাতের অক্ষর দিয়ে শুরু হয় । উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ল্যাটিন শব্দে না লেখা হলে জেনিটিক ও স্পেসিস নামের নিচে পৃথক পৃথকভাবে দাগ (Under line) দিতে হবে । উদ্ভিদতাত্ত্বিক নামের শেষে এর প্রবর্তকের নামও লিখতে হয় । এটিই দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতি । নিচের সারণিতে ফল গাছের বাংলা, ইংরেজি, উদ্ভিদতাত্ত্বিক ও পরিবারের নাম দেয়া হলো
সারণি-২ ও ফল গাছের বাংলা, ইংরেজি, উদ্ভিদতাত্ত্বিক ও পরিবারের নাম
অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
১ । আমাদের প্রতিদিন মাথাপিছু কমপক্ষে কত গ্রাম ফল খাওয়া উচিত ।
২। বাংলাদেশের মোট চাষভুক্ত জমির মধ্যে ফলের আওতায় জমির পরিমাণ শতকরা কতটুকু ?
৩। নিষেক প্রকিয়ার উপর ভিত্তি করে ফলকে কত ভাগে ভাগ করা যায় ।
৪ । আমাদের দেশে স্বল্প মেয়াদী ফল কোনগুলো।
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
১। ফল বলতে কি বোঝায় ?
২। নিষেক প্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে ফলকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় ?
৩। আদর্শ ফলের কয়টি অংশ থাকে চিত্র অঙ্কন করে দেখাও ।
৪। মানুষের পুষ্টি সরবরাহে ফল কীভাবে অবদান রাখে লেখ ।
৫ । উদ্ভিদ তাত্ত্বিক নামসহ ৫টি ফলের বাংলা ও ইংরেজি নাম লেখ ।
রচনামূলক প্রশ্ন
১ । ফল বলতে কি বোঝায়। ফলের শ্রেণি বিন্যাস গুলোর নাম লেখ এবং প্রত্যেকটির উদাহরণ দাও ।
২। বাংলাদেশে প্রচলিত দেশি ফলের একটি তালিকা তৈরি কর ।
৩। বাংলাদেশের মাটিতে সাম্প্রতিক প্রবর্তিত চাষযোগ্য ১০টি বিদেশি ফলের নাম, উদ্যানতাত্ত্বিক নাম, পরিবার, জাত ও উৎপত্তি স্থান লেখ ।
৪ । টিকা লেখ: ক) প্রকৃত ফল খ) অপ্রকৃত ফল গ) মনো ও পলিকারপিক ফল ঘ) উদ্যানতাত্ত্বিক ফল ঙ) একবীজপত্রী ফল চ) ব - পরাগী ও পরপরাগী ফল ।
অধিকাংশ ফল দীর্ঘমেয়াদি ফসল হিসেবে বিবেচিত । এ জন্য কোনো স্থানে ফল বাগান স্থাপন করতে হলে সেই জায়গার পরিবেশ, জলবায়ু ও মাটি সম্বন্ধে অবশ্যই সম্যক ধারণা থাকতে হবে । ফল বাগানের জন্য উঁচু জমি, যেখানে বৃষ্টির পানি দাঁড়ায় না বা পানি নিকাশের ভাল ব্যবস্থা আছে এ রকম খোলামেলা জায়গা ফল বাগানের জন্য নির্বাচন করা উচিত ।
প্রত্যেক ফল গাছই একটি নির্দিষ্ট পরিবেশ ও মাটি পছন্দ করে । তাই গাছের উপযোগী পরিবেশ ও মাটি নির্বাচন করতে হবে । এছাড়াও ফল বাগান স্থাপনের সুষ্ঠু পরিকল্পনা খুব প্রয়োজন । কারণ স্বল্পমেয়াদি ফসলের ক্ষেত্রে কোন ভুলত্রুটি হলে তা পরবর্তী সময়ে সহজে সংশোধন করা যায় । কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদী বৃক্ষ জাতীয় ফল বাগান প্রতিষ্ঠার সময় কোন ভুলত্রুটি থাকলে তা পরবর্তীতে সংশোধনের সুযোগ থাকে না । এ জন্য বৃক্ষ জাতীয় ফল চাষের জন্য বাগান বিন্যাস, গাছ নির্বাচন, বাজারজাতকরন, সেচ, পানি নিস্কাশন, কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা, ফল প্রক্রিয়াজাতকরন, শ্রমিক সরবরাহ, সুষ্ঠু বাগান ব্যবস্থাপনা, ফলের জাত, গাছের আকার আকৃতি ও বৃদ্ধির প্রকৃতি ইত্যাদি মৌলিক বিষয়াবলি সম্বন্ধে একজন আধুনিক ফলচাষীর অবশ্যই তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক জ্ঞান থাকতে হবে ।
জলবায়ু, জমি ও মাটিভেদে ফল গাছের শ্রেণিবিভাগ
ফলের ফলন নির্ভর করে তার সঠিক চাষাবাদ পদ্ধতির ওপর । চাষাবাদ পদ্ধতির ধরন এবং এর বাস্তবায়ন আবার নির্ভর করে স্থানীয় জলবায়ু, জমি, মাটি ও গাছের প্রকৃতি ইত্যাদির ওপর । ফল দীর্ঘমেয়াদি ফসল বিধায় কোন স্থানে বাগান স্থাপন করার পূর্বে চাষীদের অবশ্যই সেই জায়গার পরিবেশ, জলবায়ু ও মাটি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকা দরকার । এছাড়া ফল বাগান স্থাপনের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা খুবই প্রয়োজন । স্বল্পমেয়াদী ফসলের ক্ষেত্রে কোন ভুল ত্রুটি হলে তা পরবর্তীতে সংশোধনের সুযোগ থাকে তাছাড়া ক্ষতি হলেও ক্ষতির পরিমাণ কম হয় । কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী ফসলের ক্ষেত্রে সেই সুযোগ থাকে না এবং ক্ষতির পরিমান বেশি হয় । সুতরাং ফল চাষাবাদের জন্য জলবায়ু ভেদে উপযুক্ত গাছ নির্বাচন, মাটি নির্বাচন, বিভিন্ন আন্তঃপরিচর্যা সম্পাদন, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার ।
কোন নির্দিষ্ট আবহাওয়ায় সব ধরনের ফলের চাষ করা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন ফল চাষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আবহাওয়ার প্রয়োজন হয় । তবে খুব বেশি বা খুব কম তাপমাত্রায় কোন গাছ ভালভাবে জন্মাতে পারেনা । ফলের বাগান যে এলাকায়ই হাকে না কেন, মাঝে মাঝে প্রতিকুল আবহাওয়ার মুখোমুখি হতে হয়। সে সময় কিছু কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন হয় ।
কোন স্থানের তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বাতাসের গতিবেগ, বাতাসের আর্দ্রতা, শিলাবৃষ্টি, আলো, কুয়াশা ইত্যাদির দৈনিক পরিবর্তনকে ঐ স্থানের আবহাওয়া বলে । কোন স্থানের আবহাওয়ার কয়েক বছরের গড়কে সে স্থানের জলবায়ু বলে। কোন স্থানের জলবায়ুর সাথে ঐ স্থানের ফল চাষের সরাসরি সম্পর্ক আছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ ফল গাছ প্রায় সব জায়গায় জন্মাতে পারে। কারণ বাংলাদেশের একস্থান হতে অন্যস্থানের আবহাওয়ার মধ্যে তেমন বেশি পার্থক্য নেই । তাই বাংলাদেশের সব ফল সব এলাকায় কমবেশি জন্মানো যাবে এবং ফল ধরবে । আমাদের দেশে এলাকা বিশেষে আবহাওয়ার তারতম্য কিছুটা আছে, বিধায় স্থান বিশেষে কোন কোন ফল বেশি লাভজনকভাবে জন্মানো যায় । এছাড়া এলাকা বিশেষে ফলের গুণাবলির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় । কেননা ফল গাছে ফল ধরার জন্য মাটি ও আবহাওয়ার বিভিন্ন প্রভাবকগুলো কাজ করে । মাটির প্রভাবকগুলো আধুনিক প্রযুক্তি ও নতুন নতুন কৌশল দ্বারা অনেকক্ষেত্রে পরিবর্তন করা সম্ভব হয় । আবহাওয়ার প্রভাবক গুলোর পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না । তাই আবহাওয়ার প্রভাবক গুলোর ওপর নির্ভর করে ফলকে চার ভাগে ভাগ করা যায়-
ক) গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের ফল
খ) অব গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের ফল
গ) শীতপ্রধান অঞ্চলের ফল
ঘ) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ফল
ক) গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলের ফল
বিষুব রেখার ২৩-২৭০ হতে ২৩-২৭০ উত্তর দক্ষিণ অংশের মধ্যবর্তী এলাকায় যে সব ফল জন্মে সেগুলোকে গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলের ফল বলে। উদাহরণ - আম, পেঁপে, কলা, আনারস, নারিকেল, কাঁঠাল ইত্যাদি । গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে সারা বছর উচ্চ তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বজায় থাকে এবং দিনের দৈর্ঘ্য ১১ থেকে ১৩ ঘন্টার মধ্যে সীমিত থাকে । বাংলাদেশে বেশির ভাগ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ফল উৎপন্ন হয় ।
খ) অগ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলের ফল
২৩.২৭° হতে ৪০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যবর্তী এলাকায় যেসব ফল জন্মে সেগুলোকে অব গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলের ফল বলে। এ অঞ্চলে নির্দিষ্ট সময় ধরে শীতকাল বিরাজ করে। কিন্তু শীত তেমন তীব্র হয় না এবং তাপমাত্রা বরফ জমা অবস্থায় নামে না। এ এলাকার ফলগুলো হলো- কমলা লেবু, লিচু, কুল, খেজুর, ডুমুর, ডালিম, নাশপাতি, আঙ্গুর ইত্যাদি ।
গ) শীত প্রধান অঞ্চলের ফল
৪০ হতে ৬০° উত্তর দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যবর্তী অঞ্চলে যে সব ফল জন্মে সেগুলোকে শীতপ্রধান অঞ্চলের ফল বলে । এ অঞ্চলে আবহাওয়ায় শীতের তীব্রতা থাকে । শীতপ্রধান অঞ্চলের ফলগাছে ফুল ও ফল ধরার পূর্বে কিছুদিনের জন্য গাছকে বরফজমা তাপমাত্রায় অতিবাহিত করতে হয়। শীতপ্রধান অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা ১৮-২১° সেলসিয়াস ও শীতকালে ৬-৯° সেলসিয়াস থাকে । এ অঞ্চল বছরের প্রায় ৫০ থেকে ৭৫ দিন তুষার মুক্ত থাকে। এ অঞ্চলের ফল গাছের পাতা বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঝরে পড়ে যায় । তবে শীত প্রধান অঞ্চলের ফলগাছ তীব্র শীত সহ্য করতে পারে। এ অঞ্চলের ফল গুলো হলো- আপেল, পাঁচ, নাশপাতি, স্ট্রবেরি, আঙ্গুর, চেরী, পারসিমন ইত্যাদি ।
ঘ) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ফল
ভুমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে শুষ্ক এবং শীতকালে বৃষ্টি হয় । গ্রীষ্মকালে রাত্রে অতিরিক্ত কুয়াশা পড়ে এবং রাত্রিকালীন বাতাসে আর্দ্রতা বিরাজ করে। অধিকাংশ ফলই এ অঞ্চলে ভালোভাবে জন্মে থাকে । তবে এ অঞ্চলে ফলগাছে দুইবার সুপ্ততা দেখা যায়। যেমন—শীতকালে প্রচণ্ড ঠান্ডার সময় একবার এবং গ্রীষ্মকালে খরার সময় আর একবার শীতকালের বৃষ্টিপাত গাছের বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়ক হয়। এ অঞ্চলের ফলগুলো হলো- খেজুর, ডালিম, কমলা, জলপাই, আঙ্গুর, ডুমুর ইত্যাদি ।
ফল গাছ রোপণের সময় বা মৌসুম এবং চারা রোপণ ও পরবর্তী পরিচর্যা
আমাদের দেশে মে থেকে জুলাই মাস অর্থাৎ গ্রীষ্মের শেষ এবং বর্ষার প্রথম ভাগ ফল গাছের চারা রোপণের উপযুক্ত সময় । কারণ এ সময় পরিমাণ মত বৃষ্টি হয় এবং বাতাসে এবং মাটিতে প্রচুর আর্দ্রতা থাকায় গাছ সহজে মাটিতে লেগে যায়। যে সব জায়গায় পানি সেচের উত্তম ব্যবস্থা আছে, সেখানে বসন্তের প্রথম ভাগে চারা রোপণ করা যায় । বৃষ্টি না হয়ে থাকলে চারা রোপণের পূর্বদিন গর্তে কিছু পানি সেচ দেয়া যেতে পারে । রোপণের জন্য বিকাল প্রকৃষ্ট সময় । চারার শেকড় যতখানি বিস্তৃত ও গভীর ততখানি বিস্তৃত ও গভীর করে গর্তের মাটি উঠিয়ে নিয়ে গর্তে চারার নিম্নাংশ প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে। তারপর মূলগুলোকে গর্তের মধ্যে বেশ ভালো ভাবে ছড়িয়ে দিয়ে আস্তে আতে মাটি চাপা দিতে হবে । চারা রোপণের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন রোপিত চারার গর্ত জমি হতে উঁচু হয় । তা না হলে বর্ষাকালে গর্তের মাটি বসে গিয়ে চারার চারদিকে পানি জমে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করবে । চারা যাতে সহজে খাড়া থাকতে পারে এজন্য রোপণের পর চারার পাশে খুটি পুঁতে খুটির সাথে চারা বেধে দিতে হবে । চারা রোপণের অব্যবহিত পরে এবং প্রথম কিছুদিনের জন্য প্রতিদিন ঝাঝরি দ্বারা চারার গোড়ায় পানি দ্বারা সেচ দেয়া উচিত । তা ছাড়া চারা রোপণের পর অতিরিক্ত সূর্যালোকের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য চারার উপরে ছায়া প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং গোড়ায় শুষ্ক ঘাস, খড় ইত্যাদি চেপে দিতে হবে ।
চারা রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা
জমিতে চারা রোপণের পর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত চারাটির যত্ন নিতে হবে যাতে করে তা মাটিতে সহজে লেগে তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায় । এ জন্য চারার গোড়ায় বেশ কিছুদিন ঝরণা দিয়ে পানি দিতে হবে । বর্ষা মৌসুমে চারার গোড়ায় কোন কারণে পানি জমলে তা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিতে হবে । এছাড়াও চারার গোড়ার মাটি শক্ত হয়ে গেলে তা নিড়ানী দিয়ে ঝুরঝুরে করে দিতে হবে । চারার গোড়ার আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে । শুষ্ক মৌসুমে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে । এছাড়া শুষ্ক মৌসুমে পানি সেচের ব্যবস্থা না থাকলে চারার গোড়ার চারপাশে শুকনা খড়, ঘাস ইত্যাদি বিছিয়ে দিতে হবে । এভাবে মাটিতে পানি সংরক্ষণের পদ্ধতিকে মালচিং বলা হয় । এছাড়া চারা গাছটি যাতে সোজা হয়ে বেড়ে উঠতে পারে সে জন্য বাঁশের খুটি দ্বারা গাছকে বেধে দিতে হবে। অনেক সময় চারা গাছের গোড়া থেকে শাখা প্রশাখা বের হয় । প্রয়োজন মোতাবেক শাখা প্রশাখা রেখে বাকীগুলো ছাঁটাই করে ফেলতে হবে । গাছের প্রজাতি অনুসারে চারার প্রুনিংয়ের (Pruining বা ছাঁটাই) ব্যবস্থা করতে হবে । অনেক সময় খুব অল্প সময়ে কলমের চারা গাছে ফুল আসে । যার ফলে চারা গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে । এসব অনাকাঙ্ক্ষিত ফুল ছাঁটাই করে ফেলতে হবে । বৎসরে দুবার গাছে সার প্রয়োগ করতে হবে । প্রাথমিক অবস্থায় পরিমাণ সার প্রয়োগ করা হয়েছে সেই পরিমাণ সার সমান দু'ভাগে ভাগ করে বর্ষার শুরুতে এবং বর্ষার শেষে প্রয়োগ করতে হবে। পরবর্তী সময় সারের পরিমান বৎসর ওয়ারী বৃদ্ধি করতে হবে । এভাবে চারা গাছ লাগানোর পর তা ফলবতী হওয়া পর্যন্ত যত্ন নিতে হবে । যাতে সুস্থ ও সবল গাছ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীতে কাঙ্ক্ষিত ফলন দেয় ।
ফল গাছ রোপণের জন্য জমির উপযুক্ততা
প্রত্যেক ফল গাছ একটি নির্দিষ্ট ধরনের মাটিতে ভাল ফলন দেয় । অত্যধিক বেলে মাটি এবং শক্ত ভারী এটেল মাটি ফল চাষের জন্য কিছুটা অনুপযুক্ত। আর এ ধরনের মাটিতে কম্পাষ্টে সার প্রয়োগ করে ফল গাছ রোপণ উপযোগী করে তোলা সম্ভব। কিন্তু এ কাজ সময় সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য। সব সময়ই বাগানের জন্য পানি নিকাশের সুবিধাযুক্ত মাটি প্রয়োজন । সাধারণত বেলে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা কম এবং এ মাটি অনুর্বর। এ ধরনের মাটিতে কুল, কাজুবাদাম, খেজুর প্রভৃতি ফল ভাল হলেও অন্যান্য অনেক ফল ভালভাবে জন্মাতে পারে না ।
অম্ল মাটিতে চুন, ডলোমাইট (ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট সমৃদ্ধ) প্রয়োগে অম্লতা কমানো যায় এবং ক্ষার বা লবণাক্ত মাটিতে জিপসাম (ক্যালসিয়াম সালফেট) প্রয়োগে ক্ষারত্ব প্রশমন করা যায় । টক জাতীয় ফুল গাছ যেমন— লেবু জাতীয়, আমড়া, অরবরই, আনারস প্রভৃতি অম্লযুক্ত লাল মাটি পছন্দ করে । নারিকেল গাছ লবণাক্ত মাটি বেশি পছন্দ করে । কাঁকুরে বা পাথুরে লাল (ল্যোটরাইট) মাটিতে আঙ্গুর, কুল ভাল হয় । ভেজা ও স্যাতসেঁতে মাটিতে কলা, আমড়া, লটকন, পেয়ারা ইত্যাদি ভাল হয় । পানি স্তর নিচে ও রং ধুসর এ ধরনের মাটিতে আম ভাল হয় ।
বাংলাদেশের বেশিরভাগ জমি সমতল । যে সমস্ত জমিতে বর্ষা বা বন্যার পানি একেবারেই দাড়ায় না সে সমস্ত স্থান কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, পেয়ারা ইত্যাদি ফল চাষের জন্য চিহ্নিত করতে হবে। আর যে সব জমি অল্প সময়ের জল প্লাবিত হয় সে সব জমিতে স্বল্প সময়ের জন্য জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে এমন ফল চাষ করা যেতে পারে । যেমন- আম, জাম, দেওফল, চালতা, গাব, খেজুর, বেত ফল ইত্যাদি ।
পাহাড়ি এলাকায় চাল ৪৫ এর কম হলে সেখানে ভালভাবে ফলের চাষ করা যায় । বেশি ঢাল পাহাড়ে বিশেষ পদ্ধতিতে গাছ লাগানো হয় । উচু পাহাড়ের উত্তর পাশে সূর্যের আলো বেশি পড়ে না, এ রকম স্থান ফল চাষের জন্য তেমন উপযোগী নয় । ফল চাষের জন্য যোগাযাগে ব্যবস্থা, জমির মূল্য, শ্রমিকের সহজলভ্যতা, বাজার ব্যবস্থা, বাগানে কাজের যন্ত্রপাতি, সেচ ব্যবস্থা, সার, বীজ ও ফল সংক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সহজে ও কম মূল্যে প্রাপ্তির বিষয় বিবেচনা করতে হবে ।
বাণিজ্যিক ফল চাষের জন্য এলাকা নির্বাচন অর্থাৎ নির্দিষ্ট ফলের জন্য অনুকূল জলবায়ু ও মাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । যেমন- মান সম্পন্ন ভাল আম ও লিচু দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে ভাল জন্মে । সমভূমি অপেক্ষা পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকার কাজুবাদাম, এ্যাভেক্যাডো, আঙ্গুর, কমলালেবু ইত্যাদি ভাল জন্মে । মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং সিলেট ও চট্টগ্রামের অম্লত্ব ও লালমাটি এলাকায় আনারস ভাল জন্মে। অনুরূপভাবে উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকা নারিকেলের জন্য সবচেয়ে উপযোগী । বাংলাদেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে ঝড় তুফানের প্রকোপ বেশি । তাই আম, কলা পেঁপে ইত্যাদি ফল গাছ সেখানে লাগানো হলে ঝড়ে খুব সহজেই ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে । তাই এসব ফল ঐ এলাকায় চাষ করা উচিত নয়। তবে কিছু কিছু অপ্রধান ফল যেমন- গাব, আমড়া, চালতা, জাম, ডেউয়া, দেওফল, লটকন ইত্যাদি স্যাঁতসেঁতে, বৃষ্টিবহুল ও ঝড়ো এলাকায়ও ভালভাবে টিকে থাকে এবং ফলন দিতে পারে । ফল চাষের জন্য দোঁআশ মাটি সবচেয়ে উপযোগী । অত্যধিক বেলে বা এটেল মাটি, বেশি লবণাক্ত বা বেশি অম্ল মাটি বাণিজ্যিকভাবে ফল চাষের জন্য নির্বাচন করা উচিত নয় ।
কলা গাছ রোপণের জন্য মাটির প্রকারভেদ
এক এক ধরনের ফল গাছ এক এক ধরনের নির্দিষ্ট পরিবেশ; তথা বিভিন্ন ধরনের ফল গাছ বিভিন্ন ধরনের মাটি, স্থান, জলবায়ু ও পরিচর্যা পছন্দ করে । এ ছাড়া ফল চাষের উদ্দেশের ওপর নির্ভর করে কিছু কিছু নিয়মাবলি অনুসরণ করতে হয় । যেমন—
ক) পারিবারিক চাহিদা মেটানোর জন্য ফল চাষ ।
খ) ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ফল চাষ ।
গ) সৌখিন ফল চাষ ।
ঘ) মিউজিয়াম হিসেবে ফল চাষ ।
ঙ) সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ফল চাষ ।
চ) প্রযুক্তিগত অবস্থার প্রেক্ষিতে ফল চাষ ।
এখানে ফলচাষের জন্য মাটি নির্বাচনে করণীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা কর হয়েছে । ফল গাছ মাটি হতে বিভিন্ন ধরনের পুষ্টি গ্রহণ করে থাকে। এ পুষ্টি সরবরাহের জন্য জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । সাধারণ ফসলের চেয়ে ফল গাছে প্রচুর খাদ্য, পানি ও পুষ্টির প্রয়োজন হয়। গাছ মাটি হতে সবসময় পুষ্টি গ্রহণের ফলে মাটিতে পুষ্টির ঘাটতি পড়ে এবং ফলের ফলন কমে যায় । গাছে সব সময় ও সব বয়সে এক ধরনের এবং একই পরিমাণ পুষ্টির দরকার হয় না । তাই গাছের জীবনকাল ও চাহিদা বিবেচনা করে সার প্রয়োগ করতে হয় । তবে অধিকাংশ ফল গাছই দীর্ঘ মেয়াদী । যেমন- আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল, তাল, বেল ইত্যাদি । গাছ গর্তে বসানোর সময় সার দেয়া হয় । এছাড়া প্রতিবছরই গাছে সার দিতে হয় । আবার বয়স বাড়ার সাথে সাথে সারের পরিমাণ পরিবর্তন করতে হয় । গাছের বাড়ন্ত সময় ও ফল ধরার আগে পরিমাণ মত সার দিতে হয় । অন্যথায় ফলন কমে যায় । বিজ্ঞানীরা ১৭টি উপাদানকে গাছের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন । এর মধ্যে যে কয়টি উপাদান গাছের জন্য বেশি পরিমাণে প্রয়োজন হয় সেগুলোকে মুখ্য উপাদান বলে। আর যেগুলো কম পরিমাণে প্রয়োজন হয় সেগুলোকে গৌণ উপাদান বলে । জীবন্ত গাছপালায় সাধারণত ৯৫% কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন থাকে । এগুলো বাতাসে যথেষ্ট বিদ্যমান বলে তেমন অভাব হয় না । অবশিষ্ট ৫% প্রয়োজনীয় উপাদান গাছ মাটি হতে শোষণ করে থাকে । এই অবশিষ্ট উপাদানের প্রাপ্তির ওপর ফলের ফলন নির্ভর করে থাকে ।
আমরা সাধারণত নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ জাতীয় সার প্রয়োগ করে থাকি । এগুলো মুখ্য উপাদান । অনুর্বর ও বৃষ্টিবহুল মাটিতে গৌণ উপাদানের খুবই অভাব দেখা যায় । কিন্তু এগুলো পরিমাণে কম লাগলেও ফলের ফলনের জন্য খুবই অত্যাবশ্যকীয় । তবে কোন মাটিতে কোন ধরনের পুষ্টি উপাদান ঘাটতি থাকতে পারে তা দেয়া হলো ।
মাটির অবস্থা | পুষ্টিগত অবস্থা |
| ১. কম জৈব পদার্থ সম্পন্ন মাটিতে | বেশির ভাগ উপাদান ঘাটতি থাকে |
| ২. বেলে মাটিতে | বেশির ভাগ উপাদান ঘাটতি থাকে |
| ৩. অম্ল মাটিতে | ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ঘাটতি থাকে |
| ৪. বার মাটিতে | লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ ও দস্তা ঘাটতি থাকে |
| ৫. অতি অম্ল ও ক্ষার মাটিতে | ফসফরাস, বোরণ ঘাটতি থাকে |
| ৬. পুরাতন লাল মাটিতে | পটাসিয়াম, সালফার ঘাটতি থাকে |
মাটির অবস্থাভেদে কোন উপাদানের ঘাটতি থাকার সম্ভাবনা থাকলে তা পূরণ না করে সেখানে ফলপ্রসুভাবে ফল চাষ করা সম্ভব হবে না । ফল চাষে মাটির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলির গুরুত্ব অনেক । ভৌত গুণাবলি বলতে মাটির মধ্যে বায়ু চলাচলের সুবিধা, মাটির মধ্যে ছিদ্র, মাটির কণার আকার এবং মাটির স্তর কত গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত তা বোঝায় । বৃক্ষজাতীয় ফল গাছের জন্য দুই মিটার গভীর পর্যন্ত সুনিষ্কাশিত মাটি সবচেয়ে ভাল । মাটির বুনট ভাল হলে পানি ধারণ ক্ষমতা, গাছের পুষ্টি উপাদান সরবরাহ এবং মাটির মধ্যে ছিদ্র বেশি থাকে । এতে গাছের শেকড় সহজে বৃদ্ধি পায় এবং খাদ্য শোষক শেকড় মাটির বেশি গভীর হতে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে ।
মাটির বুনট ভালো না হলে পানি নিষ্কাশন ঠিকমত হবে না । ফলে পানির উপরে উঠে আসে । মাটির ভেতর । পানিতর ফুল চাষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । পানির উপরে হলে মাটিতে ছিদ্র কমে যাবে, বায়ু চলাচলে অসুবিধা হবে এবং শিকড়ের শোষণ প্রক্রিয়া ব্যহত হবে। এমনকি এর ফলে শেকড় পঁচে যেতে পারে । যেমন— - কাঁঠাল, পেঁপে, আনারস, কলা, পেয়ারা ইত্যাদি । মাটির কণার আকৃতির ওপর নির্ভর করে মাটির বুনটের পরিবর্তন হয় ।
অধিকাংশ ফল যে কোন ধরনের বুনটের মাটিতে অর্থাৎ বেলে, বেলে দো-আশ, এটেল, এটেল দো-আশ ও কাকরযুক্ত মাটিতে পরিচর্যার মাধ্যমে চাষ করা যায় । হালকা বুনটের মাটিতে কাঁঠাল, আনারস, পেঁপে, কলা, তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায় এবং ফলের মিষ্টতা বেশী হয় । আবার ভারি মাটিতে এগুলোর আকার বড় হয়, কিন্তু মিষ্টতা কম হয় । মাটির ভৌত গুণাবলী পরিবর্তন করতে অনেক বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় । মাটির ভৌত গুণাবলির ওপর মাটির ভেতরের তাপমাত্রা নির্ভর করে, যা গাছের শেকড়ের বৃদ্ধিতে প্রভাব বিস্তার করে । তাই গাছের শেকড়ের বৃদ্ধির জন্য মাটির ভেতরে অনুকূল তাপমাত্রা থাকা প্রয়োজন । মাটির রাসায়নিক গুণাবলী বিশেষ করে মাটির পিএইচ মানাংক ও মাটির লবণাক্ততা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । ফুল চাষের জন্য সবচেয়ে ভালো পিএইচ হলো ৫.৫ হতে ৮.০ । মাটি বেশি অম্লীয় হলে লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, অ্যালুমিনিয়াম বেশি দ্রবীভূত হয়, যা গাছের জন্য বিষাক্ত । মাটি বেশি ক্ষারীয় হলে লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা, কপার ও কোবাল্ট মাটিতে কম দ্রবীভূত হয়, যা গাছ শোষণ করতে পারে না। সাধারণত মাটি বেশি অম্ল হলে চুন এবং বেশি ক্ষারীয় হলে সালফার জাতীয় সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। ক্ষারীয় মাটিতে আনারসে লৌহের অভাব দেখা যায় । লবণাক্ত মাটিতে নারিকেল ছাড়া অন্য ফল লাভজনকভাবে জন্মানো যায় না । মাটিতে গৌণ খাদ্যের অভাবে নারিকেল ফলের অপক্কতা, ঝরে পড়া, ফল ও শাস গঠনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় । দস্তার অভাবে লেবু গাছের ছালে, লেবুর খোসায় আঠার থলের সৃষ্টি হয়, ফল ফেটে যায়, পাতার কিনারা শুকিয়ে যায় ।
সাধারণত উঁচু জমি, পানি জমে না বা বৃষ্টির পানিতে জলাবদ্ধতা হয় না বা নিকাশের সুব্যবস্থা আছে এমন স্থান ফল চাষের জন্য ভাল । মাঝারি উঁচু জমি যেখানে অল্প সময়ের জন্য পানি জমে থাকে সেখানে অল্প সময়ের জন্য জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে এমন ফল গাছ রোপণ করা যায় । আম, জাম, গাব, দেওফল, বেত ফল, নারিকেল, খেজুর, তাল ইত্যাদি এ শ্রেণিভুক্ত । অপেক্ষাকৃত নিচু জমিতে গাব ও পানিজাম চাষ করা সম্ভব হয় । সমুদ্র উপকূলবর্তী ও লোনা মাটিতে সব ধরনের ফল চাষ করা যায় না । তবে এ ধরনের মাটিতে ফসফরাস ও পটাশের তেমন অভাব হয় না বলে নারিকেল, সুপারী, কাউফল ও আমড়া জাতীয় ফল ভালভাবে জন্মাতে পারে ।
পাহাড়ী এলাকায় পাহাড়ের ঢাল কতটুকু তার ওপর নির্ভর করে ফল চাষ করতে হয় । কেননা ঢাল বেশি হলে অর্থাৎ ৪৫-এর বেশি ঢালে ফল চাষ করা দুরুহ । তবে বেশি ঢালে বিশেষ পদ্ধতিতে গাছ রোপণ করতে হয় । পাহাড় উচু হলে তার উত্তর দিকে বেশী আলো পৌঁছেনা । এ রকম স্থান ফল চাষের জন্য নির্বাচন করা উচিত নয় । তামাটে বর্ণের পাহাড়ী মাটি অম্লীয় ও সুনিষ্কাশিত হলে মাটির পিএইচ মানাংক সাধারণত ৪ - ৪.৫ হয় । এ ধরনের মাটিতে কাজুবাদাম, আনারস, এ্যাভাকোডো, কাঁঠাল, সুপারি ইত্যাদি জন্মানো যায় । সাধারনভাবে বাংলাদেশের প্রায় সব এলাকাতেই সব ধরনের ফল মোটামুটি জন্মাতে পারে । তবে কিছু কিছু ফল সবস্থানে ভাল ফলন দিতে পারে না যেমন— উৎকৃষ্টমানের আম দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহে ভাল জন্মে । পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ী এলাকা কমলালেবুর চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী । আনারস চাষের জন্য অম্ল মাটি উপযোগী । মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং সিলেট ও চট্টগ্রামের লালমাটি এলাকা অম্লীয় বিধায় আনারস চাষের জন্য সবচেয়ে ভাল । লোনামাটির এলাকা বরিশাল বিভাগ ও খুলনার সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা নারিকেল চাষে জন্য উত্তম । এ ছাড়াও বৃষ্টি বহুল এবং সাঁতসেতে পরিবেশ বিরাজ করে বলে গাব, চালতা, জাম, দেওফল, লটকন ইত্যাদি ভালো ভাবে জন্মাতে পারে ।
অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
১। আমাদের দেশে ফলের চারা/কলম রোপণের সবচেয়ে উপযুক্ত সময় কখন ?
২। আবহাওয়ার প্রভাবকের উপর নির্ভর করে ফলকে কত ভাগে ভাগ করা যায় ।
৩ । কোন মাটি ফল চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী ?
৪ । বাংলাদেশের কোন অঞ্চলের মাটি নারিকেল চাষের জন্য সবচেয়ে উত্তম ।
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
১। ফল বাগানের জন্য কিরূপ জমি নির্বাচন করা উচিত ।
২। আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে ফলকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় । প্রত্যেকটির ৫টি করে উদাহরণ দাও ।
৩ । আবহাওয়ার প্রভাবকগুলোর ওপর ভিত্তি করে ফলকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ?
৪ । ফল চাষের উপর তাপমাত্রার প্রভাব সম্পর্কে লেখ ।
৫ । ফল গাছ রোপনের সময় বা মৌসুম বলতে কি বোঝায় ?
৬। বৃষ্টিপাত কিভাবে ফল উৎপাদনের প্রভাব ফেলে?
৭ । সমুদ্র উপকুলবর্তী ও লোনা মাটিতে কোন কোন ফল ভালো জন্মে ?
রচনামুলক প্রশ্ন
১ । জলবায়ুর ওপর নির্ভর করে ফল উৎপাদন অঞ্চলসমূহের বর্ণনা দাও ।
২। ফল গাছ রোপণের জন্য জমির উপযুক্ততা সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর ।
৩ । জলবায়ুর প্রভাবকগুলো ফল উৎপাদন কিভাবে প্রভাবিত করে ব্যাখ্যা কর ।
৪ । ফল গাছ রোপণের জন্য মাটির প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা কর ।
৫। গাছ রোপণের সময় বা মৌসুম সম্পর্কে লেখ।
৬। চারা রোপণ সময়ের পরবর্তী পরিচর্যা গুলো সংক্ষেপে লেখ ।
৭ । ফল চাষের জন্য জমি তৈরি সংক্ষেপে লেখ ।
৮। টীকা লেখ ?
ক) জলবায়ুর চাহিদা অনুযায়ী ফলের শ্রেণিবিভাগ খ) উষ্ণমণ্ডলীয় ফল গ) অব উষ্ণমণ্ডলীয় ফল
ফল বাগানের পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । ফল বাগান স্থাপনের পূর্বেই সার্বিকদিক বিবেচনায় রেখে পরিকল্পনা ও নকশা তৈরি করতে হবে। বেশিরভাগ ফল গাছই বৃক্ষজাতীয় গাছ। পারিপার্শিক পরিবেশ, আবহাওয়া, মাটির গুণাগুণ, জনগণের চাহিদা, বাজার ব্যবস্থা উন্নতজাত ও প্রযুক্তি প্রাপ্তি ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে বাগানের পরিকল্পনা করতে হয় । বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিকল্পনা না করা হলে অযথা অর্থব্যয় হবে ও ফল চাষে ব্রতী হবে । ফল বাগানের জন্য সব সময়ই উঁচু, খোলামেলা, পানি নিকাশের সুবিধাযুক্ত এবং জলাবদ্ধতা হয় না এমন খান । নির্বাচন করতে হয়। বিভিন্ন জাতের ফল গাছ বিভিন্ন ধরনের আবহাওয়া ও মাটিতে ভালভাবে জন্মাতে পারে । মাটির গুণাগুণ অনেক ক্ষেত্রে পরিচর্যার মাধ্যমে পরিবর্তন করা যায় । কিন্তু আবহাওয়া পরিবর্তন করা যায় না । ফলের গাছ স্বল্প মেয়াদী, মধ্যম মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদি হয়ে থাকে । দীর্ঘমেয়াদি ফল গাছ ৩০/৪০ থেকে ৫০/৬০ বছর পর্যন্ত ভালভাবে ফল দিয়ে থাকে । মধ্য মেয়াদি ফলগাছ ১৫ থেকে ২০ বছর ভালভাবে ফল দিয়ে থাকে । স্বল্পমেয়াদি ফল গাছ ১-৩ বছর পর্যন্ত ফল দিয়ে থাকে । দীর্ঘ ও মধ্য মেয়াদি ফল গাছ রা পণের সময় স্থান নির্বাচনে, নকশা তৈরিতে, রোপণের দূরত্ব নির্ধারণে, জাত বাছাই ইত্যাদি বিবেচনায় যদি ভুল হয়, আর তা যদি বাগান স্থাপনের কয়েক বছর পর জানা যায় তাহলে তা সারিয়ে নেয়ার সুযোগ থাকে না । বাগান লাভজনক করতে হলে দীর্ঘ ও মধ্য মেয়াদী বাগানে আন্তফসলের চাষ করা যেতে পারে । যেমন— আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, নারিকেল প্রভৃতি ফল গাছ ৮-১০ বছরের আগে ভালভাবে ফল দেয় না । সে জন্য এ সময় সেখানে পেঁপে, কলা, আনারস, জামরুল, আতা, শরিফা, কুল লাগিয়ে খরচ পুষিয়ে নেয়া যেতে পারে ।
ফল বাগান পরিকল্পনার সাধারণ নীতিমালা
(১) ফল বাগান স্থাপন এবং কোন নির্দিষ্ট ফল ভালভাবে চাষের জন্য তার উপযোগী আবহাওয়া, জমির উচ্চতা, মাটির প্রকারভেদ, ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, পরিবহণ ও বিপণনের সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করতে হবে ।
(২) পতিত জমিতে বাগান করতে হলে সেখানে পুরাতন গাছ বা গাছের গোড়া থাকলে তা পরিষকার করে গভীরভাবে চাষ করতে হবে । পাহাড়ী এলাকা হলে কন্টুর এবং সিড়িবাধ তৈরি করে কিছু দূর পর্যন্ত সমতল করে নিতে হবে ।
(৩) বাগান তৈরিতে রাস্তা, সেচ ও নিষ্কাশন নালা, বাগানের গুদামঘর ইত্যাদি কাজের জন্য কোনক্রমেই মোট জমির শতকরা দশভাগের বেশি ব্যবহার করা সমিচিন হবে না ।
(৪) বাগানে সেচ সুবিধার জন্য কাছাকাছি পানির ব্যবস্থা থাকা দরকার ।
(৫) চিরসবুজ গাছগুলো বাগানের সামনে এবং ভেতরে লাগাতে হবে । পাতা ঝরে যায় এমন গাছ যেমন— বেল, আমড়া, বরই ইত্যাদি পিছনে এবং বাইরে লাগাতে হবে ।
(৬) সেচ দেয়ার প্রয়োজন হয় এমন গাছ পানির উৎসের কাছাকাছি এবং বৃষ্টিনির্ভর গাছ পানির উৎস হতে দূরে লাগাতে হবে ।
(৭) ছোট আকারের গাছ বাগানের সামনে এবং লম্বা ধরনের গাছ পেছনের দিকে লাগাতে হবে, তাতে বাগান তত্ত্বাবধানে সুবিধা হবে ।
(৮) বর্ষার শুরুতে সঠিক দূরত্বে গর্ত করে পরিমাণ মত সার দিয়ে চারাগাছ লাগাতে হবে ।
(৯) গাছের সঠিক বৃদ্ধির জন্য পরিমাণ মত জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করতে হবে ।
(১০) ফলের বাগানে আন্তফসলের চাষাবাদ করলে গাছের দূরত্বের সর্বোচ্চ দূরত্বে এবং তা না করলে সর্বনিম্ন দুরত্বে গাছ লাগাতে হবে ।
(১১) বাগানের চারিদিকে প্রয়োজনে বেড়া দিতে হবে । প্রবল বাতাস থেকে গাছ রক্ষার জন্য উত্তর পশ্চিম দিকে বায়ুরোধকারী বৃক্ষ ঘন সারি করে লাগাতে হবে । বেড়া গাছ গ্রীষ্মের গরম বাতাস এবং শীতের শুষ্ক ও ঠান্ডা বাতাস থেকে বাগানের ফল গাছকে রক্ষা করবে । বেড়ার চারদিকে কাটাওয়ালা পাতি, কাগজি ও গন্ধরাজ লেবুর গাছ ও করমচা গাছ লাগানো যেতে পারে । এতে বেড়ার কাজ হবে এবং ফলও পাওয়া যাবে । তবে বেড়ার জন্য লাগালে এসব গাছ ছাটা ঠিক হবে না ।
(১২) উর্বর জমিতে লাভজনকভাবে ফল চাষের জন্য যে সমস্ত ফল গাছ মাটামুটি একই সময়ে ফল দেয় সে সমস্ত ফল গাছগুলোকে পাশাপাশি লাগাতে হবে ।
(১৩) বাগানের নক্সা তৈরির আগে গাছের আকার, জমির পরিমাণ ও জমির আকৃতি, গাছ রোপণ প্রণালী ঠিক করে নিতে হবে ।
(১৪) ফলের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে বাঁশের ঝুড়ি, চটের ব্যাগ, কাঠের বা পিচবার্ডের বাক্সে প্যাকিং করে বাজারে পাঠাতে হবে । তাই বাগান এলাকার আশেপাশে এ সমস্ত উপকরণসমূহের সহজলভ্যতা থাকতে হবে।
(১৫) ফল চাষ করে সহজে এবং কম খরচে যাতে বাজারে বা চিহ্নিত স্থানে নিয়ে যাওয়া যায় সে বিষয়টি খেয়াল করতে হবে।
(১৬) বাগানের পরিচর্যার জন্য যন্ত্রপাতি যথা- কোদাল, নিড়ানি, ঝাঝরি, ফর্ক, রেফ, দা, প্রুনিংস, কাঁচি, বাডিং ছুরি, প্রেয়ার, এক চাকার ঠেলাগাড়ি প্রভৃতির ব্যবস্থা রাখতে হবে ।
ফল গাছ লাগানোর নকশার প্রকারভেদ
উন্নত পদ্ধতিতে এবং লাভজনকভাবে ফল বাগান করতে হলে বাগানে গাছ লাগানোর জন্য নকশা তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন । বাগান তৈরির আগে প্রথমে কাগজে নকশা তৈরি করে ভুলত্রুটি দেখে নিতে হবে । বাগানের নকশা তৈরি করে পরিকল্পনা অনুযায়ী বাগানের অফিসঘর, গুদামঘর, গার্ডশেড, পানির পাম্পের স্থান, ভেতরের রাস্তা, সেচ ও নিকাশ নালা, নির্দিষ্ট ফল গাছের জন্য নির্বাচিত স্থান, বেড়ার গাছ যথাস্থানে আছে বা করা যাবে কিনা তা জেনে নিতে হয় । জমির সুষ্ঠু ব্যবহার এবং জমির অপচয় রোধে প্রত্যেকটি কাজের জন্য জমি চিহ্নিত করে ফল গাছের রোপণ পদ্ধতি অনুযায়ী রোপণ দূরত্ব ঠিক করে, সেচ পদ্ধতি পরিচর্যা ইত্যাদি বিষয় বাগানের নকশায় উল্লেখ করতে হবে । বাগানের নকশা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে মাটির উর্বরতা ও অবস্থান দেখে সর্বাধিক সংখ্যক গাছ লাগানো যায় । তাতে প্রতিটি গাছ সুন্দরভাবে আলো-বাতাস পেয়ে বড় হতে পারে । পরিকল্পনা মোতাবেক গাছ লাগালে নির্ধারিত দূরত্ব বজায় থাকে এবং একটি অন্যটির বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করে না । বিভিন্ন পদ্ধতিতে ফল বাগানের নকশা বা পরিকল্পনা করা হয় । এ পদ্ধতিগুলো যথা—
১ । আয়তকার
২ । বর্গাকার
৩ । পঞ্চম সংস্থান বা তারকাকৃতি বা কুইনকাংশ
৪ । ত্রিকোনী বা ত্রিভুজাকার
৫ । ষড়ভুজী
৬ । কন্টুর বা সিঁড়িবাধ
উলিখিত ছয় প্রকার গাছ রোপণ পদ্ধতির প্রধান প্রধান বিষয়গুলো নিচে আলোচনা করা হলো । তবে রোপণ পদ্ধতি নির্ধারণ করার সময় কতকগুলো বিষয় বিবেচনা করা উচিত । যথা—
(ক) নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে কত বেশি সংখ্যক গাছ রোপণ করা যাবে ।
(খ) জমি চাষ, পানি সেচ ও নিকাশ, গাছের পরিচর্যা কত সহজে ও সুষ্ঠুভাবে করা যাবে ।
(গ) চারা রোপণের পদ্ধতির কারণে যেন গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত না হয় ।
(ঘ) এমনভাবে গাছ লাগাতে হবে যাতে বাগান দেখতে সুন্দর দেখায় ।
চারা রোপণের জন্য নকশা প্রণয়নে করণীয় কাজসমূহ
ক) মূলরেখা চিহ্নিতকরণ: প্রতিটি জমিতে চারা রোপণের আগে জমির কিনারা বা আইল দিয়ে সীমানা রেখা টানতে হবে । এরপর একটি মূলরেখা টেনে নিতে হয় । সাধারণত প্রতিটি জমিতে গাছের প্রথম সারিটি মূল রেখা হিসেবে ধরে নেয়া হয় । এ সারিটি জমিতে সারি থেকে সারির যে দূরত্বে গাছ লাগানো হবে মূলরেখাটি জমির কিনারা বা আইল হতে তার অর্ধেক দূর দিয়ে নিতে হবে। এ সারিকে মুল সারি বা ভিত্তি সারি হিসেবে বিবেচনা করা হয় । এর উপর গাছ হতে গাছের দূরত্ব চিহ্নিত করে অপরাপর সারিগুলো এমনভাবে টানতে হবে যেন একটি আরেকটির সাথে পরস্পর সমান্তরালভাবে থাকে ।
খ) জমিতে লম্বরেখা গঠন: জমির এক কোণে দাঁড়িয়ে বা মূল সারির এক প্রান্তে দাড়িয়ে যথাযথ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট । একটি রশি ধরে ৩ : ৪ : ৫ অনুপাতে বা ১২, ১৩, ২০ মিটার হিসেবে জমির দুই দিকের আইল বরাবর রশি ধরে চিহ্নিত করতে হবে । অর্থাৎ কৌণিক স্থান হতে উভয় দিকের আইল বরাবর দুদিকে রেখা টেনে একটিতে ১২ মিটার এবং অপরটিতে ১৬ মিটার দূরত্ব চিহ্নিত করতে হবে । এই চিহ্নিত স্থান দুটি সোজাসুজি সংযোগ করা হলে সংযোজিত রেখাটি যদি ২০ মিটার হয় তাহলে সংযোগস্থলে ৯০ ডিগ্রী কোণ তৈরি হবে। এরপর উভয়দিকের রেখা সরল রেখা হিসেবে প্রসারিত করা হলে একটি অপরটির উপর লম্বরেখা হিসেবে অঙ্কিত হবে । এর একটিকে মূলরেখা ধরে সমান্তরাল রেখা টানতে হবে । তবে মূল রেখাটি জমির কিনারা বা আইলে না ধরে সারি হতে সারির অর্ধেক দূরত্বে ধরতে হয় ।
গ) মুক্ত রেখা প্রতুতকরণ: জমিতে আইল বরাবর লম্ব রেখা টেনে তারপর মূলরেখা তৈরি করা হয়। এ মূলরেখার গাছ রোপনের চিহ্নিত স্থান হতে পরবর্তী রেখার বা সমান্তরাল রেখার চিহ্নিত স্থানে লম্ব রেখার উপর হতে মূল রেখার সমান্তরাল রেখা সংযোগে করা হলে মুক্ত রেখা তৈরি হয় । এ ভাবে মূলরেখার ওপর গাছের দূরত্ব অনুসারে প্রতিটি সারিতে সারি হতে সারির অংকিত রেখায় যতগুলো সম্ভব স্থান চিহ্নিত করে সংযোগ করতে হবে । তবে মূলরেখার উপর এক দিক হতে বা উভয়দিক হতে গাছ রোপণের জন্য নির্ধারিত দূরত্বের অর্ধেক দূরত্ব হতে গাছ রোপণের নিমিত্তে উলিখিত রেখাগুলো তৈরির জন্য চিহ্নিতকরণ দন্ড বা গোজ, দূরত্ব মাপার ফিতা, রশি, গাছের স্থান চিহ্নিত করে রাখার জন্য চিকন কাঠির প্রয়োজন ।
ফল গাছ রোপণের পদ্ধতিগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো
(১) আয়তাকার পদ্ধতি: এ পদ্ধতিতে পাশাপাশি দুই বা ততোধিক সমান্তরাল সারির মধ্যে মূল সারিতে গাছের স্থান চিহ্নিত করতে হবে । এরপর মূল রেখার চিহ্নিত স্থান হতে পরবর্তী সারিগুলোকে লম্বরেখায় চিহ্নিত করে মুক্ত রেখা চিহ্নিত করতে হবে। এর ফলে পাশাপাশি দুসারির মধ্যে চারটি গাছের সমন্বয়ে একটি আয়তক্ষেত্রের সৃষ্টি হবে ।
সাধারণত আয়তাকার পদ্ধতিতে সারি থেকে সারির দূরত্ব গাছ থেকে গাছের দূরত্বের চেয়ে বেশি থাকে । এ পদ্ধতিতে লাগানো ফল বাগানে আন্ত পরিচর্যা যেমন- চাষ, পানি সেচ, কোপানো, আগাছা পরিষ্কার ইত্যাদি কাজ সুবিধাজনক হয় । বাগানের জন্য রোপিত গাছ বড় হওয়ার আগে এর মাঝে শাক, আলু, তরমুজ, ফুটি, হলুদ, কচু, ডাল জাতীয় শস্য ইত্যাদি কয়েক বছর করা যায় । এর ফলে বাড়তি আয় করা সম্ভব হয় ।
হেক্টর প্রতি গাছের সংখ্যা নির্ণয়ের পদ্ধতি (আয়তাকার বা বর্গাকার পদ্ধতি):
এক হেক্টর জমিতে মোট গাছের সংখ্যা = এক হেক্টর জমি = ১০০০০ বর্গমিটার
সারি থেকে সারির দূরত্ব (ব:মি:) গাছ থেকে গাছের দূরত্ব (ব:মি:) অথবা
সারির সংখ্যা প্রতি সারিতে গাছের সংখ্যা
উদাহরণ: পেঁপে বাগানে ৫ মিটার দূরত্বে সারি করে ২ মিটার দূরত্বে চারা রোপণ করলে এক হেক্টর জমিতে কতটি চারা রোপণ করা যাবে-
অর্থাৎ এক হেক্টর জমিতে ১০০০টি চারা রোপণ করা যাবে ।
(২) বর্গাকার পদ্ধতি: এ পদ্ধতিতে পাশাপাশি দু'সারির গাছগুলোকে এমনভাবে রোপণ করা হয়, যাতে সারি হতে সারি এবং গাছ হতে গাছের দূরত্ব পরস্পর সমান থাকে । অর্থাৎ পাশাপাশি দুসারির চারটি গাছ মিলে একটি বর্গক্ষেত্র তৈরি করে । বর্গক্ষেত্রের চারকোনার স্থানগুলোতে গাছ রোপণ করা হয় । আম, কাঁঠাল, লিচু, সফেদা, জাম, জামরুল, পেয়ারা, পেঁপে প্রভৃতি ফল গাছের চারা এ পদ্ধতিতে রোপণ করা হয় । এ পদ্ধতিটি তুলনামূলকভাবে সহজ এবং মাঠে সহজে নকশা প্রণয়ন করা যায়।
জমিতে মুলরেখা তৈরি করার পর নির্দিষ্ট দূরত্ব অনুসারে সম্পূর্ণ মূল রেখায় কাঠি বা গোজ পুঁতে চারা রোপণের স্থান চিহ্নিত করতে হবে । মূলরেখার সঙ্গে লম্বরেখা টেনে সারি হতে সারির দূরত্ব চিহ্নিত স্থান হতে মূল রেখার সমান্তরাল রেখা টানতে হবে । এরপর প্রথম সারি বা মূলরেখার চিহ্নিত স্থান হতে লম্বরেখা টেনে নিলে পরবর্তী সারিগুলোতে যেখানে রেখাগুলো অতিক্রম করবে সে স্থানগুলোতে কাঠি বা গোঁজ পুঁতে দিতে হবে । প্রত্যেকটি স্থানে গাছ রোপণ করা হলে প্রতি চারটি গাছ মিলে এক একটি বর্গক্ষেত্র তৈরি করবে । এ পদ্ধতিটি বেশি প্রচলিত এবং দেখতে সুন্দর দেখায় । এখানে উল্লেখ্য যে মূলরেখাটি জমির আইল হতে সারি হতে সারির দূরত্ব বাদ দিয়ে প্রথম গাছের স্থান চিহ্নিত করা হয় । বর্গাকার পদ্ধতিতে মোট গাছের সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য আয়াতাকার পদ্ধতির অনুরূপ নিয়ম অনুসরণ করতে হবে ।
উদাহরণ একটি আম বাগান করার জন্য ১০ মিটার দূরে দূরে সারি ও ১০ মিটার দূরে দূরে চারা/কলম রোপণ করা হলে এক হেক্টর জমিতে মোট কতটি চারার প্রয়োজন হবে ।
অর্থাৎ এক হেক্টরে ১০০টি চারা বা কলম রোপণ করা যাবে ।
(১) কুইনকাংশ বা পঞ্চম সংস্থান বা তারকাকৃতি পদ্ধতি: এ পদ্ধতিটি বর্গাকার পদ্ধতির একটি বিশেষ রূপ । বর্গাকার পদ্ধতির প্রতি চার কোণের চিহ্নিত স্থান হতে মূল রেখার উপর বা পরবর্তী সারিগুলোতে দুই গাছের চিহ্নিত মধ্যবর্তী স্থানে চিহ্নিত করতে হবে । অনুরূপভাবে মুক্ত রেখাগুলোর উপর প্রতি দুই সারির মধ্যবর্তী স্থানে চিহ্নিত করতে হবে । এখন মূল রেখা বা পরবর্তী সারিগুলোর মধ্যবর্তী স্থান এবং মুক্ত রেখার মধ্যবর্তী স্থানে চিহ্নিত করতে হবে । এরপর মুল রেখা বা পরবর্তী সারিগুলোর মধ্যবর্তী স্থান এবং মুক্ত রেখার মধ্যবর্তী স্থান হতে সামনা সামনি দিকে রেখা টানলে বর্গক্ষেত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে মিলিত হবে। এই কেন্দ্রবিন্দু হবে পঞ্চম সংস্থান । কেন্দ্রবিন্দুর সংস্থানকৃত গাছটিকে ফিলার বা পূরক বলে । বর্গাকার পদ্ধতিতে চারকোনে মধ্যম মেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী গাছ লাগানো হয় এবং পুরক গাছটি স্বল্পমেয়াদী হিসেবে লাগানো হয় । যেমন— দীর্ঘমেয়াদী গাছ হলো আম, কাঁঠাল, লিচু, জাম, কামরাঙ্গা, তেঁতুল এবং স্বল্পমেয়াদী গাছ হলো লেবু, ডালিম, পেয়ারা, আতা, শরীফা, জাম্বুরা, কলা, জামরুল, করমচা ইত্যাদি । পুরক গাছগুলো যখন মধ্যমমেয়াদি বা দীর্ঘমেয়াদি গাছের সাথে আলো, বাতাস, খাদ্য উপাদান, পানি ইত্যাদির জন্য প্রতিযোগিতায় যাবে তখন পূরক গাছগুলো কেটে ফেলতে হবে । স্থায়ী গাছের দূরত্ব কমপক্ষে ৭ মিটার না হলে এ পদ্ধতি তেমন ফলপ্রসূ হিসেবে অনুশীলন করা যাবে না।
কুইনকাংশ বা পঞ্চম সংস্থান পদ্ধতিতে জমিতে গাছের সংখ্যা নির্ণয়
জমিতে মোট গাছের সংখ্যা = (সারির সংখ্যা সারিতে গাছের সংখ্যা) + পুরক গাছ
পুরক গাছ = (প্রধান সারিতে গাছের সংখ্যা - ১) (সারির সংখ্যা - ১)
উদাহরণ: কোন জমিতে ১২টি সারি তৈরি করে প্রতিটি সারিতে ১০টি করে চারা রোপণ করা হলে ঐ জমিতে পঞ্চম সংস্থান পদ্ধতিতে কতটি চারা রোপণ করা যাবে ।
৪) ত্রিকোণী বা ত্রিভুজাকার পদ্ধতি: মূলরেখা তৈরি করে মূল রেখার উপর বর্গাকার পদ্ধতির ন্যায় গাছের দূরত্ব চিহ্নিত করতে হবে । এরপর দ্বিতীয় সারিতে জমির কিনারা হতে গাছের দূরত্বের পূর্ণ দূরত্বে চিহ্ন করতে হবে । এই ভাবে পরবর্তী চিহ্নগুলো গাছের পূর্ণ দুরত্বে করতে হবে। এতে মূলরেখায় গাছের নির্ধারিত দুটি গাছের চিহ্নের মধ্যবর্তী স্থান বরাবর দ্বিতীয় সারিতে গাছের চিহ্ন পড়বে। এ পদ্ধতিতে প্রতি একান্তর বা জোড়া সারিতে প্রথম সারির দুই গাছের মধ্যবর্তী স্থানে গাছ লাগানো হয় এবং এরপর প্রতি বেজোড় সারিতে বর্গাকার পদ্ধতির ন্যায় গাছ লাগানো হয়। এতে প্রথম বা মূলরেখার দুটি এবং একাত্তর সারির একটি গাছের চিহ্ন যোগ করা হলে মাত্র একটি ত্রিভুজের সৃষ্টি করে । অনুরূপভাবে একাত্তর বা জোড় সারির একটি গাছ তৃতীয় বা বেজোড় সারির দুটি গাছের চিহ্নের সাথে যাগে করা হলে ত্রিভুজের সৃষ্টি করে । ত্রিভুজগুলো সমবাহু ত্রিভুজ হয় । ১ম, ৩য়, ৫ম বা বেজোড় সংখ্যক লাইনে বর্গাকার প্রণালীতে গাছ লাগানো হয় এবং ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ বা জোড় সংখ্যক লাইনে বেজোড় লাইনের দুটি গাছের মধ্যবর্তী স্থানে গাছ লাগানো হয় । এ পদ্ধতিতে সারি হতে সারির দূরত্ব গাছ হতে গাছের দূরত্ব অপেক্ষা বেশি রাখা হয় । প্রতি এক সারি পর পর বা একান্তর সারিতে একটি করে গাছ কম হয় । এতে করে মোট জমিতে বর্গাকার পদ্ধতি অপেক্ষা গাছের সংখ্যা কমে যায় ।
ত্রিভূজাকার পদ্ধতিতে জমিতে মোট গাছের সংখ্যা নির্ণয়
জমিতে মোট গাছের সংখ্যা = (প্রথম সারিতে গাছের সংখ্যা মোট সারির সংখ্যা) - একান্তর ক্রমিক (জোড় সারির সংখ্যা
উদাহরণ: এটি জমির দৈর্ঘ্য ৫০ মিটার এবং প্রস্থ ৩০ মিটার । এ জমিতে ১০ মিটার দূরে দূরে সারি করে একই দূরত্বে গাছ রোপণ করা হলে মোট কতটি গাছ রোপণ করা যাবে।
৫। ষড়ভুজী পদ্ধতি: ষড়ভুজী পদ্ধতি একটি সমবাহু ত্রিভুজাকার পদ্ধতি । এখানে পাশাপাশি দুই সারির তিনটি গাছ মিলে একটি সমবাহু ত্রিভুজ তৈরি করে। পাশাপাশি তিন সারির ছয়টি গাছ মিলে একটি ষড়ভুজ তৈরি করে । এর কেন্দ্রস্থলে একটি গাছ থাকে । গাছের দূরত্ব নির্দিষ্ট রাখতে হলে সারি হতে সারির দূরত্ব কমিয়ে দিতে হয় । প্রকৃতপক্ষে ষড়ভুজ তৈরি কিছুটা জটিল হলেও গাছ লাগানো হলে দেখতে সুন্দর দেখায় । যে কোন দিক হতে তাকালে লাগানো গাছগুলো একটি সরল রেখায় দেখা যায়। একগাছ থেকে অপর গাছের দূরত্ব সমান থাকে । ফলে আলো, বাতাস, খাদ্য উপাদান, পানি ইত্যাদি সকল গাছ সমানভাবে পায় । আম, কলা, আপেল, পীচ, লেবু, পেয়ারা, নারিকেল কাজুবাদাম প্রভৃতি ফল গাছের চারা এই পদ্ধতিতে লাগানো হয় । ষড়ভুজ পদ্ধতিতে গাছ লাগালে দূরত্ব ৷ ঠিক রেখেও ১৫% গাছ বেশি লাগানো যায় । ফলে একই জমি থেকে ১৫% অধিক ফল উৎপাদন করা সম্ভব ।
ষড়ভুজী পদ্ধতি জমিতে চারা সংখ্যা নির্ণয়
জমিতে মোট চারার সংখ্যা = (মোট সারির সংখ্যা প্রধান বা প্রথম সারিতে গাছের সংখ্যা) - জোড় বা একান্তর ক্রমিক সারির সংখ্যা ।
উদাহরণ: এক খণ্ড জমির দৈর্ঘ্য ৫০ মিটার এবং প্রস্থ ৪০ মিটার । ৫ মিটার দূরে দূরে সারি এবং ৮ মিটার দূরে দূরে চারা রোপণ করা হলে ঐ জমিতে মোট কতটি চারা রোপণ করা যাবে ।
(৬) কন্টুর বা ঢাল এবং সিড়িবাধ পদ্ধতিঃ পার্বত্য অঞ্চলে ঢাল এবং সিড়িবাঁধ নির্মাণ করে ঢালের আড়াআড়িভাবে ফলের চারা রোপণ করা হয় । জমিতে চাল ৩ শতাংশের বেশি এবং ১০ শতাংশের কম থাকলে সেখানে কন্টুর বা ঢাল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে জমির ঢাল অনুযায়ী সমান স্থানগুলোকে একই রেখা দ্বারা সংযোগ করে দেয়া হয় । যেখানে ভূমিক্ষয়ের সম্ভাবনা থাকে এবং সেচ দেয়া অসুবিধাজনক সেখানে এ পদ্ধতিতে গাছ লাগানো হয় । এখানে স্বাভাবিক ভাবে লাগানো গাছের পারস্পরিক দূরত্ব কখনও সমান রাখা সম্ভব নয় । পাহাড়ের ঢাল ১০ শতাংশের বেশি হলে পাহাড় কেটে সমতল সিঁড়িবাধ তৈরি করা হয় এবং ঢালের সাথে আড়াআড়িভাবে সারি করে গাছ লাগানো হয় । এখানে প্রথম সারির দুটি গাছের মধ্যবর্তী স্থানে পরবর্তী সারিতে গাছ লাগিয়ে জমির ক্ষয়রোধ করা হয় । এর ফলে সিড়ি বাঁধ পদ্ধতিতে পানিসেচ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা ঠিকমত করা যায় ও ভূমিক্ষয় রোধ করা যায় । এ কাজের জন্য ঢালের নিচের দিকে কিছুটা উঁচু করে আইল বা বাঁধ দিতে হয় ।
সকল প্রকার পদ্ধতিতেই গাছ লাগানোর মানে কাঠি বা গেজ দিয়ে চিহ্ন করতে হয়। গোজ তুলে দিয়ে ফল গাছের আকৃতি অনুসারে বিভিন্ন আকারের গর্ত খুড়ে পরিমাণ মত সার দিয়ে গর্ত পূরণ করতে হয় । সার মিশ্রিত মাটি দিয়ে গর্ত পূরণ করে অন্তত ৮-১২ দিন পরে ঐ গর্তে ফলের চারা রোপণ করতে হয় । ফল গাছ রোপণের জন্য নকশা সঠিক নির্বাচন এবং সঠিক দূরত্ব বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কেননা অপর্যাপ্ত পরিসরে গাছ ভালোভাবে বাড়তে পারে না। ফলে ফল কম ধরে ও নিম্নানের হয় । গাছ কাছাকাছি হলে রোগ ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ সহজে বিস্তার লাভ করতে পারে । অন্যদিকে অধিক পরিসরে গাছ লাগালে মূল্যবান জমির অপচয় হয়, জমিতে বেশি আপাছা হওয়ার সুযোগ পায়, জমি তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় এ ভূমির ক্ষয় হয় ।
বর্গাকার পদ্ধতি
সুবিধা
১) এ পদ্ধভিটি তুলনামূলকভাবে সহজ। কেননা মাঠে নকশা প্রণয়নে কোন ঝামেলা হয় না ।
(২) বর্ণক্ষেত্রের প্রতি কোণায় একটি করে গাছ লাগানো হয় । তাই প্রতিটি গাছ সমান দূরত্ব পায় এবং সহজে বেড়ে উঠতে পারে ।
(৩) স্বল্পমেয়াদি ও দ্রুতবর্ধনশীল ফল গাছের জন্য এ পদ্ধতি সঠিক উপযোগী।
অসুবিধা
(১) সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি এবং বর্ধনশীল ফসলসমূহ এ পদ্ধতিতে লাগানো বিশেষ উপযোগী নয় ।
(২) ফল গাছ লাগানোর কিছু কিছু নকশার বেশি গাছ লাগানো যায় কিন্তু এ পদ্ধতিতে কম সংখ্যক গাছ লাগানো যায়।
(৩) গাছ গোলাকার ভাবে চতুর্দিকে বাড়ে ফলে বর্গক্ষেত্রের চার কোণায় লাগানো গাছ হতে বর্গক্ষেত্রের কেন্দ্র কিন্তু বা মাঝখানের জায়গা অব্যবহৃত থাকে। আয়তাকার পদ্ধতি সুবিধা ও অসুবিধা বর্গাকার পদ্ধতির অনুরূপ
পঞ্চম সংস্থান পদ্ধতি
সুবিধা
(১) এ পদ্ধতিতে বর্গাকার বা আয়তকার পদ্ধতি অপেক্ষা কোন নির্দিষ্ট জমিতে বেশি সংখ্যক গাছ লাগানো যায়।
(২) জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার হয় ।
(৩) এ পদ্ধতিতে দীর্ঘমেয়াদি গাছের সাথে স্বল্পমেয়াদি গাছের সমন্বয় করা যায় ।
(৪) কিলার গাছ কেটে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায় ।
অসুবিধা
(১) দীর্ঘমেয়াদি গাছের সাথে স্বল্পমেয়ালি গাছের সমন্বয় করে না লাগানো হলে বাগান লাভজনক হয় না ।
(২) পঞ্চম স্থানের ও চার কোণার গাছের ফল বিভিন্ন সময়ে সংগ্রহ করতে হয় ।
(৩) এক জাতীয় রোগ ও পোকামাকড় অন্য জাতীয় গাছে পরজীবি হতে পারে ।
ত্রিকোণী বা ত্রিভুজ পদ্ধতি সুবিধা
(১) তিনদিক থেকে গাছের অতি পরিচর্যা সহজে করা যায় ।
(২) বাগান দেখতে সুন্দর দেখায় ।
অসুবিধা
(১) এ পদ্ধতিতে অন্যান্য পদ্ধতি অপেক্ষা গাছের সংখ্যা কম হয় ।
(২) নকশা করা কিছুটা ঝামেলাপূর্ণ ।
(৩) জমির অপচয় হয় ।
ষড়ভুজী পদ্ধতি
সুবিধা
(১) এ পদ্ধতিতে এক গাছ হতে অন্য গাছের দূরত্ব সমান থাকে ।
(২) তিন দিক থেকে বাগানের গাছে আন্ত পরিচর্যা করা যায় ।
(৩) বর্গাকার পদ্ধতি অপেক্ষা ১৫ % গাছ বেশি লাগানো যায়
(৪) এ পদ্ধতিতে লাগানো বাগান দেখতে সুন্দর দেখায়
অসুবিধা
(১) এ পদ্ধতিতে অন্যান্য পদ্ধতি (বর্গাকার বাদে) অপেক্ষা গাছের সংখ্যা কম হয় ।
(২) নকশা তৈরি কিছুটা ঝামেলাপূর্ণ ।
(৩) জমির অপচয় হয় ।
চান্স বা সিঁড়ি বাঁধ পদ্ধতি সুবিধা
(১) এ পদ্ধতিতে সুষ্ঠু নকশা প্রণয়ন করে গাছ লাগিয়ে ভূমির ক্ষয় কমানো যায় ।
(২) এ পদ্ধতিতে বর্গাকার পদ্ধতি অপেক্ষা দ্বিগুণ গাছ লাগানো যায় ।
(৩) গাছ লাগানোর জন্য রেখা তৈরির ফলে পাহাড়ের ঢাল দিয়ে বিভিন্ন দিকে চলাফেরা করা যায় ।
(৪) উঁচু দিক হতে পাইপ দ্বারা নিচের দিকে সহজে সেচের পানি প্রবাহিত করা যায় ।
অসুবিধা
(১) এ পদ্ধতিতে অন্যান্য পদ্ধতি অপেক্ষা গাছের সংখ্যা কম হয় ।
(২) নকশা তৈরি কিছুটা ঝামেলাপূর্ণ
মিশ্র ফল বাগান
বাংলাদেশে লোক সংখ্যার তুলনায় জমির মতো বেশি অভাব যে, এখানে ফলের বাগান করতে গিয়ে জমির সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করা আবশ্যক । বর্তমানে বাংলাদেশে ৮২-৯০ লাখ হেক্টর জমি থেকে খাবার যোগান দিতে হচ্ছে প্রায় ১৫ কোটি জনগাষ্ঠেীর । গত ত্রিশ বছরে জনসংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে কিন্তু চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়েনি । বর্তমানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাস করছে গড়ে ৯২৬ জন মানুষ, ফলে মাথাপিছু জমির পরিমাণ একদিকে যেমন কমে যাচ্ছে সেই সাথে কমছে চাষযোগ্য জমির পরিমাণও। অন্যদিকে মোট খাদ্যশস্যের চাহিদার বিপরীতে উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম । সে জন্য অতিরিক্ত খাদ্যঘাটতি মেটাতে নির্ভর করতে হচ্ছে বিদেশি খাদ্য আমদানি এবং দাতাগাষ্ঠেীর সাহায্যের ওপর। অন্যদিকে ফল আমাদের দরিদ্র জনগাষ্ঠেীর নাগালের বাইরে । তাই বেশী পরিমাণ ফল উৎপাদন করে পুষ্টিহীনতা দূর করা সম্ভব । একজন মানুষের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থতার জন্য প্রতিদিন ১২০ গ্রাম করে ফল খাওয়ার প্রয়োজন । কিন্তু আমরা খাই মাত্র ৩৫-৩৮ গ্রাম, যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম ।
আবার প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য একটি দেশের শতকরা ২৫% ঘন বনাঞ্চল তথা উদ্ভিজ্জ আচ্ছাদন থাকা প্রয়াজন । অথচ আমাদের প্রকৃত উদ্ভিজ্জ আচ্ছাদন মাত্র ৮.৫% যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম । সুতরাং জাতীয় চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের বনভূমি বা কৃষি জমি বাড়ার যেখানে কোনো সম্ভাবনা নেই, সেখানে ফলদ ও বনজ গাছের সাথে কৃষি উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের মিশ্র চাষের দিকে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন । প্রচলিত চাষ বিন্যাস রূপান্তরের মাধ্যমে বহুস্তর বিশিষ্ট ফল বাগান করে একক জমিতে ফলন বাড়ানোর বিকল্প নেই ।
মিশ্র বাগান কী ?
মুলত মিশ্র বাগান হচ্ছে একই জমিতে বিভিন্ন চাষযোগ্য বৃক্ষ, বিরুৎ ও গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ প্রজাতির ৩-৪ তর বিশিষ্ট বৃক্ষ রাজী সহযোগে গঠিত উদ্ভিদগুলোর একটি নিবিড় সহাবস্থান ।
মিশ্র ফল বাগানের সুবিধা
এ ধরনের বাগান পদ্ধতিতে ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হয় । বাংলাদেশের মতো ভূমি স্বল্পতার দেশে এ পদ্ধতির বাগান কৃষিতে এক যুগান্তকারী উৎপাদন ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে । ভূমি ছাড়াও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন-আলো, মাটির পুষ্টি উপাদান, পানি ইত্যাদির সর্বাধিক ব্যবহার এ পদ্ধতিতে সম্ভব । এ ধরনের বাগান পদ্ধতিতে চাষকৃত বিভিন্ন উদ্ভিদ খাড়াভাবে বিভিন্ন স্তর থেকে সূর্যালোক গ্রহণ করে । যে পরিমাণ সুর্যের আলো পৃথিবীতে আসে তার ২০-৩০ ভাগ ব্যবহার করে উপরের স্তর অর্থাৎ বৃক্ষ, ২০-৪০ ভাগ ব্যবহার করে মধ্য স্তর অর্থাৎ বিরুৎ এবং সর্ব নিম্ন স্তরে থাকে ছায়া পছন্দকারী উদ্ভিদ যা বাকি ২০-৩০ ভাগ সূর্যের আলো গ্রহণ করে ।
অন্যদিকে গাছের মূলতন্ত্র মাটির বিভিন্ন গভীরতা থেকে পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে যেমন, ছায়া প্রদানকারী উদ্ভিদ মাটির ওপরের স্তর থেকে পুষ্টি নেয়, মধ্যম সতরের উদ্ভিদ মাটির আরো নিচে এবং ওপরের স্তরের উদ্ভিদ মাটির আরো গভীর থেকে পুষ্টি উপাদান সংগ্রহ করে । এতে করে প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি প্রাকৃতিক ভারসাম্যও রক্ষা হয় ।
মিশ্র ফল বাগান পদ্ধতি আর্থিকভাবে কৃষকের জন্য ঝুঁকিমুক্ত । কেননা, কোনো কারণে কৃষক এক স্তরের ফসলপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হলেও অপর স্তর থেকে ফলন পায় । এছাড়াও বছরব্যাপি এ ধরনের বাগান থেকে ফল সংগ্রহের মাধ্যমে অর্থ পাওয়া সম্ভব । কেননা একই জমিতে বিভিন্ন ফসল থাকায় বছরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তা সংগ্রহ ও প্রয়োজনে বিক্রয় করা যায় । এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিজ্জ বৈচিত্র্যতা সংরক্ষণ করা সম্ভব । একই জমিতে বছরের প্রায় সব সময়ই বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিজ্জের উপস্থিতি ফসল চাষে বহুমুখিতার পাশাপাশি ফসল তথা উদ্ভিদের বৈচিত্র্যতা রক্ষায় সহায়ক হয় ।
নিবিড় চাষ করা হয় বিধায় বসতবাড়ির মহিলারা বা বেকার যুবকরা উৎপাদন কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারে । এতে করে বেকার সমস্যা দূরীকরণের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নেও এ ধরনের বাগান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে ।
বাংলাদেশের জন্য বহুস্তরবিশিষ্ট মিশ্র ফল বাগানের কাঠামো
ভূমি সংলগ্ন লতাপাতা সমৃদ্ধ নিম্নস্তর,
বৃক্ষসমৃদ্ধ উচ্চতর এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী স্তর নিয়েই বসতবাড়ীর বহুস্তর বাগান । নিম্নস্তরটিকে দুটি ভাগে ভাগ করে ১মি. এর কম উচ্চতা বিশিষ্ট সর্বনিম্নভরে আনারস, তরমুজ এবং ১-৩ মি. উচ্চতায় কলা, পেঁপে, পেয়ারা, লেবু ইত্যাদি চাষ করা যেতে পারে । ওপরের স্তরটির দুটি ভাগে ভাগ করে ২৫ মি. বেশি উচ্চতায় সুউচ্চ কাঠ ও ফলদ বৃক্ষ যেমন- আম, কাঁঠাল, নারিকেল এবং ১০-১২ মি. উচ্চতায় মাঝারি উচ্চতার ফল যেমন- বামন আকৃতির আম, লিচ, সফেদা ইত্যাদি উদ্ভিদ লাগানো যেতে পারে ।
দীর্ঘমেয়াদি ফল বাগানে কি ধরনের মিশ্র ফসল করা যায় সেগুলো সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো:
১। ক) অধিক সুৰ্য্যালোক পছন্দকারী - কলা, পেঁপে, পেয়ারা, তরমুজ, ফুটি ইত্যাদি ।
খ) মাঝারী সূর্যালোক পছন্দকারী- লেবু, আনারস, ডালিম, পেয়ারা, জামরুল, জামবুরা, করমচা স্ট্রবেরি, মিষ্টিআলু শাক, কলমিশাক ইত্যাদি ।
গ) কম সুর্যালাকে পছন্দকারী লটকন, ইত্যাদি । বাগানে নতুন অবস্থায় উপরোক্ত বিষয় বিচেনা করে কয়েক বছর সূর্যালোক ও মাঝারি সূর্যালোক পছন্দকারী ফসল মিশ্র সাথী ফসল হিসেবে সফলভাবে জন্মানো যায় । পরবর্তীতে ফলগাছ লাগানোর জমিতে ছায়া পড়ে গেলে কম সূর্যালোকে জন্মাতে পারে এমন ফসল চাষ করা উচিত ।
২। ক) দীর্ঘমেয়াদি মূল জাতীয় ফসলের সাথে স্বল্পমেয়াদি সাথী ফসল কোন কোন ক্ষেত্রে জন্মানো যায়। যেমন– আম, কাঁঠাল, লিচু এবং জামের সাথে ডালিম, জামরুল পেঁপে ইত্যাদি চাষ করা যায় ।
খ) গভীর মূল জাতীয় ফসলের সাথে অগভীর মূল জাতীয় ফসল নির্বাচন করতে হবে । যেমন—
i) আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু ইত্যাদির সাথে কলা, আনারস পেঁপে ইত্যাদি ।
ii) কলা, পেঁপে, ডালিম, পেয়ারা, শরিফা, আতা, জামরুল, লেবু ইত্যাদির সাথে তরমুজ, ফুটি ইত্যাদি ।
iii) দীর্ঘমেয়াদী বা বহুবর্ষজীবী ফসলের সাথে ১-৩ বর্ষজীবি ফসল নির্বাচন করতে হবে । যেমন– আম, জাম, কাঁঠাল লিচু ইত্যাদির সাথে কলা, পেঁপে, আনারস, ষ্টব্রেরি, বেগুন ইত্যাদি ।
iv) সাথি ফসল যাতে এ ধান ফসলের ফুল ও ফল ধারণ, ফল বড় হতে বা ফলের গুণগত মানে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে । সে বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে ।
v) সাথী ফসল কোন সময় প্রধান ফসলের সাথে প্রতিযোগিতায় গেলে সাথে সাথে সাথী ফসল কেটে দিতে হবে।
মিশ্র বহুস্তরবিশিষ্ট বাগানের জন্য উদ্ভিদ/ফসল নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ক্ষেত্রের নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখতে হবে ।
বাগানে গাছ লাগানোর জন্য ছায়া পছন্দকারী বা ছায়াসহকারী উদ্ভিদ ফসল হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে ।
নির্বাচিত বিভিন্ন ফসল/উদ্ভিদের সমন্বয় এমন হতে হবে যেন ফসল উৎপাদন চক্র এবং মাত্রা সারা বছর নিয়মিত উৎপাদন নিশ্চিত করতে পারে । আবহাওয়া ও জলবায়ুগত কারণে বছরের কোন কোন সময় ফসল সংগ্রহের পরিমাণ কম বা বেশি হতে পারে; কিন্তু প্রাত্যহিক কিছু না কিছু উৎপাদন যেন অব্যাহত থাকে । অর্থাৎ বছরের প্রায় সবসময়ই যেন ফলন এবং উপজাত হিসেবে জ্বালানি ও অন্যান্য উপকরণ পাওয়া যায় ।
বাগানে উৎপাদিত সামগ্রী কৃষকের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে এবং অতিরিক্ত আয়, দৈবাৎ কৃষি ফসল হানিতে ও দুফসলের মধ্যবর্তী সময়ে কৃষককে নিরাপত্তা দিতে সক্ষম হবে। পারিবারিক সদস্যদের ন্যূনতম শ্রমের মাধ্যমেই বাগানে গাছের পরিচর্যা ও ফসল সংগ্রহ করা যায় তা নিশ্চিত হতে হবে ।
অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
১। স্বল্পমেয়াদি ফল গাছ কত দিন ফল দিয়ে থাকে ?
২ । ষড়ভূজ পদ্ধতিতে বর্গাকার পদ্ধতি অপেক্ষা কত শতাংশ গাছ বেশি লাগানো যায় ?
৩ । মিশ্র বাগানের সুবিধা কী ?
৪। সাথী ফসল কী ?
৫ । কন্টুর বা ঢাল এবং সিড়ি বাঁধ পদ্ধতিতে কিভাবে চারা রোপণ করা হয় ?
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
১। বাগানের নকশা কত ধরনের ?
২। কুইনকাংশ পদ্ধতিতে প্রতিটি বর্গের মাঝে লাগানো গাছকে কী বলে?
৩ । ষড়ভুজী পদ্ধতিতে বর্গাকার পদ্ধতির চেয়ে কত ভাগ বেশি গাছ লাগানো যায় ?
৪ । ফল বাগানের পরিকল্পনার জন্য কি কি বিষয় বিবেচনা করা দরকার, তা লিপিবদ্ধ কর ।
৫ । বর্গাকার পদ্ধতির সুবিধা অসুবিধা লেখ ।
৬। মিশ্র ফল বাগান বলতে কি বোঝায়?
৭ । ফল বাগানের জন্য কেন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় সে সম্পর্কে লেখ ।
রচনামূলক প্রশ্ন
১। ফল বাগান পরিকল্পনার নীতিমালা সম্পর্কে বর্ণনা কর ।
২ । ফল গাছ লাগানোর নকশাগুলোর নাম লেখ । চারা রোপণের জন্য নকশা প্রণয়নে করণীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা কর ।
৩ । ফল বাগানে গাছ রোপণ প্রণালির গুরুত্ব কী ? ফল বাগানে বিভিন্ন গাছ রোপণ প্রণালি বর্ণনা কর ।
৪ । বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মিশ্র ফল বাগান তৈরির পরিকল্পনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর ।
জমি প্রস্তুতকরণ
ফল চাষের জন্য জমি তৈরি করা অন্যতম কাজ । স্থান নির্বাচনের কাজ শেষ হলে নির্বাচিত স্থানের ভূমিকে নকশা করার উপযোগী করে তৈরি করে নিতে হয় । এ উদ্দেশে নিচু জমি ভরাট করা, মাটি সমতল করা, সুবিধাজনক ভাবে প্লট তৈরি করা, সেচ নিকাশের জন্য নালা, বাগানের অভ্যন্তরীন রাস্তা ও গার্ডসেড ইত্যাদির জন্য স্থান নির্বাচন করা প্রয়োজন । জমির বন্ধুরতা ও মাটির প্রকৃতি অনুযায়ী এসব কাজ এমনভাবে করতে হবে যেন পরবর্তীকালে বাগানের বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা সহজ ও কম ব্যয়বহুল হয় এবং মূল্যবান জমি নষ্ট না হয় । জঙ্গল ঘেরা জমিকে কলা বাগানে পরিণত করতে হলে প্রথমে সমস্ত জঙ্গল ও অপ্রয়োজনীয় গাছ শেকড়সহ উপড়ে ফেলে মাটিকে সমান করে সুবিধাজনকভাবে প্লটে বিভক্ত করে নিতে হবে । পতিত জমি হলে প্রয়োজনানুসারে প্লট আকারে তৈরি করে নিতে হবে। স্বল্প মেয়াদি ফল যেমন কলা, পেঁপে, আনারস, তরমুজ ইত্যাদির জন্য ৫-৬ টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে । দীর্ঘমেয়াদি ফসলের ক্ষেত্রে জমি গভীরভাবে চাষ দিতে হবে । পাহাড়ী এলাকায় ভূমি ক্ষয়ের ব্যাপারটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে এবং ক্ষয়রোধ করার জন্য মাটি তেমন ওলট পালট না করেই বাগান তৈরি করতে হবে । ভালোভাবে জমি চাষের ফলে অনেক বিষাক্ত পদার্থ অপসারিত হয়। এতে করে চারা লাগানোর পর সহজে চারা রোপণজনিত ধকল সহ্য করে বেড়ে উঠতে পারে ।
সারণি – ক
গাছের আকৃতি অনুযায়ী চারা বসানোর গর্তের মাপ নিম্নে দেয়া হলো
ফল গাছ রোপণের জন্য গর্ত তৈরীর কৌশল
বাগানে কাঙ্খিত পরিমাণ ফলন পেতে হলে চারা রোপণের জন্য গর্ত করা এবং গর্তে পরিমাণ মত সার প্রয়োগ করা অপরিহার্য । চারাগাছ লাগানোর সময় পরিমিত আকারের গর্ত খনন করা আবশ্যক । তবে গর্তের আকার নির্ভর করে চারার আকার ও গাছের প্রজাতির উপর । ফল গাছের চারা রোপণের জন্য অন্তত পক্ষে ৩টি কাজ করা আবশ্যক। যথা—
(ক) সঠিক সময় ও সঠিক মাপে গর্ত খনন
(খ) গর্তে উপযুক্ত পরিমাণ সার প্রয়োগ ও
(গ) গাছের বৈশিষ্ট্য মোতাবেক চারা রোপণ ও পরিচর্যা
ক) গর্ত খনন: চারা রোপণের জন্য গর্ত খননের গভীরতা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মতামত আছে । গর্ত বর্গাকার ও অগভীর হলে চারার শেকড় কুণ্ডলী পাকিয়ে যায় এবং গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় । তবে যতদূর সম্ভব গর্ত যথেষ্ঠ গভীর ও চওড়া হওয়া বাঞ্চনীয় । চারা অবস্থায় শেকড় দুর্বল থাকে তাই গর্তের চারিপাশের শক্ত মাটিভেদ করে সহজে খাদ্য ও রস সংগ্রহ করতে পারে না। গর্তের আকার বড় করে এবং উপরের মাটি নিচে দিয়ে গর্ত ভর্তি করে দিতে হয় । এতে দুর্বল ও নরম মুল সমূহ নরম মাটি হতে সহজে রস নিয়ে তাড়াতাড়ি বড় হতে পারে । অনুর্বর মাটিতে এই পদ্ধতি অনুশীলন অত্যন্ত ফলপ্রসু । শুষ্ক ও বৃষ্টিপাতহীন অঞ্চলের মাটিতে শক্ত ও অপ্রবেশ্য স্তর থাকে । এক্ষেত্রে শক্তিশালী যন্ত্র ব্যবহার করে শক্তস্তর ভেঙ্গে দিয়ে ভালভাবে গাছ জন্মানো যায় ।
বৃক্ষ জাতীয় গাছের জন্য ৫ ফুট ব্যাস ও ৪ ফুট গভীর করে গর্ত করা যায় । গর্ত খননের পর উপরের মাটি নিচে দিয়ে গর্ত পুরণ করতে হয় । এতে গাছের শেকড় খুব ভালভাবে বিস্তার লাভ করতে পারে । বড় গর্তে রোপণকৃত গাছের শিকড় ১ বৎসরে ৭.৫ ফুট গভীরে এবং পাশে ৬ ফিট পর্যন্ত ছড়াতে পারে । অথচ ছোট গর্তে রোপণকৃত গাছের শেকড় ১ বৎসর ২ ফুটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে ।
চারা রোপণের জন্য এক সপ্তাহ হতে প্রায় একমাস পূর্বে গর্ত খননে অনেকক্ষেত্রেই তেমন কোন গুরুত্ব বহন করে । বেশি আগে গর্ত খনন করে রাখলে গর্তের পাশের ও তলদেশের মাটি শক্ত হয়ে যায় । এরূপ ক্ষেত্রে চারা রোপণের আগে পুনরায় গর্ত খনন করে নিতে হয় ।
অনুর্বর মাটিতে গর্তের উপরের মাটির সাথে সার মিশিয়ে নিচে দিয়ে গর্ত ভরাট করা হলে গাছের তেজ বেশি হয় । কিন্তু চারার গোড়ার চারপাশে যদি নিয়মিত সারযুক্ত মাটি প্রয়োগ না করা হয়, তাহলে গাছের বৃদ্ধি আস্তে আস্তে কমে যায় ।
ফল গাছ রোপণের জন্য জাত ভেদে গর্ত করার সময়
বর্ষাকাল অর্থাৎ মে থেকে জুলাই মাস জাত ভেদে সকল ধরনের চারা লাগানোর সবচেয়ে উপযুক্ত সময় । চারা লাগানোর পর এ সময় সেচ দেয়ার প্রয়োজন হয় না । বর্ষা বেশী হলে বর্ষার পরও চারা লাগানো যেতে পারে । মেঘলা দিনে বা বিকেলের দিকে চারা লাগানো ভালো । পানি সেচের ব্যবস্থা থাকলে বসন্তের প্রথমেও চারা লাগান যায় । জাতভেদে সকল ধরনের ফল গাছ রোপনের জন্য বর্ষার আগে অর্থাৎ বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ মাসে গর্ত করা উত্তম । গাছের প্রয়োজনীয় খাবার সরবরাহ এবং শেকড়ের বৃদ্ধির জন্য গাছ রোপণের আগে গর্ত করা একান্ত প্রয়োজন । ভিন্ন ভিন্ন গাছের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দুরত্বের এবং আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে । সাধারণত কোন গাছের জন্য কী আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে, তা নিম্নোক্ত বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে । যথা—
ক) গাছের আকৃতি
খ) শেকড়ের গভীরতা
গ) শেকড়ের বিস্তৃতি
ঘ) চাষের মেয়াদকাল
ঙ) গাছের খাবারের চাহিদা ইত্যাদির ওপর
গাছের আকার, মৌসুম ও মাটি ভেদে গর্তের আকার ও আয়তন
জমি তৈরি সম্পন্ন হলে রোপণ প্রণালী নির্বাচিত করে নির্দিষ্ট দুরত্বে গাছ লাগান উচিত । গাছ লাগানোর জন্য নির্বাচিত স্থানে গর্ত করা উচিত । গর্ত তৈরির জন্য নিম্নবর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে ।
গর্ত তৈরির ধাপ: গর্ত তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যেমন- কোদাল, বেলচা, খুন্তি ইত্যাদি আগেই যোগাড় করতে হবে।
১) জমিতে গর্ত করার আগে চারা রোপণের নকশা মোতাবেক ফিতা বা কাঠির সাহায্যে মাপ দিতে হবে । মাপ দিয়ে নির্ধারিত দূরত্বে খুঁটি পুঁতে চারা রোপণের স্থান চিহ্নিত করতে হবে ।
২) চারা রোপণের ২০-৩০ দিন আগে গর্ত তৈরি করে প্রতি গর্তে পরিমাণ মত সার দিয়ে মাটি ভরাট করে দিতে হবে । গর্তের মাটি এমনভাবে চেপে দেয়া দরকার যাতে মাটি আলগা না থাকে ।
৩) যে সব জায়গায় উইপোকার আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে সেখানে উইপোকা প্রতিরোধক ঔষধ ব্যবহার করতে হবে । নারিকেল গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে এটি খেয়াল রাখা উচিত।
৪) গাছের আকৃতি বিবেচনা করে গর্তের ব্যাস ও গভীরতা নির্ণয় করতে হবে । যেমন—
(ক) ছোট আকারের গাছের জন্য গর্তের ব্যাস হবে ৫০ সে:মি: এবং গভীরতা হবে ৫০ সে:মি: (খ) মাঝারি আকারের গাছের জন্য গর্তের ব্যাস হবে ৬০ থেকে ৭৫ সেমি এবং গভীরতা হবে ৬০-৭৫ সেমি (গ) বড় বা বৃক্ষ জাতীয় গাছের জন্য গর্তের ব্যাস হবে প্রায় ১ মিটার এবং গভীরতা হবে প্রায় ১ মিটার ।
ছক: গাছের আকৃতি অনুযায়ী চারা লাগানোর গর্তের মাপ ও চারার দুরত্ব
গাছের আকৃতি | চারা লাগানোর গর্ভের মাপ | একটি চারা থেকে আরেকটি চারার দূরত | গর্ত খনন বা রোপনের মৌসুম |
| (ক) বড় বা বৃক্ষজাতীয় গাছ (আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, নারিকেল, বেল তেঁতুল ইত্যাদি) | ১ মিটার ব্যাস ও মিটার গভীর বা ৯০ ৯০ সে:মি: | ৭-৮ মিটার | বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র-আশ্বিন পর্যন্ত |
| (খ) মাঝারি গাছ (পেয়ারা, আতা, শরিফা, সফেদা, লেবু, ডালিম, পীচ, জামরুল, জাম্বুরা, অরবরই ইত্যাদি) | ৬০ সে:মি: মিটার ব্যাস ও ৬০ সে:মি: গভীর বা ৭৫৭৫ সে:মি: | ৪ মিটার | বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র-আশ্বিন পর্যন্ত |
| (গ) ছোট গাছ (কলা, পেঁপে, সুপারি ইত্যাদি) | ৫০ সে:মি: ব্যাস ও ৫০ সে:মি: গভীর | ২ মিটার | বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ থেকে |
| (ঘ) খুব ছোট (আনারস, স্ট্রবেরী ইত্যাদি) | ১৫ সে:মি: ব্যাস ও ১৫ সে:মি: গভীর | ৩০ সে:মি: | বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ থেকে |
মাটির বুনট বুঝে গর্তের আকার কম বা বেশি করা যেতে পারে । যেমন- বেলে দোঁআশ মাটির জন্য গর্তের আকার কিছুটা ছোট করা যেতে পারে । কেননা বেলে মাটিতে গর্ত বড় করা হলে চারপাশের পাড় ভেঙ্গে গর্ত ভরাট হয়ে যেতে পারে । আবার এটেল বা এটেল দোআশ মাটির জন্য গর্তের আকার কিছুটা বড় করা যেতে পারে । বৃক্ষ শ্রেণির গাছের জন্য ৫ ফুট ব্যাস ও ৪ ফুট গভীরতাবিশিষ্ট গর্ত খনন করা যেতে পারে । বড় গর্তে রোপণকৃত চারার শেকড় ১ বছরে ৭.৫ ফুট গভীরে এবং পাশে ৬ ফুট পর্যন্ত ছড়াতে পারে । অথচ ছোট গর্তে রোপণকৃত গাছের শেকড় ১ বছরে ২ ফুটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে । কারণ ছোট গর্তের চারিদিকের শক্ত মাটির স্তুর থাকে ।
(৫) গর্ত খনন করার সময় গর্তের খননকৃত মাটি ছড়িয়ে রেখে শুকায়ে নেয়া ভাল । গর্তের উপরিভাগে ১৫ সে:মি: বা তিনভাগের দুইভাগ মাটি একদিকে রাখতে হবে । অনুরূপভাবে গর্তের নিচের দিকের তিনভাগের একভাগ মাটি অন্য দিকে রাখতে হবে । গর্তের উপরের দিকের মাটিতে জৈব পদার্থ বেশি পরিমাণে থাকে ।
(৬) গর্তের উপরের মাটির সাথে প্রয়োজনীয় সার মেশানোর পর গর্ত ভরাট করার সময় উপরের অংশের মাটি নিচে দিতে হবে। আর নিচের অংশের আলাদা করে রাখা মাটি গর্তের উপরিভাগে দিতে হবে। জমির উপরিভাগের মাটি বেশি উর্বর । উপরের মাটি নিচে দিলে গাছ দ্রুত বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান তাড়াতাড়ি পাবে ।
গর্তে সার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা
ফল গাছে সার প্রয়োগের মাধ্যমে পুষ্টি সরবরাহ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অন্য গাছের চেয়ে ফল গাছে মাটি হতে প্রচুর খাদ্য ও পুষ্টি টেনে নেয় এবং এই পুষ্টি ক্রমাগত কমার ফলে মাটির উর্বরতা শক্তি কমে যায় । ফলে মাটির উৎপাদনক্ষমতা হ্রাস পায়, ফলশ্রুতিতে ফলন কমে যায় ।
সব গাছের সমান পরিমাণ খাবার লাগেনা । আবার গাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন পরিমাণ পুষ্টি উপাদান প্রয়োজন হয় । নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর ফল গাছের সারের মাত্রা নির্ভর করে ।
১। ফল গাছের ধরন
২। গাছের আকার ও বয়স
৩। ফলের জাত
৪ । গাছের বৃদ্ধির স্বভাব
৫ । গাছের বৃদ্ধির পর্যায়
৬ । আবহাওয়া
৭ । উৎপাদন মৌসুম
৮ । মাটির প্রকৃতি এবং উর্বরতা শক্তি
৯। সার ব্যবহার পদ্ধতি
১০ । চাষাবাদ পদ্ধতি
১১ । সেচ ব্যবস্থাপনা
১২। জমির ফসল বিন্যাস
সার ব্যবহারে গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় এবং ফলের উৎপাদন বেড়ে যায় কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে ত্রুটিপূর্ণ সার ব্যবহারের ফলে গাছের ক্ষতিও হতে পারে । অসময়ে গাছে সার ব্যবহার করলে গাছের ফল ধারণ ব্যাহত হতে পারে । তাই সঠিক সময়ে, সঠিক পদ্ধতিতে ও পরিমাণে সার ব্যবহার করা উচিত ।
গর্তে সার প্রয়োগের মাত্রা নির্ধারণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি
গাছের (ছোট বা বড়) আকৃতির ওপর নির্ভর করে ছকে (ছক-১) বর্ণিত ও অন্যান্য নিয়ম মোতাবেক গোবর বা কম্পাস্টে সার, হাড়ের গুড়া বা টিএসপি সার, ছাই বা এমপি সার মাটির সাথে মেশাতে হবে ।
চারার উপযুক্ত বৃদ্ধির জন্য গর্তে সময়মত সার ব্যবহারের ফলে গাছের দৈহিক বৃদ্ধি তাড়াতাড়ি হয় এবং ফল ধরার পরিমাণ বেড়ে যায় । এছাড়া অসময়ে সার ব্যহার করা হলে সারের অপচয় হয় এবং গাছের ফল ধারণে অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । সার মিশ্রিত মাটি দিয়ে গর্ত ভরাট করার পর মাটি শুকনা থাকলে হালকা সেচ দিতে হবে । এর কমপক্ষে ১০-১২ দিন পর গাছ লাগাতে হয় । কেননা সার প্রয়োগের পর পর চারা লাগানো হলে রাসায়নিক সারের বিক্রিয়ায় চারা মারা যেতে পারে । রাসায়নিক সার গর্তের নিচের ৩০ সেমি. মাটির সাথে মিশানো উত্তম । গাছের আকার বিবেচনা করে হাড়ের গুড়ার পরিবর্তে তার অর্ধেক পরিমাণ টিএসপি এবং ছাই-এর পরিবর্তে প্রতি কেজি ছাই এর জন্য ১০০ গ্রাম এমপি সার ব্যবহার করা যেতে পারে।
ছক: গাছের আকৃতির ওপর নির্ভর করে
সার মিশ্রিত মাটি গর্তে দেয়ার পর পা দিয়ে মাটি চেপে দিতে হবে । কেননা বৃষ্টিপাত বা সেচ দেয়ার পর গর্তের মাটি নিচু হয়ে গেলে পানি জমে চারার ক্ষতি হতে পারে । সাধারণত চারা রোপণের পূর্বে গর্তে যে পরিমাণ সার দেয়া হয় তার অর্ধেক পরিমাণ সার বর্ষার শুরুতে একবার এবং বর্ষার শেষে বাকী অর্ধেক দিতে হবে। পরবর্তীতে চারার বৃদ্ধির সাথে সাথে বৎসরওয়ারী সারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। এভাবে চারা লাগানোর পর হতে ফলবান হওয়া পর্যন্ত যত্ন নিতে হবে, যাতে গাছ সুস্থ সবল ও সতেজ থাকে । সার প্রয়োগের সময় চারার একেবারে গোড়ায় সার দেয়া উচিত নয় । চারা বা ছোট গাছের ক্ষেত্রে চারার গোড়া হতে কমপক্ষে ০.৫ মিটার ও বড় গাছের ক্ষেত্রে ১ মিটার দূর দিয়ে সার ব্যবহার করতে হবে । তবে সাধারণভাবে চারার পাতা যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে ঠিক ততদুর পর্যন্ত দূর দিয়ে সার দিতে হবে । কারণ পাতার বিস্তৃতির সাথে সাথে শেকড়ের বিস্তৃতির একটা সম্পর্ক আছে। শুধু মাটির উপর সার দিলে সারের অপচয় হবে । তাই দুপুর বেলায় যতদূর গাছের ছায়া পড়ে ততদূর দিয়ে বৃত্তাকারে দাগ দিয়ে নিয়ে সেটুকু স্থানের মাটি আলগা করতে হবে । মাটি আলগা করার সময় কোদাল বা খুরপি ব্যবহার করতে হবে । চারার চারিদিকে বৃত্তাকারভাবে ঘুরে ঘুরে মাটি আলগা করা প্রয়োজন । এতে চারার শেকড় কম কাটার সম্ভাবনা থাকে । এছাড়া স্থানে স্থানে গর্ত করে বা চিকন নালা কেটেও সার প্রয়োগ করা যায় । সার দেয়ার পর মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে । গর্ত বা নালা করা হলে তা সার মিশ্রিত মাটি দিয়ে ভরাট করে দিতে হবে । সার দেয়ার পর হালকা পানি দেয়া উচিত । তাহলে সার থেকে খাদ্য উপাদান গাছ সহজেই গ্রহণ করতে পারবে । সার
ছক: চারা লাগানোর পর থেকে উপযুক্ত হওয়া পর্যন্ত গাছ প্রতি জৈব সারের পরিমাণ (কেজিতে)
রাসায়নিক সারের ক্ষেত্রে টিএসপি'র পরিবর্তে হাড়ের গুড়া সার এবং এমপি'র পরিবর্তে ছাই ব্যবহার করা যেতে পারে । তবে এক্ষেত্রে টিএসপি সার যে পরিমাণ ব্যবহার করা হয় তার দ্বিগুণ পরিমাণ হাড়ের গুড়া সার ব্যবহার করতে হবে । আর এমপি সার যে পরিমাণ ব্যহার করা হয় তার আটগুণ পরিমাণ ছাই ব্যবহার করতে হবে । সারের মোট পরিমাণকে দু'ভাগে ভাগ করে একভাগ গ্রীষ্মের শুরুতে এবং আর একভাগ বর্ষার শেষে প্রয়োগ করা ভালো ।
ফল গাছের জন্য সার (দীর্ঘমেয়াদি ফল গাছের জন্য)
সারের নাম | গর্তে সারের পরিমাণ | বাৎসরিক বৃদ্ধির পরিমাণ | ১০ বছরে অধিক বৎসের জন্য |
| পচা গোবর | ১০ কেজি | ১০ কেজি | ১০০ কেজি |
| ইউরিয়া | ১০০ গ্রাম | ১০০ গ্রাম | ৬০০ গ্রাম |
| টিএসপি | ২৫০ গ্রাম | ১০০ গ্রাম | ২ কেজি |
| এমপি/ছাই | ১০০ গ্রাম/১ কেজি | ৫০ গ্রাম/৫০০ গ্রাম | ৬০০ গ্রাম/৬ কেজি |
| হাড়ের গুড়া | ৫০০ গ্রাম | ২০০ গ্রাম | ৪ কেজি |
উৎস: ফুল ফল ও শাকসবজী - কামাল উদ্দিন আহমেদ
সারের মোট পরিমাণকে দুভাগ করে এক ভাগ বর্ষার শুরুতে ও অপর ভাগ বর্ষার শেষে মাটিতে প্রয়োগ করতে হয়।
অতি সংক্ষিত প্রশ্ন
১ । বড় গাছ রোপণের গর্তের মাপ কত ?
২। গর্তের আকার কিসের উপর নির্ভর করে ?
৩ । চারা বা ছোট গাছের ক্ষেত্রে চারার গোড়া হতে কমপক্ষে কত দূর দিয়ে সার ব্যবহার করতে হয় ?
৪ । ফল গাছে কখন সেচ দিতে হয় ?
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
১। ফল গাছ রোপণের জন্য গর্ত তৈরির কৌশল বর্ণনা কর ।
২ । গাছ রোপণের জন্য জাতভেদে গর্ত করার সময় উল্লেখ কর ।
৩ । গর্তে সার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর ।
৪ । গাছ রোপণের জন্য জাতভেদে গর্তের আকার কিরূপ হওয়া উচিত ।
৫ । নিম্নলিখিত আকৃতির গাছ রোপণের জন্য গর্তের আকার লেখ । বড়, মাঝারি, ছোট ও খুব ছোট ।
রচনামূলক প্রশ্ন
১ । চারা রোপণের জন্য গর্ত তৈরির ধাপগুলো বর্ণনা কর ।
২। জমিতে গাছ লাগানোর জন্য গর্তকরণ ও সার প্রয়োগ সম্বন্ধে যা জান লেখ ।
৩ । গাছের আকার, মৌসুমে ও মাটি ভেদে গর্তের আকার ও আয়তন সম্পর্কে বর্ণনা দাও ।
৪ । গর্তে সার প্রয়োগের মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা কর ।
জমিতে বা বাগানে চারা রোপণের পর হতে ফল সংগ্রহের পূর্ব পর্যন্ত গাছের যথাযথ বৃদ্ধি ও ফল ধারনের জন্য যে সমত পরিচর্যা এবং সেই সাথে স্থায়ী গাছের জন্য একবার ফল ধরা পর্যন্ত যে সমস্ত পরিচর্যা করা হয় সেগুলোকে অন্তবর্তীকালীন বা আন্তপরিচর্যা বলে ।
ফলচাষে অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যার ধাপ ফল বাগানে বিভিন্ন অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যার মধ্যে রয়েছে আন্তর্ষণ, আগাছা দমন, শূন্যস্থান পূরণ, মালচিং, পানিসেচ ও নিষ্কাশন, সার প্রয়োগ, মাচা দেয়া, অঙ্গা ছাঁটাই, সাথী ফসলের চাষ, ভূমিক্ষয় রোধ, পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন ইত্যাদি । নিম্নে বিভিন্ন ধরনের পরিচর্যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো-
১) আকর্ষণ বা ইন্টার টিলেজ (Inter-tillage)
আগাছা দমন ও জমিতে রস সংরক্ষণের জন্য বর্ষার আগে এবং বর্ষার শেষে আচঁড়া বা কোদাল ইত্যাদির সাহায্যে ফল গাছের চারদিকে কুপিয়ে এ কাজ সম্পন্ন করা হয় । এতে করে মাটির অভ্যন্তরে অনায়াসে পানি ও বায়ু চলাচল করতে পারে। আকর্ষণের ফলে মাটিতে বসবাসকারী উপকারী জীব ও জীবাণুসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় ও গাছের খাদ্যোপাদান আহরণে সুবিধা হয় । যথারীতি/নিয়মিত আন্তকর্ষণ সম্পন্ন করলে মাটির স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় ও পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষতিকর আগাছা থেকে জমি মুক্ত থাকে ।
২) শূন্যস্থান পূরণ
জমিতে চারা রোপণের পর অনেক সময় বিভিন্ন কারণে ফলগাছের চারা মারা যায় এবং শূন্য স্থানের সৃষ্টি করে । এতে একদিকে যেমন বাগানের সৌন্দর্য হানি হয় অন্যদিকে জমির অপচয় হয় এবং গাছের সংখ্যা কমে গিয়ে বাগানের ফলন কমে যায় । তাই যথাসম্ভব শূন্যস্থানে একই জাতের ও সমবয়সের চারা রোপণ করা উচিত ।
৩) মালচিং
মালচিং-এর বাংলা অর্থ আচ্ছাদন দেয়া। মাটির রস সংরক্ষণ এবং আগাছা দমনের জন্য মালচিং খুবই উপকারী । কচুরীপানা, করাতের গুড়া, চিটাধান, গাছের শুকনা পাতা, খড় ইত্যাদি মালচিং-এর জন্য ব্যবহৃত হয় ।
৪) পানি সেচ ও নিষ্কাশন
গাছের বৃদ্ধি ও ফল ধারনের জন্য পানি অত্যাবশ্যক। অগভীরমূলী ফলের বাগানে শুষ্ক মৌসুমে পানি সেচের ব্যবস্থা করা খুবই জরুরি। অনেক ফল গাছ আবার জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না । বর্ষাকালে আমাদের দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বিধায়, গাছের গোড়ায় যাতে পানি না জমে থাকে সেজন্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা খুবই জরুরি। ফল গাছের জন্য প্রয়োজনে সেচের ব্যবস্থা করা এবং জমে থাকা পানি সরানোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ।
৫) সার প্রয়োগ
বাগান হতে ভালো ফলন পেতে হলে ফল গাছে নিয়মিত সার প্রয়োগ দরকার । কিন্তু আমাদের দেশের কৃষকরা ফল বাগানে সার প্রয়োগে অনীহা প্রকাশ করে থাকেন । এ জন্য বাগানে ফলনও অনেক কম হয়ে থাকে । গাছের বয়স, আকার, মাটির উর্বরতা, উৎপাদন মৌসুম, গাছের প্রজাতি ইত্যাদির উপর সার প্রয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে । ফল গাছে নির্ধারিত মাত্রায় দু'বার সার প্রয়োগ করতে হয় । গ্রীষ্মের শুরুতে এবং বর্ষার শেষে ফল গাছে সার প্রয়োগ করা আবশ্যক।
৬) বাউনি বা মাচা দেয়া
লতানো প্রকৃতির ফল যেমন - আঙ্গুর ও প্যাশন ফ্রুট গাছ ভালোভাবে বেড়ে উঠার জন্য বাঁশ, কঞ্চি, পাটকাঠি বা সম্ভব হলে তার দিয়ে মাচা করে দিতে হয়। সময়মত বাউনি না দিলে এসব গাছের বৃদ্ধি ঠিকমত হয় না বিধায় ফলনও কমে যায় ।
ফল বাগানে আগাছা দমনের উপকারিতা
কৃষি খামার স্থাপনের উদ্দেশ্য হলো অধিকতর উৎপাদান । কিছু রোগ ও কীটপতঙ্গের ন্যায় আগাছা ও উদ্যান মাঠ ফসলের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে উৎপাদন ব্যাহত করে। প্রাথমিকভাবে আগাছাজনিত কারণে ফসলের যে ক্ষতি হয় তা বোঝা না গেলেও সামগ্রিকভাবে কীটপতঙ্গ ও রোগজনিত কারণের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি এদের দ্বারা হয় । আসলে আগাছা ফসল উৎপাদনকারীদের জন্য অবাঞ্চিত বা অনাকাংক্ষিত গাছ। বাংলাদেশে আগাছার জন্য মাঠ ও উদ্যান ফসলের উৎপাদন ২৫ শতাংশ পর্যন্ত কম হয় বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। অতএব, মাঠ ও উদ্যান ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে ক্ষতিকর আগাছা শনাক্ত করে তা সম্পূর্ণরুপে ধ্বংস করতে হবে । আগাছা ফসলের মারাত্মক শত্রু । আগাছা জায়গা দখলসহ খাদ্য উপাদান, পানি, সূর্যরশ্মি এবং বাতাসের জন্য ফল গাছের সাথে প্রতিযোগিতা করে এবং রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে । সুতরাং প্রথম হতে এদের শনাক্ত করে ধ্বংসের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্বল্প মেয়াদী ফলগাছের জন্য আগাছা দমন একটি অন্যতম করণীয় কাজ । দীর্ঘমেয়াদি ফলের ক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায় আগাছা দমনের প্রয়োজন হলেও পরবর্তীতে তা খুব দরকার হয় । কারণ আগাছা পরবর্তীতে দীর্ঘ মেয়াদী ফল গাছের সাথে পালা দিয়ে টিকে থাকতে পারে না ।
তবে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী ফল বাগানে প্রাথমিক অবস্থায় আগাছা দমন অতীব গুরুত্বপূর্ণ । কেননা গাছের বাড়ন্ত সময়ে আগাছা ফল গাছের জন্য প্রদত্ত সার ও অন্যান্য খাদ্য উপাদান, সূর্য রশ্মি ও বাতাসের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় । এই সময় আগাছা দমনের ব্যবস্থা নিয়ে আন্ত চাষের মাধ্যমে আগাছাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলে এগুলো পরবর্তীতে পঁচে জৈব পদার্থ হিসেবে মাটির সাথে মিশে মাটির গুণাগুণ বৃদ্ধি করে। আগাছা শুধুমাত্র ফসলের উৎপাদন বা ফলনহ কমায় না বরং ফসলের গুণাগুণও মারাত্মকভাবে হ্রাস করে ।
দীর্ঘ মেয়াদী বাগানের জন্য রোপণকৃত ফল গাছের প্রাথমিক দিকে আগাছা খাদ্যে ভাগ বসায় । এ জন্য গাছ রোপণের পরবর্তী পর্যায় থেকে শুরু করে প্রতি বছর বর্ষার প্রারম্ভে এবং বর্ষার শেষে ফল বাগানের আন্ত চাষের মাধ্যমে আগাছা দমনের ব্যবস্থা নিতে হয় । গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধি, বিকাশ ও মানসম্মত ফলনের জন্য ফল বাগানে গাছের গোড়া সব সময় আগাছা মুক্ত রাখা উচিত। চারার গাড়ার চারদিকে অন্তত এক মিটার পরিধির মধ্যে যেন কোন আগাছা না জন্মে সেদিকে খেয়াল রেখে নিয়মিত নিড়ানি দিতে হয় । মাটির মধ্যে বায়ু যেন ঠিকমত চলাচল করতে পারে এ জন্য ১২-১৫ সে:মি: গভীর করে চারধারের মাটি নিড়ানী দিয়ে আলগা রাখতে হয়। বছরে ২-৩ বার বয়স্ক বা ফলন্ত গাছের গোড়ার চারিদিক কয়েক মিটার পর্যন্ত (সাধারণত দুপুর বেলা যে পরিমাণ এলাকায় ছায়া পড়ে) ১২-১৫ সে:মি: গভীর করে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে মাটি আলগা রাখা প্রয়োজন । খেয়াল রাখতে হবে মাটি কুপানারে সময় যেন গাছের শেকড় বেশি কাটা না পড়ে ।
ফল গাছে প্রনিং-এর প্রয়োজনীয়তা
ফল গাছে প্রনিং-এর প্রয়োজনীয়তা গাছের অপ্রয়োজনীয় কোন অংশকে কেটে সরানোকে সাধারণভাবে ছাঁটাইকরণ বা প্রুনিং বলা হয় । প্ৰধানত: দুটি উদ্দেশে গাছের অঙ্গ ছাঁটাই করা হয়। যথা— গাছের কাঠামো গঠন এবং ফুল ও ফলের সংখ্যা ও গুণগত মানের উন্নতি সাধন । বোঝার সুবিধার্থে গাছের কাঠামো গঠনের উদ্দেশে ছাঁটাইকরণকে ট্রেনিং (Training) নামে অভিহিত করা হয় । অপরপক্ষে ফুল ও ফলের গুণগত মানের জন্য ছাঁটাইকরণকে প্রনিং (Pruning) বলা হয়।
প্রুনিং-এর সময় (Time of pruning)
গাছের সুপ্তাবস্থা (dormant period) অঙ্গ ছাঁটাই-এর জন্য উপযুক্ত সময় । গাছ বৃদ্ধির সময় ছাঁটাই পরিহার করা উচিত । পত্রপতনশীল গাছের বেলায় পাতা পড়ে যাওয়ার পরই ছাঁটাই করা যেতে পারে । আবার কুঁড়ি বের হওয়ার অনেক আগেই ছাটাই-এর কাজ সারা চাই। বেল, আঙ্গুর, শরীফা, কামরাঙ্গা, আমড়া প্রভৃতি ফল গাছের জন্য শীতকাল ছাঁটাইয়ের উপযুক্ত সময় । চির সবুজ (evergreen) গাছের বেলায় ফল সংগ্রহের পর পরই ছাঁটাই করার উপযুক্ত সময় । কুল, কাঁঠাল, আম, লিচু, পেয়ারা, প্রভৃতি ফল গাছের জন্য এ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।
কোন গাছের জন্য কিরূপ ছাঁটাই
কম বয়স্ক ও যে সমস্ত গাছে ফলোৎপাদন শুরু হয় নাই সে সমস্ত গাছের জন্য এবং কমবয়সী ফলোৎপাদনকারী গাছের বেলায় হালকা ছাঁটাই প্রয়োজন। পুরাতন গাছের ক্ষেত্রে সারা গাছ জুড়ে অধিক সংখ্যক ছাঁটাই করা প্রয়োজন । মৃত ও রোগাক্রান্ত শাখা দ্রুত ছাটাই করা উচিত । অতি পুরাতন এবং কম ফল ধরে এমন গাছে কখন কখনও ও নির্দয়ভাবে বড় রকমের ছাঁটাইয়ের প্রয়োজন দেখা দেয় । কুল গাছের সকল শাখা প্রশাখা কেটে দেয়া হয় । কাঁঠাল গাছের কিছু কিছু ছোট শাখা এবং ফলের বোঁটার নিম্নস্থ শাখা কাটা হয় । লিচু গাছের শাখা ছাঁটাই হয়ে যায় শাখাসহ ফল সংগ্রহের কারণে। আম, পেয়ারা, লিচু, কমলা, কামরাঙ্গা, বেল, শরীফা, আতা, আমড়া, জাম প্রভৃতির প্রয়োজন মত শাখা ছাঁটাই করা যেতে পারে ।
ফল গাছের অঙ্গ ছাঁটাই
বেশির ভাগ বৃক্ষ জাতীয় ফল গাছের চারা অবস্থায় কিছু কিছু অঙ্গ ছাঁটাই করা হলে চাহিদা মোতাবেক গাছের আকৃতি সুগঠিত ও সুন্দর করা যেতে পারে । কলমের চারার ক্ষেত্রে অঙ্গ ছাঁটাই বিশেষভাবে উপকারী । অনেক সময় বয়স্ক গাছের অঙ্গও ছাঁটাই করা প্রয়োজন পড়ে। যেমন— কুল, পেয়ারা, লিচু, কাঁঠাল গাছ-এর উপযুক্ত উদাহরণ । মুলত অঙ্গ ছাঁটাই বলতে গাছের অপ্রয়োজনীয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে গাছ বড় হলে সমস্যা হতে পারে কেটে বাদ দেয়াকে বোঝায়। অঙ্গ ছাঁটাই করা হলে গাছের ফলন বাড়ে এবং গাছটি সুন্দর দেখায় । ছাটায়ের সময় চারার/গাছের ছোট ছোট অংশ/ ডালপালা ছেটে ছোট করে দেয়া হয়। কোন গাছের একই সাইজের দুটো ডালের মধ্যে যদি একটি অপেক্ষা আরেকটি বেশি ছাঁটাই করা যায় তাহলে বেশি ছাঁটাই করা ডালটি কম বাড়বে । গাছের আকৃতি সুন্দর ও ফল বেশি হওয়ার জন্য অনেক সময় ডালপালা ছাঁটাই করে কমিয়ে দেয়া হয় । ছাঁটাই-এর সাথে ফল উৎপাদনের পরিমাণের সরাসরি সংযোগ আছে। অনেক ফলবতী গাছ বেশি ছাঁটাই করা হলে দীর্ঘদিন ধরে ফলন কম হবে । তাই গাছ বিশেষে সতর্কতার সাথে সঠিকভাবে ছাঁটাই করতে হবে । লতানো গাছে ফলন বৃদ্ধি ও সঠিক আকার দেয়ার জন্য ছাঁটাই অপরিহার্য। আঙ্গুরের মত লতানো ফল গাছকে ছোট মাচায় দিলে বেশি ফলন দেয় । এছাড়া অনেক সময় বড় গাছের মাথা হেঁটে ছোট করে রাখলে ফল পাড়তে, যত্ন নিতে ও অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যার সুবিধা হয়। কিছু কিছু চারা গাছ লাগানোর পর প্রধান কাণ্ড বা ডগা তাড়াতাড়ি বেড়ে লম্বা হয় এবং ডালপালা কম হয় বা আদৌ হয় না। এসব ক্ষেত্রে প্রধান কাণ্ড বা ডগা কেটে দিলে ডালপালা গজায়ে ঝাকড়া হয়, যা ফলন বৃদ্ধির জন্য সহায়ক। গাছের ভারসাম্য রক্ষার জন্য চারদিকে সম দূরত্বে তিন থেকে পাঁচটি ডাল রাখলে ভালো হয় । বড় গাছের ভেতরে ছোট ছোট এবং গাছের ভিতর বাতাস ও রোদ চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি করে । গাছের কাণ্ড মজবুত করা এবং ফলন বাড়ানোর জন্য চারা লাগানোর দুই/তিন বছরের মধ্যে প্রধান কাণ্ডের সাথে গাছের ডালের বিন্যাস ঠিক করে হেঁটে দিতে হয় ।
যেমন— রোগাক্রান্ত ও দুর্বল ডাল সব সময় হেঁটে দিতে হয়। কেননা রোগাক্রান্ত ডাল থেকে সব সময় রোগ ছাড়ানারে সম্ভাবনা থাকে ।
মূল ছাঁটাই (Root Pruning )
ফলের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দ্যেশে মূল ছাঁটাই একটি কার্যকর ব্যবস্থা । এর ফলাফল সচরাচর শাখা ছাঁটাইয়ের বিপরীতে হয়ে থাকে । গাছের গোড়া হতে কিছু দূরে অর্থাৎ গাছের আকার অনুযায়ী ৩ হতে ১০ ফুট দুরে নালা খনন করে সেখানকার সকল মূল কেটে দেয়া মুল ছাঁটাই-এর একটি পদ্ধতি । নালাটি গাছের চার পাশ দিয়ে সম্পূর্ণ চক্রাকারে, অর্ধচন্দ্রাকারে, এক চতুর্থাংশ চক্রাকারে প্রভৃতি বিভিন্ন পরিধি বা দৈর্ঘ্যের হতে পারে। গাছ হতে কিছু দূরে গর্ত করলে কিছুটা মূল ছাটাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয় । আবার সারা বাগান বা মাঠ জুড়ে লাঙ্গলের সাহায্যে জমি চাষ করলেও মুল ছাঁটাই হয়ে যায়। যেসব গাছের অঙ্গ অধিক বৃদ্ধি হওয়ার কারণে ভালোভাবে ফলবতী হয় না তাদের মূল ছাঁটাই ফলের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে । মূল ছাঁটাই করলে গাছে নাইট্রোজেন সরবরাহের পরিমাণ কমে যায়, ফলে গাছের মধ্যস্থিত নাইট্রোজেনও কার্বোহাইড্রেটের অনুপাত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে এবং ফুল ও ফল উৎপাদনে সহায়তা করে ।
পাতা ছাঁটাই (Pruning of leaves)
হাপর হতে চারা স্থানান্তরিত করে রোপণের সময় চারার অনেক মূল নষ্ট হয়ে যায়, তাতে গাছে পানি সরবরাহের পরিমাণ কমে যায় । অথচ গাছের উপরিভাগের পাতার মাধ্যমে আগের মত প্রবেদন ক্রিয়া চলতে থাকে । ফলে গাছে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানির অভাব দেখা দেয় এবং পানির অভাব অতিরিক্ত হলে গাছ মরে যায়। এ জন্য হাপর হতে চারা উঠিয়ে কিংবা উঠানোর ঠিক আগেই কিছু পাতা হেঁটে দিলে গাছ বাঁচানো সহজ হয় ।
ফুল ও ফল পাতলাকরণ (Thining of flower and fruit )
গাছে অতিরিক্ত সংখ্যক ফুল এলে তাদের কিছু কিছু ভেঙে দেয়া যেতে পারে। তাতে অপর ফুল সমূহের ফলে পরিণত হতে সুবিধা হয় । অতি ছোট গাছে ফুল আসলে ফুলকে ফলে পরিণত হতে না দিয়ে ভেঙে দিলে ফলের দরুণ গাছ দুর্বল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। গাছে অনেক সময় অতিরিক্ত ফুল ধরলে ফলের আকার ও গুণগত মান কমে যায়। এরূপ ক্ষেত্রে ফল ছিড়ে পাতলা করে দিলে অবশিষ্ট ফল আকারে বড় হয় এবং তাদের গুণাগুণ ঠিকমত প্রকাশ পায়। আবার ফল বেশি পাতলা করে দিলে গাছের খাদ্যসামগ্রী তথা কার্বোহাইড্রেট পরিমাণ ব্যয় না হওয়ার দরুণ পরের বৎসর ফল ধরার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেতে থাকে ।
প্রুনিং (Pruning) সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য
ছাঁটাই এমনভাবে করা উচিত যাতে কাটা অংশটি ভূমির সমান্তরাল না হয়ে যথাসম্ভব ভূমির সাথে খাড়াভাবে হয় । তা হলে এ স্থানে সূর্যের কিরণ দ্বারা ফেটে যাওয়ার এবং বৃষ্টির পানি জমে রোগ ও কীটের উপদ্রবের সম্ভাবনা কমবে । কুঁড়ির ঠিক উপরের দিকে কাটলে ভাল হয়। এতে করে কুঁড়ি হতে নতুন শাখা বের হওয়ার সুবিধা হবে । এমনভাবে কাটতে হবে যাতে কাটার নিম্নাংশ কুঁড়ির দিকে এসে ওটার বিপরীত দিকে থাকে । দেড় ইঞ্চি অপেক্ষা কম ব্যাস বিশিষ্ট শাখার কাটা স্থানে কোন প্রলেপ না দিলেও চলে। দেড় ইঞ্চির অধিক ব্যাস বিশিষ্ট শাখার জন্য সাধারণ পেইন্ট, বোর্দাপেষ্ট ইত্যাদির প্রলেপ দেয়া যেতে পারে ।
ফল গাছের পোকা ও রোগ বালাই দমন
বাংলাদেশের মাটি এবং উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু ফল উৎপাদনের উপযোগী । তেমনি ভাবে এখানকার জলবায়ু নানা প্রকার রোগবালাই ও পোকামাকড়ের উপদ্রবের অনুকূল । পোকা মাকড় ও রোগ বালাই ফসলের মারাত্মক শত্রু । তাদের আক্রমণে বাগানের সমপূর্ণ ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে । এ জন্য সঠিক সময়ে ফল ও ফল গাছকে ক্ষতিকর পোকামাকড়, রোগ বালাই ও নানাবিধ প্রতিকূল পরিবেশগত অবস্থা থেকে রক্ষার জন্য উপযুক্ত দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পোকা মাকড় ও রোগবালাই দমনের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়া হয় । তবে ঢালাওভাবে পোকা মাকড় ধ্বংস করা উচিত নয় । কেননা ফল বা ফল গাছের অনিষ্টকারী পোকামাকড়ের সাথে অনেক উপকারী পোকাও থাকে । এরা ফুলের পরাগায়নে সাহায্য করে এবং অনিষ্টকারী পোকামাকড়ের ডিম ও কীড়া খেয়ে অনেক উপকার করে থাকে । ফলে বা ফল গাছে পোকা মাকড় ও রোগ বালাই আক্রমণের পূর্বে সতর্কতামুলক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত । কেননা আক্রমণের পর দমন করা অপেক্ষা আগে প্রতিরোধ ব্যবস্থা করা উচিত।
এ জন্য সময়মত জমি চাষ, আগাছা দমন, পরিমাণ মত সার ব্যবহার, পানি সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ভালো জাত নির্বাচন করে সঠিক সময়ে সঠিক স্থানে রোপণ করে সুস্থ গাছ জন্মাতে হবে । গাছ দৈহিকভাবে দুর্বল হলে নানা প্রকার পোকামাকড় ও রোগ বালাই এর আক্রমণ বেশি হতে পারে । তাই মান সম্মত ফল উৎপাদনের জন্য সঠিক সময়ে পোকা মাকড় ও রোগবালাই দমনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে ফল বাগান সব সময় পরিষ্কার পরিছন্ন রাখা, ফল গাছ হতে পরজীবি উদ্ভিদ অপসারণ, মরা ডাল, পাতা ইত্যাদি অপসারণ এবং পোকা মাকড় ও রোগবালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন জাত ব্যবহার করতে হবে।
অতি সংক্ষিত প্রশ্ন
১ । ফল বাগানে অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা কখন করা যায় ।
২। আন্তঃকর্ষণের উপকারীতা কী ?
৩ । ফল বাগানে শূন্যস্থানে কী রকম চারা লাগানো উচিত ?
৪। প্রুনিং কখন করতে হয় ?
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
১ । অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যার সংজ্ঞা লেখ ।
২ । প্রনিং এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর ।
৩ । ফুল ও ফল গাছের পোকা ও রোগ বালাই দমন সম্পর্কে লেখ ।
৪ । ফল গাছে প্রনিং-এর সময় উল্লেখ কর ।
৫ । মূল ছাঁটাই-এর উপকারিতা বর্ণনা কর ।
রচনামূলক প্রশ্ন
১। ফল চাষে অন্তর্বর্তী পরিচর্যার ধাপগুলোর বর্ণনা কর ।
২ । প্রুনিং-এর পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা কর ।
৩ । ফল বাগানে আগাছা দমনের উপকারিতা বর্ণনা কর ।
৪ । ফল ও ফল গাছের পোকা মাকড় ও রোগ বালাই দমন সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা দাও ।
ফসল উৎপাদন ও আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনায় সেচ ও নিষ্কাশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভিদের বৃদ্ধি, পরিপূর্ণ বিকাশ ও পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় পানি কৃত্রিম উপায়ে মাটিতে সরবরাহ করাকে সেচ বলে । অপরদিকে মাটি থেকে কৃত্রিম উপায়ে অতিরিক্ত পানি ও লবণকে অপসারণ করাকেই নিষ্কাশন বলে । সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা মুলত দুটি পারস্পরিক এবং প্রাকৃতিক পদ্ধতির পরিপুরক । স্থায়ী ও নির্ভরযাগ্য শস্য উৎপাদনের লক্ষে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার অন্যতম পূর্ব শর্ত হচ্ছে সেচ ও নিষ্কাশন মানব সভ্যতার ঊষালগ্নে মানুষ যখন চাষাবাদ শুরু করে তখনই সেচ ও নিষ্কাশনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়ে আসছে।
ফল গাছে পানি সেচের গুরুত্ব
পানি মৃত্তিকাস্থ খাদ্যোপাদানসমূহকে দ্রবীভূত করে গাছের বিভিন্ন অংগে সঞ্চালন, অংগার (Carbon) আত্মকরণ, শস্যের সজীবতা, প্রয়োজনীয় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সরবরাহ প্রভৃতি কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । মাটিতে পর্যাপ্ত রসের অভাব হলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় । বাংলাদেশে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত অধিক হলেও এটি বার মাস সমভাবে বিস্তৃত নয়। ফলে আষাঢ় মাস হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত অতিবৃষ্টি আর কার্তিক হতে জ্যেষ্ঠ মাস পর্যন্ত অনাবৃষ্টির কারণে ফল গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় । উদ্ভিদের জন্য পানি একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান । যখনই পানির অভাব ঘটে তখনই উদ্ভিদে নানারূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং দীর্ঘ সময় পানির অভাব হলে গাছ মারা যেতে পারে । মাটিতে যখন গাছের জন্য প্রয়োজনীয় পানি (মাটির রস) সহজ লভ্য অবস্থায় থাকে না তখন কৃত্রিম উপায়ে গাছে পানি সরবরাহ করা হয় । গাছে কখন কিভাবে কতটুকু সেচ দিতে হবে তা বিভিন্ন অবস্থার ওপর নির্ভর করে । যেমন- আবহাওয়া, মাটির বুনট, গাছের প্রকৃতি, গাছের বৃদ্ধির পর্যায়, বাড়ন্ত ফুল ও ফল অবস্থায়, বয়স্ক গাছ ইত্যাদি ।
ফল গাছের জন্য পানি সেচ অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । ফল গাছ লাগানোর পর দ্রুত বৃদ্ধির জন্য শুকনো মৌসুমে নিয়মিত সেচ দিতে হয় । ফলধারী গাছে প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দেয়া উচিত । বৃষ্টির ওপর নির্ভর করে ফল গাছ রাপেণে অল্প ক্ষতি হলেও দীর্ঘ সময় অনাবৃষ্টিতে গাছের প্রচুর ক্ষতি হয় । অগভীর মূলবিশিষ্ট গাছের জন্য শুষ্ক মৌসুমে পানি দেয়া বা সেচ আবশ্যক । যেমন- নারিকেল, সুপারী, পেঁপে, আনারস, পেয়ারা, আতা, আর, কলা ইত্যাদি । অপরদিকে গভীর ও অগভীর মূল বিশিষ্ট কিছু সংখ্যক ফল গাছ আছে যেগুলো স্বল্পদিন অনাবৃষ্টিতে তেমন ক্ষতি হয় না । এমনকি জলাবদ্ধতায়ও তেমন কোন অসুবিধা হয় না । যেমন– আম, জাম, গাব, ডেওয়া, চালতা, তাল, খেজুর, লিচু ইত্যাদি ।
ফল গাছে পানি নিষ্কাশনের গুরত্ব
জমিতে যেমন পানি সেচ দেওয়া দরকার তেমনি প্রয়োজন অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা । গাছপালা সুন্দরভাবে জন্মানোর জন্য গাছের গোড়া বা শেকড় অঞ্চল হতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বের করে দেয়া হলো নিষ্কাশন । পানি জমে থাকলে জলাবদ্ধতা হয়। এতে গাছের প্রয়োজনীয় উপাদান প্রাপ্তিতে নানাবিধ সমস্যা হয় । এমনকি জলাবদ্ধতায় অনেক গাছ মারা যায় । তাই গাছ জন্মানোর জন্য নিকাশন অপরিহার্য ।
কোন কোন ফল গাছ যেমন কাঁঠাল, পেঁপে, আনারস, তরমুজ, কলা ইত্যাদি পানির প্রতি বেশি সংবেদনশীল অর্থাৎ এসব গাছের গোড়ায় পানি জমে থাকলে গাছের খুব ক্ষতি হয়। এমন কি গাছ মারা যেতে পারে । যেমন— কাঁঠাল গাছের গোড়ায় পানি জমে থাকলে গাছ মারা যায় । তাই কাঁঠাল বাগানে কোন গাছের গোড়ায় পানি জমে থাকলে তা জরুরি ভাবে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। সুন্দরভাবে পানি নিষ্কাশনের জন্য বাগানের চারদিকে নিষ্কাশন নালা থাকা আবশ্যক যেন সেচের অতিরিক্ত পানি বা অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে অতিরিক্ত পানি অনায়াসে বের হয়ে যেতে পারে। নিষ্কাশন নালা খাল বা জলাশয়ের সাথে সংযুক্ত করে দিতে হবে।
মাটিতে পানির অভাব হলে যেমন গাছ পালা বাড়তে পারে না। আবার জমি হতে অপ্রয়োজনীয় বা অতিরিক্ত পানি বের করে না দিলেও গাছপালা বাড়তে পারে না ।
ফল গাছে পানি সেচের সময় ও পানির পরিমাণ
জমিতে বা ফলের বাগানে কখন সেচ দিতে হবে এবং কী পরিমাণ সেচ দিতে হবে এ দুটি প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণ সেচের পানি প্রদানের লক্ষে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে-
- শস্যের পানির আবশ্যকতা (Crop water requirement )
- সেচ পানির প্রাপ্যতা (Water availability)
- শেকড় অঞ্চলে মৃত্তিকার পানি ধারন ক্ষমতা (Water holding capacity)
- সেচ ব্যবস্থাপনা ।
উলেখিত বিষয়গুলো বিবেচনার জন্য মৃত্তিকা, উদ্ভিদ, আবহাওয়া, সেচের পানির উৎস ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত উপাত্ত ও তথ্যাদির প্রয়োজন । মৃত্তিকার যে সব তথ্যাদি বিশেষ ভাবে জানা ও বিশেষণ আবশ্যক সেগুলো হচ্ছে মাটির বুনট, গভীরতা, সংযুক্তি, লবণাক্ততা বা ক্ষারত্ব, বায়বীয়তা, নিষ্কাশন, অনুপ্রবেশ, অনুস্রবণ, চুয়ানো, ভূগর্ভস্থ পানি তলের গভীরতা এবং পানি ধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি ।
উদ্ভিদ সম্পর্কিত জরুরি তথ্যাদি হচ্ছে ফসলের প্রকার, শেকড়ের বৈশিষ্ট্য, বর্ধনের সময় বিভিন্ন ধাপে পানির ব্যবহার, মৃত্তিকায় পানি স্বল্পতার কারণে উদ্ভিদের যে ধাপ সর্বাধিক ক্ষতিগত হয় ইত্যাদি ।
আবহাওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে চাষাবাদের ঐতিহ্যগত পদ্ধতি বীজ বপন অথবা চারা রোপণের তারিখ, গাছের ঘনত্ব, সারির দূরত্ব, সার ব্যবহার, আগাছা অথবা পাকামাকড় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ।
উদ্ভিদের ক্ষরা সহনীয়তা বলতে বোঝায় মৃত্তিকাস্থ শেকড় অঞ্চলে যে পরিমাণ সঞ্চিত পানি (%) গাছ ব্যবহার করলে গাছের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না । অধিকাংশ ফসলের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, গাছ মৃত্তিকায় সঞ্চিত পানির ৫০% ব্যবহার করার পরে যদি সেচ দেয়া হয় তাহলে ফসল উৎপাদনের মাত্রা কমে যায় না। এ ক্ষেত্রে সেচকে বলা হয় মৃত্তিকাস্থ প্রাপ্য পানির ৫০% কমতিতে সেচ প্রদান । কোন কোন ফসলের ক্ষেত্রে ৭৫% পানি কমতিতে ও ফসলের উৎপাদনের ক্ষতি হয় না। তবে ৫০% মাত্রাকেই সাধারণ সেচের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। তিনটি প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে সেচের সময় ও পরিমাণ নির্বাচন করা যায় যথা—
ক) মৃত্তিকা সম্পর্কিত
খ) উদ্ভিদ সম্পর্কিত
গ) আবহাওয়া সম্পর্কিত
ক) মৃত্তিকা সম্পর্কিত
এ পদ্ধতিতে প্রধানত মাটিতে পানির প্রাপ্যতা মাপা হয়। জমি থেকে মাটির নমুনা সংগ্রহের সময় মনে রাখতে হবে যেন এই নমুনা যে জমি থেকে মাটি নেয়া হবে মোটামুটিভাবে সেই জমির মাটির প্রতিনিধিত্ব মূলক হয় । এক্ষেত্রে অনুভব পদ্ধতি এবং অন্যান্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে মাটিতে পানির প্রাপ্যতা নির্ধারণ করা যায়।
১ । অনুভব পদ্ধতি (Feel Method)- এ পদ্ধতিতে মৃত্তিকার অবস্থা দেখে এবং স্পর্শ করে মৃত্তিকার পানির পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা করা হয়। মৃত্তিকার পানি ধারন বা রসের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য ফসল ভেদে ৩০-১০০ সে:মি: নিচ থেকে অথবা সংশিষ্ট ফসলের শেকড়ের গভীরতার ৬০-৭০% নিচ থেকে মাটি খুঁড়ে মাটির নমুনা সংগ্রহ করা হয় । সংগৃহীত নমুনা থেকে এক মুঠো মাটি হাতের মুঠিতে চেপে বল বানানো হয় এবং স্পর্শের অনুভূতি ও অবস্থা সারণি-১ প্রদত্ত অবস্থার সাথে তুলনা করে পানি সেচের উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করা যায় ।
সারণি-১ হাতের সাহায্যে মৃত্তিকার পানির পরিমাণ পদ্ধতি ও সেচের সময় নির্ধারণ
মুক্তিরসের পরিমাণ (পানিধারন ক্ষমতার অংশ % | সূক্ষ্ম বুনটের মৃত্তিকা (এটেল মৃত্তিকা, পলি এটেল প্রভৃতি) | মধ্যম থেকে মোটা বুনটের মৃত্তিকা | ||
মৃত্তিকা অবস্থা | করণীয় ব্যবস্থা | মৃত্তিকা অবস্থা | করণীয় ব্যবস্থা | |
| ০-২৫ | খুব শুষ্ক | অতি সত্ত্বর সেচের ব্যবস্থা করতে হবে | খুব শুষ্ক | অতি সত্ত্বর সেচের ব্যবস্থা করতে হবে |
| ২৬-৫০ | হাতের মুঠোয় চাপ দিলে দলা বেঁধে যায় এবং চাপ দেয়ার সাথে সাথে গুড়ো গড়ো হয়ে যায়। | অতি সত্ত্বর সেচের ব্যবস্থা করতে হবে | হাতের মুঠোয় চাপ দিলে দলা বাধে না | অতি সত্ত্বর সেচের ব্যবস্থা করতে হবে |
| ৫১-৭৫ | হাতের মুঠোয় চাপ দিলে শক্ত ও কিছুটা আঠালো দলা বাধে এবং ফেলে দিলে ভাঙ্গে না। | ২-৩ দিন পর সেচ দিলেও চলে | হাতের মুঠোয় চাপ দিলে দলা বাধে, ফেলে দিলে দলা ভেঙ্গে গুড়ো হয়ে যায়। | ১-২ দিন পর সেচের ব্যবস্থা করতে হবে |
| ৭৬-১০০ | হাতের মুঠোয় চাপ দিলে দলা বাধে এবং তালু ভিজে যায়, কিন্তু রস বের করে না ফেলে দিলে দলা ভাঙ্গে না। | ২-৩ দিন পর সেচ দিতে হবে | হাতের মুঠোয় চাপ দিলে দলা বাধে পানি বের হয়না ফেলে দিলে দলা ভাঙ্গে যায়। | ২-৩ দিন পর সেচের ব্যবস্থা করতে হবে |
| ১০০ | কাদা মাটি হাতের মুঠোয় চাপ দিলে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে মাটি বের হয়ে আসে। | সেচ দিতে হবে না । অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। | হাতের মুঠোয় চাপ দিলে ভেজা দলা বাধে। তালু ভিজে যায়, কিন্তু পানি বের হয়ে আসে না। | সেচ দিতে হবে না। ৭দিন পর পুনঃ মাটি পরীক্ষা করে ব্যবস্থা নিতে হবে । |
খ। উদ্ভিদ সম্পর্কিত পদ্ধতি
উদ্ভিদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেও সেচের প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায় । যখন মৃত্তিকাস্থ পানির পরিমাণ কমে যায় তখন গাছের পাতার রং বদলে যেতে পারে (যেমন— সবুজ থেকে হলুদ বর্ণ ধারণ), পাতা কুঁকড়িয়ে যেতে পারে । এ ছাড়াও গাছের বৃদ্ধির হার কমে যেতে পারে । কোন উদ্ভিদের এ জাতীয় উপসর্গ সেচের আবশ্যকতা নির্দেশ করে । তবে এই পদ্ধতির সমস্যা এই যে, এ সমস্ত উপসর্গ দেখা দেয়ার বেশ আগেই গাছ অতিরিক্ত পানি পীড়নের শিকার হয়, ফলে গাছের যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে যায় এবং ফলন কমে যায় ।
গ। আবহাওয়া সম্পর্কিত পদ্ধতি
এ পদ্ধতিতে আবহাওয়ার বিভিন্ন দিক যেমন- বৃষ্টিপাত, সোলার রেডিয়েশন, তাপমাত্রা, আপেক্ষিক আর্দ্রতা, বাষ্পীভবন ইত্যাদি মাপা হয়। সেই সাথে বিভিন্ন গাণিতিক সমীকরণ নির্ণয় করা হয়। বাষ্পীয় প্রস্বেদন, বৃষ্টিপাত, অনুপ্রবেশ, চুয়ানোসহ অন্যান্য অপচয় ইত্যাদির ভিত্তিতে সেচের আবশ্যকতা ও সময় নির্ধারণ করা যায়।
সেচের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলোর বর্ণনা
জমিতে সেচের পানি বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করা যায়। ফসলের পানির প্রয়োজনীয়তা, পানির উৎস ও প্রাপ্যতা, পানির গুণাগুণ, মাটির প্রকার, জমির অবস্থান, চাষাবাদের ধরন ইত্যাদির ভিত্তিতে সেচের পদ্ধতি নির্বাচন করা হয় । আধুনিক সেচ পদ্ধতিকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায় যথা-
১। ভূ - উপরিস্থ (Surface)
২। ভূ- মধ্যপ্ত ( Sub-surface)
৩। স্প্রিংকলার (Sprinkler)
৪ । ট্রিকল (Trickle)
১। ভূ - উপরিস্থ সেচ পদ্ধতি (Surface irrigation system)
এ পদ্ধতিতে পানি সরাসরি জমিতে দেয়া হয় ও সেচের পানি জমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় । এক্ষেত্রে জমিতে কয়েক সে:মি: পানি দিয়ে প্লাবিত করা হয় । পানির প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জমিকে প্রথমে মসৃন এবং পরে জমিতে বর্ডার (পাড় বা কিনার) ফারো (লাঙলের ফলার গভীর দাগ), করোগেশন (ঢেউ খেলানে আকৃতি) ইত্যাদি তৈরি করা হয় ।
ভূ-উপরিস্থ সেচ পদ্ধতিকে নিম্নলিখিত ৩ ভাগে ভাগ করা যায় ।
১। অনিয়ন্ত্রিত পাবন পদ্ধতি (Uncontrolled flooding)
২। নিয়ন্ত্রিত প্লাবন পদ্ধতি (controlled flooding)। এ পদ্ধতি আবার ৩ প্রকার । যেমন—
ক) বর্ডার স্ট্রিপ (Border Strip)
খ) চেক প্লাবন (Check flooding)
গ) বেসিন (Basin)
৩ । ফারো পদ্ধতি (Furrow Method)। এ পদ্ধতি আবার ২ প্রকার । যেমন-
ক) ফারো (Furrow)
খ) করোগেশন (Corrugation)
১। অনিয়ন্ত্রিত প্রাথম পদ্ধতি (Uncontrolled flooding)
যখন নালা থেকে পানি কোন রকম বাঁধ অথবা ডাইক অথবা অন্য কোন রকম প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই জমিতে দেয়া হয় তখন তাকে অনিয়ন্ত্রিত প্লাবন পদ্ধতি বলে। যেখানে অত্যন্ত সপ্তায় প্রচুর পরিমাণে সেচের পানি পাওয়া যায় সেখানে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
সুবিধা
- কম শ্রমিক যারা অল্প সময়ে বেশি জমি ভেজানো যায়
- এতে কোন বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না ।
- জমি সমতল বা একদিকে সামান্য ঢাল করে নিলেই হয়।
অসুবিধা
- সেচের পানির প্রায় ৮০ ভাগই অপচয় হয়
- ভূমিক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
- জমি সমতল করা প্রয়োজন হয় সেচের সময় তদারকির দরকার হয়
২। নিয়ন্ত্রিত প্লাবন পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে যুক্ত প্লাবনের পানিকে নিয়ন্ত্রণ বা বাধ দিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রবাহিত করা হয়।
ক) বর্ডার স্ট্রিপ পদ্ধতি (Border strip )
এ পদ্ধতিতে মাঠকে অনেক গুলো খণ্ড বা ভাগে বিভক্ত করা হয়। এই খণ্ডগুলো সাধারণত ১০-২০ মি: প্রশস্ত ও ১০০-৪০০ মিটার লম্বা হয়। একটি খণ্ড থেকে অন্য খও নিচু বাধ যারা বিচ্ছিন্ন করা হয় । সরবরাহ
নালা থেকে পানি এই খণ্ডসমূহে সরবরাহ করা হয়। পানি নিচের দিকে প্রবাহিত যে সমস্ত খণ্ডের জমিকেই ভিজিয়ে দেয় । প্রতিটি খন্ডে আলাদাভাবে সেচের পানি দেয়া হয়। সব ধরনের মৃত্তিকাতেই এই পদ্ধতিতে সেচ দেয়া যায়।
খ. চেক পাবন পদ্ধতি (Check Flooding) এ পদ্ধতিতে চারদিকে নিচু বাঁধ দ্বারা ঘেরা তুলনামূলক সমতল জমিতে বেশি পানি দেয়া হয় । অত্যন্ত পরিশোষক মৃত্তিকার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বেশি উপযোগী । এছাড়াও ভারি মৃত্তিকা যেখানে পানির হার কম সেখানেও এ পদ্ধতি কার্যকর । বতুত এই পদ্ধতি বর্ডার স্ট্রিপ পদ্ধতির একটি রূপান্তর ।
গ) বেসিন পদ্ধতি
নিচু বাঁধ দ্বারা পরিবেষ্টিত সমতল জমিতে দ্রুত পানি দেয়া হয় এবং জমি শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত পানি ধরে রাখা হয় । ধান চাষের জন্য এ পদ্ধতি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয় । এ ছাড়াও ফল বাগানে সেচ প্রদানের জন্য এ পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী । একটি বেসিনের আওতায় ১ থেকে ৫ অথবা বেশি পরিমাণ সেচ দেয়া হয় ।
সুবিধা
- পানির অপচয় বেশি হতে পারে না।
- যে বাগানে যতটুকু পানি প্রয়োজন সেভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় ।
- জমির অবস্থান বিবেচনা করে সমস্ত জমি সমতল করার প্রয়োজন হয় না ।
অসুবিধা
- জমিতে অনেক আইল করার কারণে জমির অপচয় হয় ।
- শ্রমিক খরচ বেশি ।
- আংশিক ভূমি ক্ষয়ের সম্ভাবনা থাকে ।
- বাঁধ যাতে ভেঙে না যায় সেজন্য সার্বক্ষণিক তদারকি এর জন্য শ্রমিক রাখা প্রয়োজন হয় ।
৩। ফারো পদ্ধতি
ফারো পদ্ধতি দু ধরনের যথা ফারো ও করোগেশন
ক) ফারো: ফারো পদ্ধতিতে শস্য/গাছের সারির মধ্যবর্তী ফারোতে (ছোট নালা) পানি সরবরাহ করা হয় । নালা গুলো সাধারণত প্রায় সমুন্নত ভূমি অথবা জমির ঢাল অনুযায়ী করা হয় । যে সমস্ত শস্য সারিবদ্ধ ভাবে চাষ করা হয় তাদের জন্য এ পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী ।
খ) করোগেশন। এটি কারো পদ্ধতিরই একটি রূপান্তরিত অবস্থা। এ পদ্ধতিতে পানি ছোট নালায় দেয়া হয়। এবং এই নালাগুলো সমস্ত মাঠ জুড়ে নির্মাণ করা হয়। পানি এই নালার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং চুইয়ে দুই নালার মধ্যবর্তি এলাকাতে সেচ প্রদান করে ।
সুবিধা
- ভারি মাটিতে পানির অপচয় কম হয়, যেহেতু সমস্ত জমিতে ভাসানো সেচ দিতে হয় না ।
- ভূমির ক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা নাই
অসুবিধা
- সতর্কতার সাথে নালা তৈরি করতে হয়
- হালকা মাটি হলে পানি চুয়ায়ে বেশি ক্ষতি হয়
- হালকা মাটিতে নালার পাড় ভেঙ্গে নালা বন্ধ হয়ে যায়
২। ভু - মধ্যস্থ সেচ পদ্ধতি - এই পদ্ধতিতে মাটির বুনট এবং ফসলের শেকড়ের গভীরতার ভিত্তিতে ভূ-পৃষ্ঠের নিচে পানি প্রবাহিত করা হয় । এ প্রক্রিয়ায় পানি শেকড় অঞ্চলে পৌঁছায়। গভীর নালা, মাটিতে প্রোষিত সিমেন্ট বা ধাতু নির্মিত ছিদ্র যুক্ত পাইপ, টাইল, ড্রেন ইত্যাদির মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের নিচে গাছের শেকড় অঞ্চলে পানি সরবরাহ করা হয়। অর্থাৎ এ পদ্ধতিতে ভূ-অভ্যন্তরে এমন একটি কৃত্রিম পানির তল তৈরি করা হয় যেখানে গাছ প্রয়োজনীয় পানি সংগ্রহ করতে পারে ।
সুবিধা
- পানির অপচয় হয় না
- মাটি শক্ত হওয়ার সুযোগ থাকে না
- ভূমি ক্ষয় হয় না।
- ভূমি নষ্ট হয় না
অসুবিধা
- নল বা পাইপ বসানোর জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন,
- নল বা পাইপ বসানোর জন্য শ্রমিক বেশি লাগে, খরচ বেশি,
- গাছের শেকড় বা মাটি দ্বারা পাইপের ছিদ্রগুলো বন্ধ হয়ে যেতে পারে ।
৩। স্প্রিংকলার বা ছিটানো পদ্ধতি/সিঞ্চন পদ্ধতি
এই পদ্ধতিতে পানি পাইপ ও স্পিংকলার নজল-এর মাধ্যমে বাতাসে ছড়িয়ে দেয়া হয় এবং তা বৃষ্টির মতই মাটিতে পড়ে। এ পদ্ধতি প্রায় সব রকম ফসল ও মৃত্তিকার জন্যই উপযোগী।
সুবিধা
- পাহাড়ি বা অসমতল জমিতে এ পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি উপযোগী
- পানির অপচয় কম হয় এবং সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়
- সার ও কীটনাশক এ পানিতে মিশিয়ে দেয়া যায়
অসুবিধা
- পাইপ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির খরচ বেশি
- সেচের জন্য দক্ষ লোকের প্রয়োজন:
- জোরে বাতাস বয়ে যাওয়ার সময় সেচ দেয়া যায় না।
৪। ট্রিকল বা ড্রিপ পদ্ধতি
এটি ড্রিপ পদ্ধতি হিসেবেও পরিচিত। এ পদ্ধতিতে ছোট ব্যাসযুক্ত পাইপের একটি বিস্তারিত নেটওয়ার্ক থাকে। যার দ্বারা পানি সরাসরি গাছের গোড়ায় ফোটায় ফোটায় দেয়া হয়। এই পদ্ধতি ফল বাগান ও গ্রীন হাউসের জন্য বিশেষ উপযোগী।
সুবিধা
- তুলনামূলক ভাবে পানি কম লাগে।
- প্রতিটি গাছের গোড়ায় সঠিক ও সম পরিমাণ সেচ দেয়া যায়।
- বেলে মাটি ও অসমতল পাহাড়ি জমিতে সেচ দিতে বিশেষ উপযোগী।
- শ্রমিক খরচ ও আগাছার প্রকোপ কম হয়।
অসুবিধা
- সব এলাকায় সেচ দেয়া সুবিধাজনক নয়।
- স্থাপন বেশ ঝামেলাপূর্ণ ও ব্যয়বহুল
- পানির নল ও পানি নিঃসরক প্রায়ই বন্ধ হতে পারে
- খুবই পরিষ্কার পানির দরকার
- পানির প্রবাহ অবিরাম পর্যবেক্ষণ করতে হয়
নিষ্কাশনের বিভিন্ন পদ্ধতি: নিষ্কাশন নালা বা নর্দমার মাধ্যমে ফসলের শেকড় অঞ্চল থেকে অপ্রয়াজনীয় বা অতিরিক্ত পানি বের করে দেয়াকে নিষ্কাশন বলে । নিষ্কাশন নালা প্রধানত দুধরনের হয় প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম । কার্য পদ্ধতি অনুসারে নিস্কাশন নালা তিন প্রকার । যথা -
(১) ভূ -- পৃষ্ঠস্থ নিষ্কাশন ব্যবস্থা (Surface)
(২) ভূ নিম্নস্থ নিষ্কাশন নালা ( Sub - Surface or tile)
(৩) সম্মিলিত ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূ-নিম্নস্থ নিষ্কাশন নালা (Combinaton of surface and sub- surface drains)
(১) ভূ-পৃষ্ঠস্থ নিষ্কাশন নালা
যে সমতল জমিতে উপরিস্তরের গভীরতা কম এবং ভূ-পৃষ্ঠের অল্প নিচেই অপ্রবেশ্য স্তর যেমন- লাঙল তল, শক্ততল বা এটেল মাটির স্তর রয়েছে সে সব জমির জন্য ভূ-পৃষ্ঠসহ নিষ্কাশন নালা উপযোগী ।
ভূ-পৃষ্ঠস্থ নিষ্কাশন নালা তিন রকমের । যেমন-
ক) স্টর্ম নিষ্কাশন ব্যবস্থা বা গভীর নালা ব্যবস্থা
খ) চুয়ানো নিষ্কাশন ব্যবস্থা
গ) সম্মিলিত স্টর্ম ও চুয়ানো নিষ্কাশন ব্যবস্থা
ক) স্টর্ম বা গভীর নিষ্কাশন নালা- এ নালা সাধারণত অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি নির্দিষ্ট সময়ে বের করে দেয়ার জন্য গভীর করে তৈরি করা হয় ।
(খ) চুয়ানো নিষ্কাশন নালা ( Seepage drain): সেচ নালার বা খালের পানি পাশের জমির চেয়ে উঁচু দিয়ে প্রবাহিত হলে পাড় চুঁইয়ে জমিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে । চুয়ানো পানি নিষ্কাশনের জন্য সেচ খালের পাড়ের পাশেই চুয়ানো খাল খনন করা হয় । খাল গভীর করে খনন করতে হয় । চুয়ানো পানি জমা হলে এখান দিয়ে নিকাশিত হয় ।
(গ) সম্মিলিত স্টর্ম ও দুয়ানো নিষ্কাশন নালা- এ নালা প্রথমে চওড়া ও অগভীর করে তৈরি করে মাঝখান দিয়ে কম চওড়া করে অগভীর নালা করা হয় । এতে বৃষ্টির পানি এবং চুইয়ে আসা পানি উভয়ই বের হতে পারে ।
ভূ- পৃষ্ঠস্থ নিষ্কাশন নালা ব্যবস্থার প্রকার
পাঁচ ধরনের ভূ-পৃষ্ঠস্থ নিষ্কাশন নালা ব্যবস্থা আছে। ফসল ক্ষেত্রের অবস্থা বিবেচনা করে এ পাঁচ প্রকার ব্যবস্থা থেকে দুটি বা ততোধিক ব্যবস্থা সম্মিলিতভাবে ব্যবহার করতে হতে পারে। ব্যবস্থাগুলো নিম্নরূপ-
ক) এলাপোথাড়ি নালা ব্যবস্থা (Random drain)
খ) প্রবাহ পথে অটককরণ নালা ব্যবস্থা (Interception)
গ) ভিন্নদিকে প্রবাহিতকরণ নালা ব্যবস্থা (Diversion)
ঘ) উপরিভাগ নালা ব্যবস্থা (Bedding)
ও) মাঠ নালা ব্যবস্থা (Field drain)
২। ভূ-মধ্যস্থ বা ভূ-নিম্নস্থ নিষ্কাশন ব্যবস্থা/টাইল (Sub Surface or tile): এ পদ্ধতিতে মাটির অভ্যন্তর থেকে পানি টাইল অথবা মোন (Tilte or mole) নালার মাধ্যমে নিষ্কাশন করে ভু-গর্ভস্থ পানির তল গাছের শেকড় অঞ্চলের নিচে নামানো হয়। এই নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে টাইল নিষ্কাশন ব্যবস্থাও বলে। এই নিষ্কাশন ব্যবস্থার ভূ-পৃষ্ঠের নিচে নিষ্কাশন নালা স্থাপন বা তৈরি করা হয়। ভূগর্ভস্থ পানি তলের অবস্থান গাছের শেকড় থেকে পতীরে নামিয়ে শেকড়ের পর্যাপ্ত বৃদ্ধি ও শেকড় অঞ্চলে প্রয়োজনীয় বায়ু চলাচলের সুবিধার জন্য এ নিষ্কাশন ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকরি। বাংলাদেশে উঁচু জমিতে আবাদকৃত ফসলের জন্য এই ধরনের নিষ্কাশন নালা ব্যবহার করা যেতে পারে।
বিভিন্ন উপযোগিতা বিবেচনায় টাইল নালা পদ্ধতিতে কয়েক ধরনের বিন্যস্ততা দেখা যায়। সাধারণ টাইল নিষ্কাশন পদ্ধতিসমূহ হলো-
১ । ইন্টারসেপশন (Interception)
২। র্যানডম (Random)
৩ । ডাবল মেইন (Double main )
৪ । পারালাল (Parallel )
৫ । গ্রিড আয়রন (Gridiron )
৬। হেরিং বোন (Herring bone)
(৩) সম্মিলিত ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূ-নিম্নস্থ বা ভূ-মধ্যস্থ নিষ্কাশন ব্যবস্থা
এই পদ্ধতিতে উপরে বর্ণিত উভয় প্রকার নিষ্কাশন পদ্ধতি একত্রে ব্যবহার করা হয় । এ ব্যবস্থায় ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি নিষ্কাশনের নালার তল মাটির নিচে নিষ্কাশন নালা তৈরি করা যায় । এ নালার চতুর্দিকে ফিল্টার দ্রব্য ব্যবহার করা হয় ।
অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
১। স্থায়ী ও নির্ভরযোগ্য শস্য উৎপাদনের লক্ষে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার অন্যতম পূর্বশত হলো কী ?
২ । কোন কোন ফল গাছ সেচের প্রতি বেশি সংবেদনশীল ।
৩ । অনুভব পদ্ধতি কী ?
৪ । আধুনিক সেচ পদ্ধতিতে কত ভাগে ভাগ করা যায় ?
৫। একটি বেসিনের আওতায় কতটি গাছকে সেচ দেয়া যায় ?
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
১। পানি সেচ বলতে কী বোঝায় ।
২ । সেচের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ ।
৩ । নিষ্কাশনের গুরুত্ব বর্ণনা কর ।
৪ । নিষ্কাশনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর ।
৫ । ফল বাগানে সেচের গুরুত্ব বর্ণনা কর ।
রচনামূলক প্রশ্ন
১ । সেচের প্রধান পদ্ধতিগুলোর নাম উল্লেখ সহ যে কোন একটি পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা লেখ ।
২। পানি নিষ্কাশনের উদ্দেশ্য এবং সুবিধা অসুবিধা লেখ ।
৩ । বাগানে সেচের প্রয়াজনীয়তা নির্ধারণের বিষয়গুলো বর্ণনা কর ।
৪ । ফল বাগানে পানি সেচের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর ।
৫ । নিষ্কাশনের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলোর বিবরণ দাও ।
বাংলাদেশের মাটি এবং উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু ফল উৎপাদনের উপযোগী । তেমনিভাবে নানা প্রকার রাগবালাই ও পোকামাকড়ের উপদ্রব্যের জন্যও অনুকূল । পোকামাকড় দমনের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়া হয় । তবে ঢালাও ভাবে পোকামাকড় ধ্বংস করা উচিত নয় । কেননা, ফল বা ফল গাছের অনষ্টিকারী পোকামাকড়ের সাথে অনেক উপকারী পোকাও থাকে । এরা ফুলের পরাগায়ণে সাহায্য করে এবং অনিষ্টকারী পোকামাকড়ের ডিম ও কীড়া খেয়ে অনেক উপকার করে থাকে ।
ফল বা ফলগাছে পোকামাকড় ও বালাই আক্রমণের পূর্বে সতর্কতামূলক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত । কেননা আক্রমণের পর দমন করা অপেক্ষা আগে প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেয়া অনেক ভাল । এ জন্য সময়মত জমিচাষ, আগাছা দমন, সুষম সার ব্যবহার, পানিসেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা করতে হয় । এছাড়া ভাল জাত নির্বাচন করে সঠিক সময় ও সঠিক স্থানে রোপণ করে সুস্থ গাছ জন্মাতে হবে । গাছ দৈহিকভাবে দুর্বল হলে নানা প্রকার পোকামাকড় ও বালাইয়ের আক্রমণ বেশি হতে পারে । পোকামাকড়ের আক্রমণের লক্ষণ ও কীটের উপস্থিতি বিভিন্নভাবে বোঝা যায় । যেমন- ফল ছিদ্রকরা, পাতা ফ্যাকাশে বা হলদে হয়ে যাওয়া, ফল বা পাতা খাওয়া, পাতা চিবানো, পাতা মাড়ানো, কাণ্ড বা শেকড় নষ্ট করা, গাছে সুড়ঙ্গ সৃষ্টিকারী পোকার মলের চিহ্ন দেখে বুঝতে পারা যায় ।
ফল ও ফল গাছের আক্রমণকারী প্রধান প্রধান পোকা
বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ফলে ও ফল গাছে নানা ধরনের পোকা মাকড় আক্রমণ করে থাকে । নিম্নের সারণিতে ফল ও ফল গাছে আক্রমন কারী প্রধান প্রধান পোকামাকড়ের তালিকা দেয়া হলো ।
ফল ও ফল গাছের আক্রমণের ধরন দেখে পোকা শনাক্ত
ফল ও ফল গাছের অনিষ্টকারী পাকামাকড় দমন করতে হলে এর স্বভাব, প্রকৃতি, বিস্তৃতি, জীবন বৃত্তান্ত, আবির্ভাবের সময় ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । নিম্নের বর্নিত ফলের প্রধান প্রধান পোকার আবির্ভাবের সময় ও ক্ষতির লক্ষণ দেখে শনাক্তকারী পোকার বাংলা ও ইংরেজি নাম দেয়া হলো ।
ক্র নং | অবির্ভাব্বে সময় | আক্রমণের ধরন/বতির লক্ষণ | শনাক্তকারী পোকার বাংলা ও ইরেজি নাম |
| ১ | জানুয়ারি - এপ্রিল ও জুন-জুলাই | বাচ্চা ও পূর্ণবয়ক অবস্থায় কচি পাতা ও ফুলের রস চুষে খায়। গাছ দুর্বল হয়, যথেষ্ট ফুল হওয়া সত্ত্বেও গুটি হওয়ার আগেই ফুল ঝরে পড়ে । | আমের হপার পোকা Mango hopper |
| ২ | এপ্রিল-মে | স্ত্রী পোকে কাঁচা আমের গায়ে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়ে ফলের শাঁসের মধ্যে আঁকা বাঁকা সুড়ঙ্গ তৈরি করে খেতে থাকে। প্রাপ্ত বয়স্ক উইভিলে পরিণত হয়ে আমের খোসা ছিদ্র করে বাইরে বের হয়ে যায় । | আম ফলের ভোমরা পোকা Mango fruit weevil |
| ৩ | মার্চ নভেম্বর | স্ত্রী পোকা আম গাছের কাণ্ড ও শাখায় গর্ত করে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে কীড়া বের হয়ে কাণ্ড বা শীখার মধ্যে সুড়ঙ্গ করে ঢোকে । আক্রান্ত শাখা সহজেই ভেঙ্গে যায়। চারা গাছের কাণ্ড আক্রান্ত হলে গাছ মারা যেতে পারে । | আম গাছের কাণ্ডের মাজর পোকা Mango stem borer |
| ৪ | মার্চ - নভেম্বর | বিছা পোকার কীড়া আম গাছের পাতা খেয়ে গাছকে পশুন্য করে দেয়। ফলে গাছে ফুল ও ফল আসে না। | আম পাতার বিছা পোকা Mango leaf gall midges |
| ৫ | এপ্রিল মে | কীড়া আমের ভেতর ঢুকে শাঁস খাওয়ার ফলে আম পঁচে যায়। আক্রান্ত ফল কাটলে তার মধ্যে অসংখ্য কীড়া কিলবিল করতে দেখা যায় | আমের মাছি পোকা Mango fruit fly |
| ৬ | মে - অক্টোবর | কাঁঠাল ছিদ্র করে ভেতর ঢুকে পচিয়ে ফেলে। | কাঁঠালের ফল ছিদ্রকারী পোকা Stone weevil |
| ৭ | এপ্রিল- আগষ্ট | পূর্ণ বয়স্ক বিটল কঁচি কলা পাতা ও কচি কলার খোসা খায়। ফলে কলার পাতা ও ফলের ওপর ছোট ছোট দাগের সৃষ্টি হয় । | কলার পাতা ও ফলের বিটল পোকা Banana leaf and fruit beetle |
| ৮ | জুলাই - অক্টোবর | পুর্ন বয়স্ক উইভিল কলা গাছের গোড়ায় শিকড়ের ওপর ডিম পাড়ে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়ে কাণ্ডের ভেতর ঢুকে যায়। ফলে আক্রান্ত অংশ পচে যায়, ডগার পাতা শুকিয়ে গাছ মরে যায়। | কলা গাছের কাণ্ডের শুড় পোকা Banana Stem weevil |
| ৯ | ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল | কীড়া ফসলের বোটার দিকে ছিদ্র করে ঢুকে শাঁস ও বীজ খায়। | লিচু ছিদ্রকারী পোকা Litchi fruit borer |
| ১০ | মার্চ - জুন এবং আগস্ট-অক্টোবর | ক্ষুদ্র মাকড় পাতার নিচে ছিদ্র করে রস শোষণ করে। ফলে আক্রান্ত পাতা কুঁকড়ে যায় ও শুকিয়ে ঝরে পড়ে । | লিচু পাতার ক্ষুদ্র মাকড় Litchi mite |
| ১১ | মে - অক্টোবর | পাতা থেকে রস চুষে খায় । | পেয়ারা সাদা মাছি whitefly |
| ১২ | মে - অক্টোবর | ফল ছিদ্র করে শাঁস খায়। | ফলের মাছি Fruit fly |
| ১৩ | জুন- সেপ্টেম্বর | ডগা, ফল, কুড়ি থেকে রস চুষে খায়, ফন্দ্রে আকার ছোট হয় । | ছাতরা পোকা Mealy bug |
| ১৪ | সারা বছর | নারিকেল গাছের মাথায় না বের হওয়া পাতা কেটে ক্ষতি করে । | নারিকেল গাছের গন্ডার বা গোবরে পোকা Rhinoceros beelle |
পোকা দমনের পদ্ধতি
ফসল জন্মানোর কালে প্রায়শ এগুলোকে কীট কিংবা রোগ দ্বারা আক্রান্ত হতে দেখা যায় । কীট কিংবা রোগ দমন করতে না পারলে ফসল বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় । ফসলের পোকামাকড় দমনে গৃহীত ব্যবস্থাগুলো কোন সময় অর্থাৎ ফসলের বৃদ্ধি ও পোকার আক্রমণের কোন স্তরে প্রয়োগ করা হবে তার উপর নির্ভর করে দমন পদ্ধতিকে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে । যথা- (ক) প্রাফোইল্যাক্সিস- পোকামাকড় যাতে গাছ বা ফলে আক্রমণ করতে না পারে সে জন্য পূর্বেই যে ব্যবস্থা নেয়া হয় তাকে প্রতিরোধক বা প্রিভেনটিভ ব্যবস্থা বলে । (খ) থেরাপি- আক্রান্ত গাছে পোকামাকড়ের আক্রমণ বৃদ্ধি ঠেকানারে জন্য বা দমনের জন্য যে ব্যবস্থা নেয়া হয় তাকে প্রতিষেধক বা কিউরেটিভ ব্যবস্থা বলে ।
গাছ সুস্থ ও সঠিকভাবে বেড়ে উঠার জন্য চারার যথাযথ যত্ন, জমি কর্ষণ, ও সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে । এর ফলে গাছের পোকামাকড় আক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মাবে । গাছ কখনো কখনো শারীরিকভাবে দুর্বল হতে পারে । এ সময় কোন কোন পোকামাকড় গাছে বা ফলে আক্রমণ করতে পারে । তাই গাছের অবস্থা দেখে পানি বা খাদ্য উপাদানের ঘাটতি থাকলে তা পূরণ করে গাছকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে । তাতে গাছে পোকামাকড় আক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মাবে এবং গাছ শক্তিশালী হবে ।
গাছে পোকামাকড়ের আক্রমণ ঠেকাতে দুটি দমন ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিরোধক বা প্রিভেনটিভ ব্যবস্থাকে প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণও বলা যেতে পারে । এ পদ্ধতিতে গাছে পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রাকৃতিক উপায়ে নিয়ন্ত্রিত হয় । এ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় । যেমন- ক) আবহাওয়াগত অবস্থার পরিবর্তন খ) জমির উঁচু নিচু অবস্থানগত অবস্থা গ) পরিবেশগতভাবে এক ধরনের পোকা দ্বারা অন্য ধরনের পোকা ধ্বংস হওয়া এবং ঘ) আশ্রয়দাতার নিকট হতে আক্রমণকারী পোকাকে বিচ্ছিন্ন করা ।
অপর দমন ব্যবস্থা যথা- প্রতিষেধক বা কিউরেটিভ ব্যবস্থাকে প্রয়োগিক নিয়ন্ত্রণ বলা যেতে পারে । এ পদ্ধতিতে গাছে পোকামাকড়ের আক্রমণ কৃত্রিম উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয় । এ পদ্ধতিকেও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় । যেমন —
১। যান্ত্রিক দমন (Mechanical control)
২। জৈবিক দমন (Biological Control)
৩ । পরিচর্যামূলক দমন (Cultural Control)
৪ । পোকামাকড় প্রতিরোধী জাত (Use of resistant variety)
৫ । রাসায়নিক দমন (Chemical Control)
৬ । আইনগত দমন (Legal Control)
৭ । ভৌত দমন
যান্ত্রিক উপায়ে পোকা দমন পদ্ধতি ও উপকারিতা
পোকামাকড় দমনে প্রতিষেধক পদ্ধতির অন্তর্গত যান্ত্রিক পদ্ধতি সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো ।
১। যান্ত্রিক দমন পদ্ধতি
এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে পোকামাকড় দমন করা যায়। যেমন- আলোর ফাদ, প্রতিরক্ষামূলক বাধা, জালি, ভৌতশক্তি, উত্তাপ অথবা শৈত্যের ব্যবহার, বিদ্যুৎ, পানি ইত্যাদি । যান্ত্রিক উপায়ে কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ হলো বিশেষ ধরনের কোন যন্ত্র, মানুষের শ্রম ও কোন বিশেষ দ্রব্যের সাহায্যে কীটপতঙ্গ দমনের একটি কৌশল। কৌশলগতভাবে কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ অর্থনৈতিক ভাবে সাধারণত লাভজনক হয়ে থাকে । কিন্তু এ পদ্ধতি ব্যবহার করে অধিক সংখ্যক কীটপতঙ্গ দমন করা সম্ভব হয় না, তবে এ পদ্ধতি পরিবেশ বান্ধব । যান্ত্রিক উপায়ে কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলো নিচে আলোচনা করা হলো ।
(i) হাত দ্বারা আহরণ
যে সব পোকা ডিম গাদা করে পাড়ে এবং ডিম ফুটার পর শুককীট/কীড়া একত্রে গাদা করে অবস্থান করে সে সব পোকা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এ পদ্ধতি উত্তম। এ সব পোকার ডিম হাত দিয়ে সংগ্রহ করে মারা যায় । যেমন বেগুন, শিম, কাঁকরালে ও করলা গাছের পাতা হতে এপিল্যাকনা বিটলের ডিমের গাদা এবং বিটল হাত দ্বারা সংগ্রহ করে সহজেই মেরে ফেলা যায় । অথবা আক্রান্ত ডিমের গাদাসহ ডাল বা পাতা কাঁচি দিয়ে কেটে সংগ্রহ করে পিষে বা মাটিতে পুঁতে ধ্বংস করা যায় ।
(ii) পোকা ধরার জাল ব্যবহার
আক্রান্ত ক্ষেতে পোকা ধরার জাল দ্বারা সুইপ করে ঝাড়া দিয়ে অনেক পোকা আটকানো যায় । পরে এ গুলোকে মাটিতে পুঁতে মেরে ফেলা যায়। যেমন- ধানের পামরী পোকা এ পদ্ধতির মাধ্যমে সহজেই দমন করা যায় ।
(iii) পিটিয়ে এবং খুঁচিয়ে
যে সকল পোকা খাদ্য দ্রব্য পেলে সেখানে দলে দলে ভিড় জমায় সে সকল পোকা মাকড় ঝাড়ু বা অন্যকোন বস্তু দ্বারা পিটিয়ে দমন করা যায়। যেমন- তেলাপোকা, পিঁপড়া ইত্যাদি। আবার কিছু পাকা আছে যারা পোষকের দেহে গর্ত করে বা ফাটলে লুকিয়ে থেকে ক্ষতি করে। এদেরকে লাহোর শিক দ্বারা খুঁচিয়ে মেরে ফেলা যায় যেমন নারিকেলের বিটল পোকা ।
(vi) ঝাঁকিয়ে (Shaking)
ছোট ছোট গাছে পোকা আক্রমণ করলে সেগুলো অনেক সময় কঁকিয়ে মাটিতে ফেলে মেরে ফেলা হয় । যেমন আমড়া, লিচু, কলা ইত্যাদি গাছের বিটল । গাছ কুপিয়ে মাটিতে ফেলে এ সমস্ত পোকা মেরে ফেলা যায় ।
(v) প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে
কীট পতঙ্গ যাতে কাঙ্খিত ফসলের সংস্পর্শে আসতে না পারে সে জন্য প্রতিকন্ধকতা বা বাধার সৃষ্টি করে ফসলকে রক্ষা করা যায়। যেমন পাটের বিছা পোকায় আক্রান্ত ক্ষেতের চার পাশে নালা করে সেখানে কীটনাশক মিশ্রিত পানি দিলে পোকা পার্শ্ববর্তী ক্ষেতে যেতে পারে না।
অনুরূপভাবে ডালিম, কুমড়া বা কলা কচি অবস্থায় কাপড়, চট বা । নিচের দিকে মুখ ভালো পলিথিন ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিলে এ ফসলগুলোর ফল যেমন- ডালিমের প্রজাপতি, ফলের মাছি পোকা এবং কলার বিটলের আক্রমণ হতে রক্ষা করা যায় ।
(vi) চালুন দ্বারা চেলে ও কুলা দ্বারা ঝেড়ে চেলে
গোলাজাত শস্যের কতগুলো পোকা এ পদ্ধতির মাধ্যমে দমন করা যায় । যেমন- ময়দার কেড়ী পোকা, চালনি দ্বারা চেলে এবং চালের কেড়ী পোকা কুলা দ্বারা ঝেড়ে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যায় ।
(vii) যান্ত্রিক ফাঁদ
ফাদের সাহায্যে শস্যের কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ একটি উত্তম পন্থা। কীট পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের জন্য বেশ কিছু যাত্রিক ফাদ আবিষকৃত হয়েছে যেমন- আলোর ফাঁদ, আঠা লাগানো ফঁদ ইত্যাদি । উজ্জ্বল আলোর নিচে বড় গামলা বা পাত্রে কীটনাশক মিশ্রিত বা সাবান মিশ্রিত পানি রেখে দিলে পোকা আলোতে আকৃষ্ট হয়ে উড়ে এসে পানিতে পড়ে মারা যায়, যেমন- ধানের মাজরা পোকার মথ, চুংগী পোকা, সবুজ পাতা ফড়িং ইত্যাদি। ছোট ছোট পোকা, যেমন ফলের মাছি পোকা, আঠা লাগানো ফাঁদের সাহায্যে আকৃষ্ট করে মারা যায় ।
যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পোকা দমনের উপকারীতা
১। দৈহিক উপায়ে পোকা দমনের ফলে অর্থাৎ কীটনাশকের পরিবর্তে হাত দিয়ে পোকা ধরে অথবা পাতার ডিমের গুচ্ছ হাত দিয়ে তুলে ধ্বংস করে, পোকামাকড়ের আশয়স্থল নষ্ট করে, আলোর ফাঁদ পেতে এবং পোকা খেকো পাখিকে জমিতে বসতে দেয়ার ব্যবস্থা করে পোকা দমন করলে পরিবেশ দূষণ রোধ হয় ।
২। কীট ও বালাই নাশকের মত ব্যবহার পরবর্তী পার্শ্বক্রিয়া না থাকায় পরিবেশ ও জীব বৈচিত্রের কোন ক্ষতি হয় না ।
৩। উপকারী পোকা মাকড় ও কীট পতঙ্গের সুরক্ষা হয় এবং জীব বৈচিত্র্য অক্ষুন্ন থাকে ।
৪ । কীট ও বালাই নাশকের ব্যবহার কমিয়ে আর্থিক সাশ্রয় করা যায় ।
৫। উপকারী পোকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় যেমন- মৌমাছি, মাকড়সা
পোকা দমনে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার উপকারীতা
বাংলাদেশে নিয়ন্ত্রণহীন জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত মানের প্রচুর খাদ্য উৎপাদন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে । ফলে ব্যাপক রাসায়নিক দ্রব্য যেমন- সার ও বালাইনাশকের ব্যবহার অনেক বেড়ে গেছে। এগুলো প্রয়োগের ফলে পোকা মাকড়ের জীবনচক্র এবং বংশবৃদ্ধিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে । শুধু তাই নয় লাগামহীন বালাই নাশক প্রয়োগের দরুন সকল প্রজাতির পোকা মাকড়সহ মানব দেহে দেখা দেয় বিভিন্ন রকম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া । যারা এ সকল বালাই নাশক ক্ষেতে ও ফসলে ছড়াচ্ছে তারাতো এর শিকার হচ্ছেই তাছাড়া সাধারণ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী দৈনন্দিন যে খাদ্য খাচ্ছে তার মধ্যে বালাই নাশকের অবশিষ্টাংশ হিসেবে তাদের দেহে এসব বিষ যাচেছ । এ বিপর্যয় শুধু আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার নামে কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদির যথেচ্ছ অপব্যবহারের ফলে ঘটে চলেছে । যদিও ফসলে বালাই বলতে ফসলের অনিষ্টকারী সকল প্রকার পোকা মাকড়, রোগ জীবানু আগাছা ও মেরুদন্ডী প্রাণী যা মানুষের স্বার্থে আঘাত হানে তাকে বোঝায়। বালাই দমনের জন্য বালাইনাশকের ওপর নির্ভর করার ফলে বহুবিধ সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে, যেমন- আগের তুলনায় পরবর্তী ফসলে পোকার আক্রমণ বৃদ্ধি, মানুষ ও পশু পাখির বিষক্রিয়াজনিত বিপদ, ফসলের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি, পোকার প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও পরিবেশ দূমি করণ । এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা একান্তভাবে দরকার ।
সাফলাজনকভাবে পোকা মাকড় দমন করতে হলে শুধু মাত্র বালাইনাশকের ওপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না । বালাইনাশক প্রয়োগ ছাড়াও পোকা মাকড় দমনের অন্যান্য পদ্ধতিগুলো জানা এবং প্রয়োগ করা দরকার । সাধারনভাবে বলতে গেলে অল্প খরচে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের কোন ক্ষতি না করে যখন যে ব্যবস্থাটি প্রয়োজন তা প্রয়োগ করে ফসলের শুভ্র পোকামাকড়ের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করাকে পোকা মাকড় দমনের সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) বলা হয়। অন্যভাবে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা হচ্ছে, রোগ ও পোকামাকড় সহ অনিষ্টকারী প্রানী ইত্যাদি বালাই দমনে ব্যবহার্য সকল দমন পদ্ধতিগুলোর মধ্যে বুদ্ধিমত্তার সাথে বিবেচনা করে সঠিক, সহজ ও কার্যকর পদ্ধতি নির্বাচন ও ব্যবহার নিশ্চিত করা । এতে করে নির্বাচিত এক বা একাধিক পদ্ধতি অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিবেশের দিক থেকে গ্রহন উপযোগী হয় । এ ব্যবস্থাপনা ফসলের বালাইকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যাতে করে তা কোনরূপ আর্থিক ক্ষতি করতে পারে। আর এ জন্যই বলা হয় যে, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার প্রধান উদ্দেশ্য হলো অধিক ফসল ফলানোর মাধ্যমে ভোক্তাদের জন্য কোনরূপ ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকবে । সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার উপকারিতা নিচে দেয়া হলো ।
১। শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন খরচ কমিয়ে দেয়।
২। প্রাকৃতিতে বিদ্যমান জৈবিক ভারসাম্য রক্ষা করতে সহায়তা করে ।
৩। বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবহার কম হওয়ায় পরিবেশ দূষণ মুক্ত থাকে ।
৪ । উপকারী পোকা মাকড়, মাছ, ব্যাঙ, পশুপাখি ইত্যাদি সংরক্ষণে সহায়তা করে
৫। অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ ও বালাইর সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত থাকে ।
৬। বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যদির যথেচ্ছ ব্যবহার কমিয়ে আনে।
৭। অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ ও ক্ষতিকারক বালাইসমূহ কীটনাশক ও বালাই নাশক সহনশীলতা প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করার সুযোগ পায় না ।
৮ । উপযুক্ত পরিবেশ ও প্রতিবেশ বজায় থাকে ।
২। জৈবিক দমন
এই পদ্ধতিতে পোকার প্রাকৃতিক শত্রু সমূহ যেমন- পরভোজী, পরজীবি এবং রোগজীবাণু কৃত্রিম উপায়ে বৃদ্ধি করে আক্রান্ত শস্য ক্ষেতে ছেড়ে দিয়ে দমন করা হয় । অনেক পোকা আছে যারা পরজীবি ও পরভোজী হিসেবে অন্য পোকা দমনে ব্যবহৃত হয় । রোগ জীবাণুর মধ্যে ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, কৃমি সফলভাবে জৈবিক দমনে ব্যবহৃত হয় ।
৩। পরিচর্যামূলক দমন
ফল বাগান ও শস্য ক্ষেতে নিয়মিত পরিচর্যার দ্বারা কীটপতঙ্গের ক্ষতি থেকে ফল ও ফসলকে মুক্ত রাখা সম্ভব । বিভিন্ন প্রকার পরিচর্যা যেমন- জমি কর্ষণ, আগাছা নিধন, শস্য বপন ও রোপণের তারিখ পরিবর্তন, বাগানে ও শস্য ক্ষেতে সেচ ও নিষ্কাশন, ফল গাছ ও শস্য ছাঁটাই, পরিমিত সার প্রয়োগ ইত্যাদি ।
৪। পোকা মাকড় প্রতিরোধীজাত ( Resistant variety)
পোকা প্রতিরোধীজাত ব্যবহার, কীটমুক্ত চারার ব্যবহার ইত্যাদি পদ্ধতিতে পোকা দমন করা যায় ।
৫। রাসায়নিক দমন
বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যাদির মাধ্যমে কীটপতঙ্গ দমন করা হয়। এ সব দ্রব্যাদির মধ্যে কীটনাশক, আকর্ষক, বিকর্ষক, হরমোন ও খাদ্য নিরোধক উল্লেখযোগ্য ।
রাসায়নিক দমনের জন্য কীট নাশককে আবার বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায় । যেমন—
১। রাসায়নিক গঠনের উপর ভিত্তি করে ।
২। কীট পতঙ্গ বা গাছের মধ্যে কীটনাশকের কার্য প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে এবং
৩ । কীট পতঙ্গ বা গাছের মধ্যে ঔষধের প্রবেশ প্রণালির ওপর ভিত্তি করে ।
তবে কীট নাশকের ক্রিয়া এবং প্রবেশ প্রণালীর ওপর ভিত্তি করে কীট নাশককে ৫টি ভাগে ভাগ করা যায়
। (ক) পাকস্থলীর বিষ (খ) স্পর্শ বিষ (গ) অন্তর্বাহী বিষ (ঘ) ধুপন বিষ এবং (ঙ) বিতাড়ণকারী বিষ
আকর্ষকের মধ্যে ফেরামোন কৃত্রিমভাবে তৈরি করে পুরুষ পোকাকে আকৃষ্ট করে মারা যায় । বিকর্ষক কীট পতঙ্গকে নিরুৎসাহ, এড়িয়ে চলার প্রবণতা, অনাগ্রাসন ইত্যাদির মাধ্যমে দুরে সরিয়ে রাখে। হরমোন কীট পতঙ্গ দমনের আধুনিক পদ্ধতি । কৃত্রিম হরমোন যেমন- এলটুসিড, ডিমিলিন আক্রান্ত ক্ষেতে ছড়িয়ে দিলে কীট পতঙ্গ সরাসরি মরে না, কিন্তু বৃদ্ধি ব্যাহত হয় । সেই সাথে বিকলাঙ্গ, স্বল্পায়ু প্রজনন ক্ষমতা রহিত করে দমন কর যায় । খাদ্য নিরোধক, কীট পতঙ্গকে স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণে বিরত রাখে ।
৬। আইনগত দমন
কোন ক্ষতিকর পোকা কোন দেশ বা অঞ্চলে যাতে প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য আইনগত ভাবে বাধা প্ৰদান করা হয় । আক্রান্ত গাছের অংশ ও বীজ এক দেশ থেকে অন্য দেশ বা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে চলাচলে আইনগত বিধিনিষেধ আরোপ করে অনেক পোকা ও রোগের ব্যাপক বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করা হয় । এই দমন পদ্ধতিকে কোয়ারেন্টাইন দমন পদ্ধতি বলে । বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যেমন সামুদ্রিক বন্দর, আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ও সীমান্ত এলাকায় পোকা দমনের জন্য আইনগত ব্যবস্থা আছে । সারা বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের গাছ বা বীজ বা চারা আনা নেয়ার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক আইন আছে।
৭। ভৌত দমন
অধিক তাপমাত্রা প্রয়োগ করে, যেমন: গুদামে ১০-১২ ঘন্টা ৫০° সে তাপমাত্রা প্রয়োগ করলে, অন্য দিকে আক্রান্ত শস্য দানাকে প্রখর রোেদ শুকালে, অনেক ক্ষতিকর পোকা মারা যায় । অধিক ঠান্ডা যেমন: গুদাম ঘর ৫-১০° সে. তাপমাত্রায় কয়েক ঘণ্টা রেখে দিলে অনেক শস্য দানার ক্ষতিকর পোকা দমন হয় ।
অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
১। আম ফলের প্রধান পোকা কোনটি ।
২। পোকা দমন পদ্ধতিগুলোকে কত ভাগে ভাগ করা যায় ?
৩ । গাছে ও ফলে পোকার আক্রমণ সচরাচর কখন ঘটে থাকে ?
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
১ । আমের প্রধান অনিষ্টকারী পোকাগুলোর নাম লেখ । আম ছিদ্রকারী পোকার ক্ষতির ধরন বর্ণনা কর ।
২। কলার পাতা ও ফলের বিটলের বৈজ্ঞানিক নাম কী ।
৩ । যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পোকা দমনের কৌশলগুলোর নাম লেখ ।
৪ । রাসায়নিকভাবে কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলো লিপিবদ্ধ কর ।
৫ । ফল ও ফল গাছের পোকা দমনে আইপিএম পদ্ধতি গ্রহণ করলে কীভাবে লাভবান হওয়া যায় ব্যাখ্যা কর ।
৬ । ফল ও ফল গাছে আক্রমণের ক্ষতির চিহ্ন দেখে কিভাবে পোকা সনাক্ত করা যায় ?
রচনামূলক প্রশ্ন
১। ফল ও ফল গাছের আক্রমণকারী প্রধান প্রধান পোকার নাম ও বৈজ্ঞানিক নাম লেখ ।
২ । আম, লিচু ও নারিকেলের প্রত্যেকটির ৩টি পোকার নাম, তাদের ক্ষতির লক্ষণ ও প্রতিকার বর্ণনা কর ।
৩ । পোকা দমন পদ্ধতিগুলোর নাম উল্লেখ পূর্বক যে কোন একটি পদ্ধতির বিবরণ দাও ।
৪ । যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পোকা দমনের সুবিধা অসুবিধা এবং উপকারিতা বর্ণনা কর ।
৫ । আইপিএম বলতে কি বোঝায় । ফল ও ফল গাছে পোকা দমনে আইপিএম পদ্ধতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর
উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বা শরীরবৃত্তীয় কার্যক্রম ব্যাহত হওয়াকে উদ্ভিদের রোগ বলে । উদ্ভিদের শ্বসন, শোষণ, প্রশ্বেদন ও সালাকে সংশেষণ প্রক্রিয়া কোন কারণে বিঘ্নিত হলে উদ্ভিদ দেহে অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পায় । এ অস্বাভাবিকতাকে উদ্ভিদের রোগ বলে । খাদ্য প্রাণে ভরপুর ফল অতিগুরুত্বপূর্ণ ফসল । শারিরিক সুস্থতা ও সুঠাম দেহ রক্ষায় ফলের ভুমিকা অপরিসীম । রোগ ফলের সে গুণাগুণ নষ্ট করে । অতএব ফলের ও ফল গাছের রোগের ধরন, তার কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে জানা প্রয়োজন ।
ফল ও ফল গাছে নানা প্রকার রোগ হতে পারে । গাছে রোগ হলে তার নানা প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায় । গাছে বা ফলে আক্রমণের লক্ষণ বিভিন্ন রকম হয় । এই লক্ষণ গাছের শেকড়, কাণ্ড, পাতা ও ফলসহ বিভিন্ন অংশে হতে পারে । গাছে বা ফলে এই অসুস্থতার লক্ষণ দেখামাত্র উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত । তাই রোগ হওয়ার মত বা ছড়ানো উপযোগী আবহাওয়া দেখলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া একান্ত প্রয়োজন । গাছে রোগ হওয়ার লক্ষণ দেখা দেওয়া মাত্র উপযুক্ত ব্যবস্থা নিলে অনেক রোগ থেকে গাছ ও ফলকে রক্ষা করা যায় । এমনকি রোগের বিস্তার রোধ করা যায় ।
কার্যকারণের দিকে দৃষ্টি রেখে, বিজ্ঞানী ফল ও ফল গাছের রোগ ব্যধিসমূহকে পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন । যথা- ১ । ছত্রাকজনিত রোগ, ২। ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ ৩ । ভাইরাস জনিত রোগ ৪ । নেমাটোড জনিত রোগ এবং ৫ পুষ্টি উপাদানের অভাব জনিত রোগ । সবচেয়ে অধিক সংখ্যক রোগ হচ্ছে ছত্রাক জনিত, মোট রোগসমূহের প্রায় ৫০ ভাগের অধিক হবে । অপরপক্ষে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস ঘটতি রোগের সংখ্যা ৩০-৩৫ ভাগ হতে পারে । নেমাটোড দ্বারা আক্রান্ত রোগের সংখ্যা অন্যান্যদের তুলনায় কম ।
বাংলাদেশের ফল ও ফল গাছের প্রধান প্রধান রোগের তালিকা
ফল ও ফল গাছের রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকার
বৈজ্ঞানিক কৃষির বিকাশ ও উদ্ভিদ রোগের বিকাশ ফসল চাষাবাদের শুরু থেকে সমান্তরালভাবে চলছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে খাদ্য ঘাটতি মেটানোর জন্য কৃষি বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ শুরু করে। যেমন-
১। নতুন জাতের আবাদী ফসল / গাছ
২। অধিক ফলনশীল ফসলের জাত
৩। উন্নত ও আধুনিক সারের উদ্ভাবন ও ব্যবহার
৪ । অঢেল সেচের পানি এবং
৫। পতিত না রেখে জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার
কিন্তু রোগ ব্যাধির প্রতি বিশেষ নজর না রেখে এসব প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। ফলে বিভিন্ন মাধ্যমে রোগ বালাই বিস্তার লাভ করে । যেমন-
১। বীজ ও অন্যান্য অঙ্গজ বংশবৃদ্ধির উপকরণের সাথে শক্তিশালী রোগজীবাণুর আবির্ভাব
২। নতুন শস্য জাত চাষের ফলে পূর্বের রোগ জীবাণুর অধিকতর শক্তি সঞ্চয়
৩। বিরাট এলাকা জুড়ে একই ফসল ও একই জাত চাষ, নিবিড় চাষ এবং সারা বছর ফসল দ্বারা মাঠ আচ্ছাদিত থাকায় রোগজীবাণু বেঁচে থাকার, বংশ বৃদ্ধি ও বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ পায় ।
৪ । সার ও পানি নির্বিচারে ব্যবহার রোগজীবাণু বিস্তারে সহায়ক । সুতরাং যে প্রযুক্তি বা কৌশল আমরা ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োগ করছি তা রোগ জীবাণু বৃদ্ধির জন্য অনুকূল । আধুনিক প্রযুক্তি রোগ জীবাণু সম্পর্কিত বিপদ বৃদ্ধির যেমন সহায়ক, তেমনি বৈজ্ঞানিক ভাবেই রোগজীবাণু নিয়ন্ত্রণও সম্ভব।
জনসংখ্যা বৃদ্ধির মোকাবেলায় অধিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য আমাদের আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োজন । একইভাবে রোগ বালাই নিয়ন্ত্রণেও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হলো-
১। মাঠে বা বাগানে যা রোপণ বা বপন করা হবে তা শস্য/গাছে পরিণত হবে।
২। যা আবাদ করা হবে তা থেকে সর্বোচ্চ ফলন পাওয়া যাবে ।
৩। যা উৎপন্ন হবে তা নিরাপদে বাজারে আসবে এবং অবশেষে তাই গ্রাহকের নিকট পৌঁছাবে । উপরোক্ত তিনটি বাক্য হতে এটা বোঝায় যে, ফসল চাষাবাদের প্রত্যেকটি বা যে কোন ধাপে রোগ সৃষ্টি হয়। এ রোগ দমনের প্রয়োজন রয়েছে; উৎপাদনের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রেখে লক্ষ মাত্রায় পৌঁছার জন্য ।
উদ্ভিদ রোগ দমনের মূলনীতি (Principle of plant disease control)
একটি কার্যকরি উদ্ভিদ রোগ দমন কর্মসূচি প্রণয়নে নিম্নলিখিত মূল বিষয়গুলো মনে রাখা দরকার ।
১। শস্যের প্রকার ও লতা, গুল্ম গাছ, অর্থকরী ফসল, খাদ্য শস্য ইত্যাদি শস্যের বৃদ্ধির পর্যায়।
২। রোগজীবাণুর প্রকৃতি ও ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি রোগ জীবাণুর জীবনচক্র, বীজ, মাটি বা বায়ু বাহিত, বিস্তারের ধরন ইত্যাদি ।
৩ । রোগের প্রকৃতি ও অভ্যন্তররীণ বাহ্যিক, বীজ, মুল, ফুল, পাতায় আক্রমন এ সকল বিষয় মনে রেখে উদ্ভিদ রোগ দমন কর্মসূচি নিম্নলিখিত ৪টি মূলনীতির ভিত্তিতে প্রণয়ন করা যায় ।
ক. রোগজীবাণু বর্জন (Exclusion of pathogen)
খ. রোগ জীবাণু নির্মূল (Eradication of the pathogen)
গ. রোগ জীবাণুর হাত থেকে ফসলকে বাঁচানো
ঘ. রোগ প্রতিরোধী জাত উন্নয়ন (Resistant variety)
উপরোক্ত ৪(চার) মূলনীতির উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদের রোগ দমনে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় ।
১ । আইন প্রয়োগের মাধ্যমে (Legislative measures )
২ । চাষাবাদ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে (Cultural practices)
৩ । রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার (Use of Chemicals)
৪ । রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার (Use of resistant variety )
৫ । জৈবিক দমন (Biological control)
৬ । সমন্বিত রোগ দমন (IPM - Intergrated Pest Management) রোগ দমন ব্যবস্থা কোন সময় নেয়া হলে তার উপর ভিত্তি করে রোগ দমন পদ্ধতি দু'প্রকার
১। প্রোফাইলক্সিস: রোগ যাতে সৃষ্টি না হয় তার ব্যবস্থা নেয়াকে প্রিভেনটিভ ব্যবস্থা বলে ।
২। থেরাপি: রোগ শুরু হওয়ার পর রোগের বৃদ্ধি রহিত করার ব্যবস্থাকে কিউরেটিভ ব্যবস্থা বলে ।
সারণি ১ উদ্ভিদের রোগ দমন পদ্ধতিগুলো নিমে ছকে দেখানো হলো
উদ্ভিদ সংগনিরোধ (Plant Quarantine )
সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত একটি আইন যার মাধ্যমে কোন এলাকায় কোন নতুন বা অধিকতর শক্তিশালী রোগ জীবাণু প্রবেশে বাধা দেয়ার উদ্দেশে কৃষিজাত পণ্যের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয় । একে উদ্ভিদ সংগনিরোধ বলা হয় ।
১৬৬০ সালে কারবারী গাছ নিষিদ্ধ করে ফ্রান্স প্রথম উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন চালু করে । পরবর্তীতে ১৯১২ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ফেডারেল কোয়ারেন্টাইন আইন চালু হয় । বাংলাদেশে ১৯৬৬ সালে ক্ষতিকর বালাই আইন প্রণীত হয় যা ১৯৮৯ সালে সংশোধিত ও ১৯৯২ সালে বর্ধিত আকারে অনুমোদিত হয়ে চালু রয়েছে । কোয়ারেন্টাইল বা সংগনিরোধ ব্যবস্থাকে ২ ভাগে প্রয়োগ করা যায় ।
ক) Exclusive guarantine: এটা সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা ও নির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে কার্যকরি করা হয় । যেমন— আলুর মড়ক রোগ দেখা দিলে কোন দেশ ইচ্ছে করলে সে বৎসর পৃথিবীর যে কোন দেশ থেকে আলু বীজ আমদানী বন্ধ রাখতে পারে। অথবা নির্দিষ্ট কোন দেশ থেকে আলু বীজ আমদানীর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে ।
খ) নিয়ন্ত্রিত কোয়ারেন্টাইন: এটা কিছুটা শিথিল আইন । পরিদর্শন সনদপত্র প্রদান, বীজ পরিশাধন ও সনদপত্র প্রদান এবং সনদপত্র প্রদানের মাধ্যমে বীজ আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। উপরোক্ত আইন সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগের জন্য দরকার পোষক ও রোগজীবাণুর প্রাকৃতি ও রোগ বিভারের ধরনের উপর সম্যক জ্ঞান ।
কোয়ারেন্টাইন আইন কোন দেশের প্রবেশ পথে বিমান বন্দর, সামুদ্রিক বন্দর, স্থল বন্দর ইত্যাদি কার্যকরী করা যায় । ঐ সব পথে কোয়ারেন্টাইন বস্তু পরীক্ষা করা হয় । কোয়ারেন্টাইন বস্তু বলতে বোঝায়, চারা গাছ, গাছের পাতা, ফুল, ফল, কাণ্ড, মূল বা মূল সমষ্টি, বীজ সমষ্টি, বীজ, মাটি টবের গাছ ইত্যাদি যাদের মাধ্যমে অনাকাংখিত রোগজীবাণু বাহিত হতে পারে ।
প্রবেশ পথে রোগজীবানুকে তিনটি শ্রেণিতে বিবেচনা করে কোয়ারেন্টাইন বস্তু পরীক্ষা করা হয়। যথা-
শ্রেণি কঃ যে রোগজীবাণু কোন এলাকায় সম্পূর্ণ নতুন ও শক্তিশালী । যেমন- বাংলাদেশের জন্য 'Septoria nodorum' (গমের ব্লচ রোগ), সিনকাইট্রিয়াম এন্ডাবোয়োটিকাম (আলুর ওয়ার্ট রোগ)।
শ্রেণি খ: যে রোগজীবাণু নতুন নয় কিন্তু অধিকতর শক্তিশালী যেমন: ফাইটোপথেরা ইনফেসটানস (আলুর মড়ক রোগ)।
শ্রেনী গঃ যে রোগ জীবাণু সব সময় কিছু না কিছু রোগ ছড়ায় তবে মারাত্নক নয়। বাইপালোরিস অরাইজি (ধানের বাদামি দাগ রোগ)।
চাষাবাদ পদ্ধতি (Cultural practices)
চাষাবাদ পদ্ধতির মাধ্যমেও ফসলের রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যেমন ভাল এবং সুস্থবীজ বাছাই করে বপন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে জমি তৈরি, ভালোভাবে জমি চাষ দেয়া, সুষম সার ব্যবহার, শস্য পর্যায় বা জমি পতিত রেখে, আগাছা দমন করে, পরিষ্কার সেচের পানি ব্যবহার, পরিপক্ক ফসল কাটা, ফসলের আবর্জনা পরিষ্কার, ফসল সঠিকভাবে শুকানো ইত্যাদি পদ্ধতি অবলম্বন করে রোগ-জীবানু এড়িয়ে চলা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে সুস্থ বীজ বপন করলে বীজ বাহিত রোগের তীব্রতা কমে । জমিতে পটাশ সারের অভাব হলে ধানের কাণ্ড পঁচা রোগ যেমন বেশি হয়, তেমনি নাইট্রোজেনের আধিক্যে ধানের ব্লাস্ট ও ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট রোগ বেশি হয় ।
আগাছা অনেক রোগজীবাণুকে আশ্রয় দেয়। যেমন- বন্য বেগুন গাছ কেটে ফেললে আলুর মড়ক রোগ এড়ানো যায় । শস্য পর্যায় অবলম্বন করে বায়ু বাহিত রোগ লিফ রাষ্ট, পাউডারি মিলডিউ, অলটারনারিয়া রাইটের তীব্রতা কমানো যায় । জমি পতিত রেখে কৃমি জনিত শেকড়-গিট, গোড়াপচা ও মুল পঁচা রোগ দমন করা যায় ।
উচ্ছেদ (Eradication )
ও প্রধান পাষক বা বিকল্প পোষক ধ্বংসের মাধ্যমে রোগ দমন করা যায় ।
জৈবিক দমন (Biological Control)
উদ্ভিদ রোগ জীবাণুকে জীবিয় এজেন্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রণকে জৈবিক দমন বলে। এ সমস্ত এজেন্টকে এন্টাগনিষ্ট বলে । ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি কৃত্রিম এন্টাগনিস্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এন্টাগনিস্ট-এর বৈশিষ্ট্য হলো এরা উদ্ভিদের রোগ উৎপাদন করে না ।
মাটিতে বা পত্রপৃষ্ঠে রোগজীবাণু ও এন্টাগনিষ্ট একত্রে বাস করে । এ দুয়ের মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশে ভারসাম্য রক্ষিত হয় । ভারসাম্য বজায় থাকলে ফসলে রোগ হয় না বা তীব্রতা কম থাকে । কিন্তু ভারসাম্য ক্ষুন্ন হলে
অর্থাৎ এন্টাগনিস্ট যদি শক্তি হারিয়ে ফেলে তাহলে ফসলের রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় । এমনকি মহামারী দেখা দিতে পারে। এন্টাগনিস্ট-এর শক্তি বৃদ্ধি করে এ ভারসাম্য পুনরায় স্থাপন করা যায় ।
বিভিন্ন পদ্ধতিতে এটা করা যায় । যেমন-
১। হাইপার প্যারাসিটিজম: এখানে এন্টাপনিষ্ট রোগজীবাণুর রোগ সৃষ্টি করে ।
২। আরোপিত প্রতিরোধঃ রোগ সৃষ্টির ক্ষমতাশীল ভাইরাস স্ট্রেন অনুপ্রবেশের দ্বারা উদ্ভিদের প্রতিরোধ সৃষ্টি করলে পরবর্তীতে অধিকতর শক্তিশালী ভাইরাস ঐ গাছের রোগ সৃষ্টি করতে পারে না । রোগ জীবাণু দমনের এ কৌশলকে Cross Protection বলে।
৩। ব্যাকটেরিয়া ও ফাজ প্রয়োগ: ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসকারী ভাইরাস প্রয়াগের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস।
৪। ফাঁদ শস্য: কিছু শস্যের সংস্পর্শে আসলে কৃমি খাদ্যাভাবে মারা যায় । তিতা বেগুন জমিতে লাগালে কৃমির সংখ্যা কমে যায়।
৫। বৈরীভাবাপন্ন গাছ: এসপারাগাস ও মেরিগোল্ড প্রভৃতি গাছের মূল থেকে বিষাক্ত পদার্থ (পটাশিয়াম সায়ানাইড) বের হয় বলে সংবেদনশীল শস্যের সাথে এদের মিশ্র ফসল চাষ করলে কৃমির সংখ্যা কমে যায় ।
৬। মিশ্র ফসল: পোষক ও অপোষক শস্য মিশ্র ফসল হিসাবে চাষ করলে অপোষক গাছ রোগজীবাণুর সহায়ক নয় বলে পোষাকের রোগের তীব্রতা কমে যায় ।
৭। বীজবাহিত রোগ: এন্টাগনিস্ট ব্যাকটেরিয়া পাউডার বীজের সাথে মিশ্রিত করে বীজ বপন করলে বীজের পচন । চারার বরাইট ইত্যাদি রোগ কমে যায় ।
৮। মাটির জৈব সংশোধন: সবুজ সার, করাতের গুঁড়া, হাড়ের গুঁড়া, সরিষার খৈল, ছাই ইত্যাদির দ্বারা মাটি পরিশোধন করলে মাটিতে উপকারী অণুজীবের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে ফসলের রোগের তীব্রতা কমে যায় ।
পোকা দমনের মত উদ্ভিদ রোগের জৈবিক দমন এখনও কার্যকরীভাবে ব্যবসায়িকভিত্তিতে ব্যবহৃত হচ্ছে না। কিন্তু ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া Antagonist হিসাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে । যেমন Trichoderma harzianum নামক ছত্রাক ।
উদ্ভিদ নির্যাস দ্বারা রোগ দমন (Plant extract )
উদ্ভিদের নির্যাস ব্যবহার করে উদ্ভিদের রোগ দমন একটি আধুনিক প্রযুক্তি । সাম্প্রতিক কালে বাংলাদশেও উদ্ভিদ রোগ দমনে উদ্ভিদ নির্যাস সফলতার সাথে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন- রসুনের রস (পানি: রসুন - ১:১) কিংবা মান্ডার পাতার রস (পানি ও পাতা = ১৪১ ) দ্বারা বীজ শাধেন করলে চড়সড়ংরং বিহীহধং অনেক বীজবাহিত ছত্রাককে দমন করা যায়।
রোগ প্রতিরোধীজাত ব্যবহার (use of disease Resistant variety)
রোগ প্রতিরোধী বলতে পোষাকের দ্বারা পরজীবীর আক্রমণ প্রতিহত করার মতোক বুঝায়। পোষাকের এই ক্ষমতা নিজস্ব বংশ পরম্পরায় স্থায়ী। এটা জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা প্রকট (dominant) ও রোগ সংবেদনশীল প্রচ্ছন্ন বিশিষ্ট্য। প্রকট জিন যে জাতে থাকে সে জাত রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা সম্পন্ন । বিভিন্ন পদ্ধতিতে (নির্বাচন, সংকরায়ন, টিস্যু কালচার, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি) এ প্রকট “জিন” সংবেদনশীল জাতে স্থানান্তর করা যায়। রোগপ্রতিরোধ জাত ব্যবহারই হচ্ছে উদ্ভিদ রোগ দমনে উত্তম ও আধুনিক পন্থা
রাসায়নিক দমন (Chemical Control):
উদ্ভিদ রোগ সৃষ্টির পূর্বে বা পরে রোগনাশক প্রয়োগে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কার্যকারিতার উপর ভিত্তি করে রোগনাশককে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় যথা-
১) প্রতিরক্ষামূলক রোগনাশক
২) নিরাময়কারী রোগনাশক এবং অ্যান্টিবায়োটিক
প্রতিরক্ষামূলক (Preventive) রোগনাশক
এগুলো প্রতিরোধের লক্ষে রোগাক্রমণের পূর্বে বা শুরুতে প্রয়োগ করা হয় । প্রতিরক্ষামূলক রোগনাশক অজৈব ও জৈব রাসায়নিক প্রকৃতির হতে পারে । রোগ দমনের ঔষধগুলোকে মোটামুটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায় । যথা- তাম্র ঘটিত রাগ নাশক, গন্ধক ঘটিত রোগনাশক, জৈবরোগনাশক (ঔষধ), পারদ ঘটিত রোগ নাশক এবং ধুম্র উৎপাদক মাটি পরিশাধেক। অধিকাংশ ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট রোগ ঔষধ প্রয়োগে দমন করা যায় । ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ ঔষধ ব্যবহারে তেমন ফল লাভ হয় না বরং বীজ পরিশোধন দ্বারা রোগ বিস্তার রোধ করা হয় । ভাইরাস রোগ আক্রান্ত গাছকে সুস্থ করার কোন ঔষধ নেই, কেবলমাত্র আক্রান্ত গাছে কীটনাশক ছিটিয়ে জাবপোকা, হপার প্রভৃতির বিস্তৃতি রোধ করা যায়। ভাইরাস হতে পরিত্রাণের লক্ষে সুস্থ গাছ হতে বীজ নেয়ার ব্যবস্থা করা হয় । নেমাটোড জনিত রোগ ও অন্যান্য কোন কোন রোগের বেলায় মাটি পরিশোধন করতে হয় ।
সাধারণত আক্রান্ত গাছ কিংবা অজাকে রক্ষা করা ও রোগকে সরাসরি দমন করার উদ্দেশে তাম্র ঘটিত, গন্ধকঘটিত ও জৈব ঔষধ ছিটানোর ব্যবস্থা করা হয়। পারদ ঘটিত ঔষধ গুঁড়ার আকারে ডাস্টিং এর কাজে ব্যবহার করা হয় বীজ শাধেনের জন্য । ফিউমিগ্যান্ট বা ধুম্র উৎপাদক ঔষধ ব্যবহৃত হয় মাটি শোধনের জন্য । বোর্দোমিকচার সহ কয়েকটি ঔষধ নিজেরাই তৈরি করে নেয়া যায়। যে সব স্থানে বোর্দোমিকচারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । সেখানে বোর্দো মিকচারের স্থানে অন্যান্ন তাম্র ঘটিত ঔষধ যেমন কপার অক্সিক্লোরাইড, কপার-এ- কম্পাউন্ড, কুপ্রাভিট ও পেরেনকসের যে কোনটি প্রযোজ্য ।
উপরে বর্ণিত রোগনাশকগুলো গাছ বিশোষণ করে না এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা করলেও তা সর্বাঙ্গে ছড়ায় না । সাধারনত এগুলো স্থানীয় ভিত্তিতে কাজ করে । এগুলো গাছের রোগের আক্রমণ কমায় তাতে কোন সন্দেহ নেই । কিন্তু আক্রান্ত গাছকে রোগমুক্ত করে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারে না কিছু কিছু রোগ-নাশক আছে যা গাছে বিশোষিত হয়ে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে এবং গাছের দেহের মধ্যে জীবাণু থাকলে অথবা প্রবেশ করতে চেষ্টা করলে তাকে ধ্বংস করে এবং রোগ নিরাময় করে গাছকে সুস্থ করে । নিরাময়কারী রোগনাশক সিস্টেমিক বা সর্বাঙ্গবাহী, অক্সামিন, পিরাসিডিন ও বেঞ্জি মিডাজেল শ্রেনীর, সিস্টেমিক প্রকৃতির অক্সামিন, ভিটাভেক্স ও পরান্ট ভ্যাক্স । পিরামিডিন-মিলকার্ব, মিলটেক্স বেঞ্জি মিডোজল- বেনোমিল-এবং ব্যাভিস্টিন অ্যান্টিবায়াটিক রোগনাশক এটি অণুজীব থেকে উৎপন্ন এক প্রকার দ্রব্য যা অন্যান্য অনুজীবের ক্ষতি কারক। সিস্টেমিক রোগনাশকের ন্যায় এটিও সর্বাঙ্গীয় প্রকৃতির। স্ট্রেপটোমাইসিন, এগ্রিমাইসিন এক্টিডাওন, ব্লাস্টিসিডিন, কাসুমিন বিশেষ উল্লেখ্যযোগ্য অ্যান্টিবায়োটিক রোগনাশক।
সমন্বিত রোগ দমন (Integrated Pest Management IPM)
উদ্ভিদের সবগুলো রোগ দমন পদ্ধতি সমানভাবে কার্যকরী নয় এবং রাসায়নিক পদ্ধতি তাৎক্ষণিক কার্যকর হলেও রোগনাশক পরিবেশ দুষন করে। রোগ প্রতিরোধীজাত উন্নয়ন সময় সাপেক্ষ ও অন্যান্য পদ্ধতি ব্যয় বহুল ।
প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষিত না করে উদ্ভিদ রোগ দমনের সকল কার্যকর উত্তম পদ্ধতিগুলোর সমন্বয় সাধন করে রোগ দমনের যে পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা তাই সমন্বিত রোগ দমন। সুস্থ সবল রোগ জীবাণুমুক্ত বীজ ব্যবহার, পরিচ্ছন্নভাবে জমি তৈরি, আগাছা দমন, সুষম সার প্রয়োগ, রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার, মাঠে রোগ দমনে কার্যকর রোগনাশকের ন্যূনতম ব্যবহার ও উপযুক্ত সময় ফসল উত্তোলন ইত্যাদি ওচগ পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য দিক ।
রোগনাশকের নাম ও প্রয়োগ মাত্রা
বাংলাদেশে ব্যবহার জন্য অনুমোদিত ও রেজিস্ট্রিকৃত কিছু রোগনাশকের নাম ও প্রয়োগে মাত্রা নিম্নের সারণিতে দেওয়া হলো-
সারণি-১
রোগের নাম, ফসলের নাম ও রোগনাশকের নামসহ প্রয়োগ মাত্রা
অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
১ । ফল গাছের রোগ ব্যধিসমূহকে কত ভাগে ভাগ করা যায় ?
২। রোগ দমন কর্মসূচির মূলনীতি কয়টি ?
৩। কৃষি ক্ষেত্রে শক্তিশালী রোগজীবাণুর আবির্ভাব কিভাবে ঘটে ?
৪ । কীভাবে রোগজীবাণু অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করে থাকে ।
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
১। কলার প্রধান প্রধান রোগগুলোর নাম লেখ ।
২। আমের বৃত্ত পচা রোগ কোথায় দেখা যায় এবং কিভাবে আক্রমণ করে লেখ ।
৩ । বোর্দো পেষ্ট তৈরির উপাদানের নাম ও অনুপাত লেখ ।
৪ । বোর্দো মিকচার কোন কোন রোগে ব্যবহৃত হয় ব্যাখ্যা কর ।
৫ । কুলের পাউডারী মিলডিউ রোগের লক্ষণসমূহ ব্যাখ্যা কর ।
৬। ফল ও ফল গাছে রোগ সৃষ্টির কারণগুলো কি কি ।
৭ । আই পি এম বলতে কী বোঝায় লেখ ।
৮। এন্টাগনিস্ট বলতে কী বোঝায় লিখ ।
রচনামূলক প্রশ্ন
১ । ফলের প্রধান প্রধান ১০টি রোগের নাম, ফসলের নাম ও রোগের কারন লিপিবদ্ধ কর ।
২। পেয়ারার ফোসকা ও উইলট রোগ দমনের উপায় লেখ ।
৩ । সমন্বিত রোগ দমন বলতে কী বাঝায় আলোচনা কর ।
৪ । কলার পানামা রোগ, পেয়ারার ক্যাংকার ও কুলের পাউডারি মিলডিউ রোগ দমন সম্পর্কে লেখ ।
৫ । বোর্দো মিকচারের প্রস্তুত প্রণালি বর্ণনা কর ।
ফসলের লাভজনক ফলন এবং তার গুণাগুণ শুধু উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে না। সাথে সাথে সঠিক সময়ে ফসল সংগ্রহ এবং সংগ্রহ প্রণালির ওপর ও তা অনেকটা নির্ভর করে। ফসল সংগ্রহ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফলকে উৎপাদন পর্যায় হতে ব্যবহারিক পর্যায় আনা হয় । যত্নের সাথে এ কাজের তদারকি এবং সঠিক সময়ে ফসল সংগ্রহের ফলে আমরা পাই আর্থিক মূল্য সম্পন্ন গুণগতমানের ফসল এবং এর বর্ধিত খাদ্য উপাদান । ফল অক্ষত অবস্থায় দীর্ঘদিন সংরক্ষণের জন্য এবং উৎকৃষ্ট মানের প্রক্রিয়াজাত খাদ্য দ্রব্য তৈরি করার জন্য ফসল যথা সময়ে সতর্কতার সাথে সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তা অনবীকার্য। বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারের লক্ষ্য অনুযায়ী ফসল যখন নিজ নিজ জাতের সর্বোৎকৃষ্ট আকার, রং, স্বাদ এবং গুণাগুণ অর্জন করে, তখনই ফসল সংগ্রহ করা উচিত। অপরিপক্ক ফল সংগ্রহ করলে যেমন গুণাগুণ বজায় থাকে না তেমনি চাষী ফলের ন্যায্য মূল্য পায়না। আবার বেশি পরিপক্ক হলেও গুণগত মান তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে ফল দ্রবত পচেযায় । যার ফলে বেশি দিন সংরক্ষণ করা যায় না। ফলের পরিপকৃত এমন একটি অবস্থা যখন ফলের আকার ও আয়তন এবং বয়সের সর্বশেষ অবস্থা, অর্থাৎ এরপর ফলের আকার ও আয়তন আর বৃদ্ধি পায় না । ফল পাকার অর্থ হলো পরিপকৃতার পর ফলের গুণাগুণের এমন পরিবর্তন, যার মাধ্যমে ফল ভক্ষণযোগ্য বা খাবার উপযোগী হয় । ফল পাকার সাথে সাথে ফলের রং, গন্ধ ও বুনটের পরিবর্তন হয়, যার দর”ন ফল ভোক্তার নিকট গ্রহণ যোগ্য হয় ।
ফলের পরিপক্বতা
ফলের পরিপক্কতা এমন একটি অবস্থা যখন ফল আকার, আয়তন এবং বয়সে সর্বশেষ অবস্থায় পৌছে অর্থাৎ এর পর ফল আর আকার ও আয়তনে বৃদ্ধি পায় না । কিছু লক্ষণ দেখে ফলের পরিপক্বতা নিরুপণ করা যায় । এই লক্ষণ গুলো কে ফলের পরিপকৃতার লক্ষণ বা (Maturity Index) বলা হয় । ফল ধারণ থেকে দিবস সংখ্যা, আকার, আকৃতি, রং, বুনট, আপেক্ষিক ঘনত্বের পরিমান, দ্রবনীয় শক্ত পদার্থ, চিনি, অস্ত্রের হার এবং চর্বির পরিমাণ ইত্যাদি পরিপক্বতার লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ফল সংগ্রহের পূর্বে ফলের পরিপক্কতা দেখে সংগ্রহ করা উচিত। ফল সংগ্রহের সময়ের ওপর নির্ভর করে ফলের বাহ্যিক সতেজতা, ফলের স্বাদ, গুণাগুণ, গন্ধ ও আকার ইত্যাদি । ফল বর্ধনের তিনটি ধাপ বিদ্যমান। যেমন—
১। বাড়ন্ত (ফুল হতে গুটি ধারন করে উপযুক্ত হওয়া পর্যন্ত)
২। পরিপক্বতা (ফল উপযুক্ত হওয়ার পর সংগ্রহ করার পর্যায়ে পৌঁছা পর্যন্ত) এবং
৩ । পরিপক্কতার পর পেকে উঠা বা ফিজিওলোজিক্যাল ম্যাচুরিটি ।
ফল তোলার জন্য ফলের পরিপক্বতা একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা । কারণ ফল পাকা অবস্থাতেই খাওয়ার উপযুক্ত হয় । উদাহরণ- কলা, জাম, আনারস, পেয়ারা, বেল, পিচ, আঙ্গুর, লিচু ইত্যাদি একমাত্র পরিপক্ক অবস্থাতেই খাওয়া যায় । ফলের মধ্যে এমন অনেক ফল আছে যে গুলোর শ্বসন কাজ হল তালোর পর রুদ্ধ হয়ে যায় । শ্বসন কাজ বন্ধ হওয়ার ফলে তার মধ্যে সঞ্চিত শর্করা বা শ্বেতসার থেকে চিনিতে রূপান্তর ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় । যেমন- আংগুর, লেবু, জাম্বুরা, লিচু, ইত্যাদি ।
আবার ফলের মধ্যে এমন অনেক ফল আছে যে গুলার শ্বসন কাজ ফল তোলার পরও চলতে থাকে। এমনকি ফলের পরিপক্কতার সাথে সাথে শ্বসন কাজ বাড়তে থাকে এবং ফলের মধ্যে সঞ্চিত শর্করা বা শ্বেতসার চিনিতে রূপান্তরিত হতে থাকে । যেমন- আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে বেল, কামরাঙ্গা, আমড়া, ইত্যাদি । তাই এ জাতীয় ফল পরিপক্ক অবস্থা হতে খাওয়ার উপযোগী বা উপযুক্ত হওয়ার সময়ের মধ্যে পড়তে হবে । এরপর পরিবহন ও বাজারজাতকরণের কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।
বিভিন্ন লক্ষণ দেখে ফলের পরিপক্কতা নিরূপণ করা হয়। বিশেষ অবস্থায় ফলের পরিপক্বতা নিরূপণ করা কষ্টসাধ্য । যেমন-
ক) বাড়ন্তবস্থায় ফল রোগাক্রান্ত হলে অপরিপক্ক অবস্থায় পরিপক্ক ফলের মত রং ধারণ করে ।
খ) জমিতে রস ও পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি থাকলে অপরিনত বয়সের ফল পরিপক্ক দেখায় ।
গ) জমিতে রসের ও পুষ্টি উপাদানের পরিমান বেশি থাকলে এবং তাপমাত্রা কমে গেলে ফলের পরিপক্বতা বিলম্ব হয় ।
ঘ) পোকা মাকড়ের আক্রমণ হলে ফল অপরিণত বয়সে পেকে যায় ।
ঙ) হঠাৎ অতিরিক্ত ঠান্ডা আবহাওয়ায় পরিণত বয়সেও ফল পরিপক্ক হয় না ।
ফলের পরিপক্বতা নিরূপণ করা যায় দু'ভাবে যথা-
১। বাহ্যিক অবস্থা দেখে ও ।
২। অভ্যন্তররীণ পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে
১। বাহ্যিক অবস্থা: ফল ধারণ থেকে দিনের হিসাব, ফলের আকার ও আকৃতি, ফলের রং, ফলের ওজন, ফল শক্ত বা নরম, ফলের ত্বকের গন্ধ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে ।
২। অভ্যন্তরীণ: শর্করা বা শ্বেত সারের পরিমাণ, মিষ্টতার পরিমান, ফলের কষ বা রসের ঘনত্ব, বীজের পরিপুষ্টতা, ভক্ষণযোগ্য অংশের ঘনত্ব (শক্ত বা নরম অবস্থা), আঁশের পরিমাণ, আঁশের দৃঢ়তা ও স্পষ্টতা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে ।
ছক: বাহ্যিক পরিবর্তন দেখে ফলের পরিপক্কতা নিরুপণ :
ফলের নাম | ফুল ধরা হতে পরিপক্ক অর্থাৎ উপযুক্ত হওয়ার সময় (দিন) | ফলের শরীর তাত্বিক পরিবর্তন/বাহ্যিক পরিবর্তন |
| (ক) আম | ৯০-১২০ দিন | ১ । ফলের চামড়া ফিকে সবুজ রং ধারণ করে । ২। পরিপক্ক সবুজ আমের বোটা ছিড়লে কষ বের হতে থাকে এবং | তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় । ৩ । আম পরিপক্ক অবস্থায় পানিতে ডুবে যায় । ৪ । স্বাভাবিক অবস্থায় গাছ থেকে দুএকটা আধাপাকা আম ঝরে পড়ে । ৫ । আমের বোটার কষ স্বচ্ছ বিন্দুর মতো দেখায় । |
| (খ) কলা | ৯০-১২০ দিন | ১ । কলা পরিপুষ্ট হলে শিরাগুলো সমান হয়ে মোটামুটি গোলাকার হয়ে যায় । ২। কলার খোসা মসৃণ হয় ও হালকা সবুজ রং দেখা দেয় । ৩ । কলার কাদির গোড়ার দিকের কলায় হলদে রং দেখা দেয় । ৪ । কলার পিছনের ফুল শুকিয়ে যায় । |
| (গ) আমড়া | ৬০ | ১ । আমড়া পরিপুষ্ট হলে চামড়া টান টান ও মসৃণ হয় । ২। আমড়ার বোটার চারদিকে সামান্য দূরে ফিকে হলদে ও উজ্জ্বল বর্ণ হয় । ৩ । পরিপুষ্ট আমড়ার গায়ে ফোটা ফোটা কালচে চিহ্ন দেখা দেয় । |
| (ঘ) কামড়াঙ্গা | ৬০ | ১। পরিপুষ্ট ফল সামান্য হলদে হয় ও ফলের ত্বক উজ্জ্বল হয় । ২। শিরাগুলোর মাঝের গভীরতা কমে যায় অর্থাৎ শিরা গুলো নিচের দিকে মোটা হয়ে যায় । ৩ । হাতে নিলে ভারি অনুভূত হয় । |
| (ঙ) বেল | ১ বৎসর | ১। পরিপক্ক ফলের গায়ের রং হালকা হলদে ভাব হয় । ২। বোটায় চাপ দিলে বোটা খসে যায় এবং বোটার সংযোগস্থানে সামান্য ঢেউ খেলানো গর্ত হয়ে যায় । ৩ । ফলের গায়ে টোকা দিলে টন টন শব্দ করে । ৪। সামান্য জোরে আঘাত করলে ফলের চামড়া ফেটে যায় । ৫ । হাতে নিলে হালকা অনুভূত হয় । |
| (চ) পেঁপে | ২০ | ১। পেঁপের রং ঘন সবুজ থেকে হালকা সবুজাভ হলুদ হতে থাকে । ২। পেঁপের কষ স্বচ্ছ পানির মত হতে থাকে । ৩ । বোটার চারদিকে হালকা হলুদ রঙের উজ্জ্বল আভা দেখা যায় । ৪ । পেঁপের গায়ে নখ দিয়ে চাপ দিলে কষ বের হয়ে সঙ্গে সঙ্গে জমে যায় । |
| (ছ) আনারস | ১১০ | ১ । আনারসের চোখগুলো সামান্য হলুদ রং ধারণ করে ২। চোখের মধ্যস্থল চ্যাপ্টা দেখায় এবং চারপাশে সামান্য ফুলে উঠে ৩ । আনারসের নিচের দিকে হালকা হলুদ রং ধারণ করে। ৪ । চোখের উপরের খোসাগুলো ধীরে ধীরে শুকায়ে যায় । |
ফল সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি
মানুষের শরীর সুস্থ, সবল ও রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে ফলের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ । ফলের গুণগত মান বজায় রাখার জন্য সঠিক সময়ে গাছ থেকে ফল পাড়া অতীব জরুরি । ফলের ভালো ফলন এবং তার গুণাগুণ শুধু উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদের ওপর নির্ভর করে না । সঠিক সময়ে এবং সঠিক পদ্ধতিতে ফল সংগ্রহ করার উপরও ফলের গুণাগুণ এবং লাভ নির্ভর করে । অনেক সময় অনেক বেশি মূল্যে বিক্রির জন্য কাঁচা ফলই বাজারে উঠায় । এটা মোটেই উচিত নয় । মাঝে মাঝে কঁচা ফলকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পাকা রঙ ধারণ করায়ে বাজারে বিক্রয় করে । এতে অনেকে প্রতারিত হয় । লোকে জানাজানি হলে এ ধরনের ফল আর ক্রয় করতে চায় না । এতে উৎপাদক, বিক্রেতা উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয় । তাই ফল এমন অবস্থায় পড়তে হবে যাতে পাড়ার পর অতি অল্প সময়ে পাকে এবং কেউ প্রতারিত না হয় ।
ফল তরতাজা রাখার জন্য সংগ্রহের সময় বিশেষ যত্নবান হতে হবে। সংগ্রহের সময় ফল ক্ষতিগ্রস্থ বা আঘাতপ্রাপ্ত হলে বাজার মূল্য ও পুষ্টিমান কমে যায় । অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে আর্থিক ক্ষতি হবে । তবে ফলের মান বজায় রাখার জন্য পরিপুষ্ট অবস্থায় ফল সংগ্রহ করা উচিত । ফল সংগ্রহের জন্য কিছু উপকরনের প্রয়োজন হয়, যেমন- কঁচি, ছুরি, মই, রশি, ব্যাগ, ধারালো দা ইত্যাদি। ফল সংগ্রহের প্রাককালে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনায় রাখতে হবে, যেমন-
ক) ফলের পরিপক্কতার উপযুক্ত বয়সে সংগ্রহ করতে হবে ।
খ) পরিষ্কার আবহাওয়ার সময় ফল পাড়তে হবে ।
গ) ফল পাড়ার সময় সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে যাতে ফল আঘাত না পায় বা থেতলিয়ে না যায় ।
ঘ) সাবধানতার সাথে ফলগুলো এক জায়গায় জড়ো করতে হবে ।
ঙ) ফল জড়ো করার শানটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও ছায়াযুক্ত হতে হবে ।
৬) ফল পাড়ার জন্য ব্যবহৃত উপকরণ ও যন্ত্রপাতি ভালোভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে । সাধারণত দু'ভাবে ফল সংগ্রহ করা যায়। যথা-
১। হাত দিয়ে তোলা বা পাড়া এবং
২। মেশিনের সাহায্য পাড়া ।
১। হাত দিয়ে তোলা বা পাড়া: উন্নত ও উন্নয়নশীল সব দেশেই বেশির ভাগ ফল সতেজ অবস্থার বিক্রির জন্য হাত দিয়ে পাড়া হয় । হাত দিয়ে ফল পাড়ার কতগুলো সুবিধা আছে। যেমন-
- অনেক বেশি যত্ন সহকারে ফল পাড়া যায় ।
- একসাথে অনেক লোককে কাজে লাগানো যেতে পারে।
- হাত দিয়ে ফল পাড়তে এক সাথে বেশি অর্থের প্রয়োজন হয় না ।
- অপরিপুষ্ট বা যে ফল আরও কিছু সমর গাছে রাখা যাবে সেগুলো বাদ দিয়ে সংগ্রহ করা যায়।
- ফল পাড়ার সময় সহজেই চারদিকে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করে ফল পাড়া যায় ।
হাত দিয়ে পাড়ার অসুবিধাগুলো
ফল পাড়তে বেশি সময় লাগে ।
জরুরি ভিত্তিতে বেশি লাকে দরকার হলে অনেক সময় চাহিদামত লোক পাওয়া যায় না।
কোন ফল কোন বয়সে সংগ্রহ করতে হবে সে বিষয়ে সকল শ্রমিককে প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রয়োজন হয়।
২। মেশিনের সাহায্যে ফল পাড়া। হাত দিয়ে ফল পাড়া বেশি পছন্দনীয় হলেও অনেক সময় মেশিনের সাহায্যে ফল সংগ্রহ করতে হয়। মেশিনের সাহায্যে ফল সংগ্রহের কতগুলো সুবিধা আছে। যেমন-
সুবিধাগুলো-
তাড়াতাড়ি ফল সংগ্রহ করা যায় বা পাড়া যায়
কাজের পরিবেশ আধুনিক ও উন্নত মনে হয়।
কাজে নিয়োজিত লোকদের কাজ তদারকি করা সুবিধা জনক হয় ।
প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাবনা থাকলে তাড়াতাড়ি ফল পাড়া যায় ।
মেশিনে ফল পাড়ার অসুবিধাগুলোঃ
ফল পাড়ার সময় পাছের ক্ষতি হতে পারে।
যন্ত্র বা মেশিনের দাম অনেক বেশি যা সকলের পক্ষে ক্রয় করা সম্ভব হয় না ।
ছোট বাগান বা অল্প সংখ্যক পাছের জন্য মেশিন দিয়ে ফল সংগ্রহ করা লাভজনক হয় না ।
যেখানে শ্রমিক সহজলভ্য সে এলাকার মেশিন ব্যবহারের ফলে লোকের কাজ করার সুযোগ কমে যাবে, ফলে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে ।
মেশিন ব্যবহারের জন্য বড় বড় বাগান তৈরি করতে হয় ।
মেশিনে উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত, ছোট/বড়, উত্তম/খারাপ সব ফলই এক সাথে সংগ্রহ হয়ে যায় ।
ফল পাড়ার সময় বা ছিড়ার সময় যে সব ফল আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেগুলো কাচি দিয়ে কেটে পাড়া উচিত। যে সব ফল হাতের নাগালের মধ্যে থাকে না সে গুলো গাছে উঠে অথবা জালি ৰাধা বাঁশের লাঠির সাহায্যে পারা উচিত। ভাতে লাঠির মাথার জানির মধ্যে করে আস্তে আস্তে ফল পাড়া যায়। আবার লাঠির মাথার ছুরি বা কাচি বেধে বোটা কেটে ফল পাড়া যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে ফল যে পাড়তে উঠে তার কাঁধে এলে বা ঝুড়ি ঝুলারে রাখলে সুবিধাজনক হয়।
ফল পাড়ার আগে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে যে ফল কি উদ্দেশ্যে পাড়া হচ্ছে। কেননা আচার বা টক জাতীয় খাদ্য দ্রব্য হিসেবে ফল সংরক্ষণ করতে হলে অপরিপক্ক অবস্থায় অনেক সময় ফল পাড়তে হয়। অন্যদিকে ফুস জাতীয় খাদ্য দ্রব্য তৈরি করতে হলে বেশি পাকানোর প্রয়োজন হয় । ফল টাটকা অবস্থায় দূরে পাঠাতে হলে সম্পূর্ণ পরিপুষ্ট অবস্থায় পড়তে হয়। অনেক সময় বেশি দুরে পাঠাতে হলে ফল পাকার ৪-৫ দিন আগেও পাড়তে হয়। ফল পরিপুষ্ট হলে বিভিন্ন ফলের জাত বিশেষে সর্বোৎকৃষ্ট আকার, রং, স্বাদ, গন্ধ এবং গুণাগুণ অর্জন করে। আর তা ক্রেতার নিকট সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য হয়
ফল পাড়ার পূর্বে বিবেচ্য বিষয় বা গাছ থেকে ফল পাড়ার সতর্কতা
১। পুষ্টতা সঠিকভাবে নির্ধারণে করে ফল পাড়ার কাজ শুর করতে হবে। কারণ অপুষ্ট ফল পাড়লে তা ঠিকমত এবং স্বাদ, রং, সুবাস ইত্যাদির ঠিকমতো উন্নয়ন ঘটে না।
২। ফলের যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ফল সংগ্রহের কাজে শ্রমিকরা সতর্কতা ও করছে কি না তা নিশ্চিত হতে হবে। এ ছাড়া গাছে ঝাঁকি দিয়ে ফল পাড়া ঠিক নয় ।
৩ । গাছ মোচড়ানো, ফল মাটিতে ফেলে দেয়া, ফলের গায়ে আঘাত দেয়া, ফলের গায়ে মাটি লাগানো, সংগৃহিত ফলে সূর্যের তাপ লাগানো পরিহার করতে হবে ।
৪ । ফল বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে । এতে রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হয় ।
৫ । গাছ থেকে ফল পাড়ার পর দীর্ঘক্ষণ গাছের নিচে জমা করে রাখা ঠিক নয় । কারণ বাতাসে ভাসমান সে জীবাণু এ সময় আমের বোটায় আক্রমণ করার সুযোগ পায় ও বোটা পচা রোগের সৃষ্টি করে ।
৬ । সকাল বেলা ফল পাড়া ভালা, কারণ তখন আবহাওয়া ঠান্ডা থাকে, বৃষ্টি বাদলার দিনে ফল পাড়া পরিহাস, রতে হবে ।
৭ । কিছু বোটা সহ ফল সংগ্রহ করা ভালো । আমের ক্ষেত্রে ৩-৪ সে.মি. বোটাসহ আম পাড়তে পারলে বোঁটা পচা রোগের প্রকোপ অনেক কমে যায় । অবশ্য গাছ ছোট হলে এ কাজ সহজ হয় ।
৮ । ফল পাড়ার জন্য সব সময় ধারালো ছুরি ব্যবহার করতে হবে । ছোট গাছের ফল পাড়ার জন্য সিকেচার ব্যবহার । করা সুবিধাজনক ।
৯ । প্রত্যেক ফলের বোটায় একটি নরম জায়গা থাকে, সেখানে চাপ দিলে বোটা সহজেই ভেঙে যায় ।
১০ । আম পাড়ার পর কিছুক্ষণ উপুড় করে রাখা ভালো, এতে ফলের আঠা আমের গায়ে লাগতে পারে না ।
ফল বাছাইকরণ
ফল গাছ হতে সংগ্রহ করা সব ফল একই মান ও আকার সম্পন্ন হয় না । একই জাত হওয়া সত্ত্বেও ফল আকার আকৃতিতে বিভিন্ন ধরনের হয় । এদের মাঝে আবার কতগুলো রোগাক্রান্ত বা পোকায় খাওয়া হতে পারে । উলিখিত সব ধরনের ফল বাজারজাত করার পূর্বে ফলকে বাছাই বা শ্রেণিভুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন । আকার আকৃতি ও অন্যান্য গুণাগুণ বিবেচনায় বাজারজাত করা হলে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে ফলের দাম নির্ধারন সহজতর হয় । এতে করে ক্রেতা তার পছন্দ মত ফল ক্রয় করে সমতুষ্ট হতে পারে । ফলের উৎপাদিত অঞ্চল হতে দূরবর্তী কোন অঞ্চলে প্রেরণের উদ্দেশ্য থাকলে ফলের পরিপক্কতার মাত্রানুযায়ী বাছাই করে পৃথক পৃথক বাক্সে পাঠানো প্রয়োজন । এতে ফল নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে । ফল সংগ্রহকালীন সময় হতে শুরু করে বিক্রয় পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে কমবেশি ফল বাছাই সম্পন্ন হয় ।
পরিপক্ব হওয়ার পর একই গাছ হতে সংগ্রহ করা ফল একইরকম গুণ সম্পন্ন হয় না । কেননা একই গাছের সব ফল এক সাথে বড় হয় না এবং একই আকৃতির হয় না । একই সাথে পরিপুষ্ট হয় না এবং একই সাথে পাকেও না । এমনকি পাকার সময় একই ধরনের রংও ধারন করে না । একই গাছের বা একই জাতভুক্ত গাছের ফল কতগুলো রোগাক্রান্ত, পোকায় খাওয়া বা শারীরিকভাবে বিকৃত হতে পারে । এমন কি একই গাছে ফুল ও ফল হওয়ার সময় যে অংশ রোদ বা আলো বাতাস বেশি পায় সে অংশের ফলের মধ্যে এক ধরনের পরিবর্তন দেখা দেয় । আবার গাছের ভিতরের দিকের বা ডালপালার ছায়ায় যে সব ফল হয় সেগুলোর মধ্যে অন্য ধরনের পরিবর্তন দেখা যায় । গাছের যে অংশে রোদ ও আলোবাতাস বেশি পায় সে অংশের ফল সাধারণত রোদ পোড়া, উজ্জ্বল রং বা ফলের ত্বকে ফোটা ফোটা তিলের মত দাগ ইত্যাদি পাওয়া যায়। এ ফলগুলো আগে পাকে এবং বেশি মিষ্টি হয় । গাছের ভিতরে বা ছায়ায় যে ফলগুলো হয় সেগুলো সাধারণত আকারে বড় হয়, ফল ও জাত বিশেষে রং সবজ বা কোমল হয় এবং মিষ্টতা কম হয় ।
পাড়ার পর সমস্ত ফল একত্রে মিশানো অবস্থায় না রেখে বড়, ছোট, রোগাক্রান্ত বা পোকায় খাওয়া, অপরিপক্ক, শারীরিকভাবে বিকৃত, রঙ ইত্যাদি দিক বিবেচনা করে বাছাই করে শ্রেণিবিভক্ত করা উচিত । তাছাড়া ভালো ফলের আকর্ষণীয়তা ফুটে ওঠে না । ফল দেখতে সুন্দর না হলে ক্রেতা যথোপযুক্ত দাম দিতে আগ্রহী হয় না । তাই ফল পাড়ার পর বাজারে পাঠানোর আগে বাছাই করে শ্রেণিবিভক্ত করা একান্ত প্রয়োজন । খারাপ ফলগুলোকে স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করা যেতে পারে । ফল বাছাইকরণের সময় উচ্চমান সম্পন্ন ফলের সাথে নিম্নমানের ৫-১০ ভাগ মিশ্রন গ্রহণযোগ্য বলে ধরা যেতে পারে । সাধারণত আকার, আকৃতি, রং, পরিপক্বতার মাত্রা, রোগাক্রান্ত, পোকা খাওয়া ইত্যাদির উপর নির্ভর করে ফল বাছাই করা হয়ে থাকে । খারাপ ফলগুলোকে ফলজাত দ্রব্য তৈরীতে ব্যবহার করা যেতে পারে । ফল বাছাই দু'ভাবে করা যায় । যথা: ক) হাতের সাহায্যে এবং খ) মেশিনের সাহায্যে
ক) হাতের সাহায্যে ফল বাছাই করতে হলে ফল হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে ফলের আকার নির্ণয় করা হয় । চোখে দেখে ফলের আকার ও রং অনুমান করে শ্রেণি করা হয় । অনেক সময় হাতে নিয়ে ফলের ওজন নির্ণয় করা হয় । ফল শক্ত কেমন তা হাতে ধরে অনুমান করা হয় । তবে এ কাজটি ফল ভেদে বিভিন্ন রকম হতে পারে । গাছ হতে পাড়ার পর সব ফল একই রকম পাওয়া যায় না । কোনটি হালকা হলুদ, কোনটি গাঢ় সবুজ, কোনটি বড়, কোনটি ছোট, কোনটি খুব শক্ত এবং ওজন বেশি আবার কোনটি তেমন শক্ত নয় এবং ওজনে হালকা, কোনটি রোগ ও পোকা মাকড়ে আক্রান্ত কোনটি পাড়ার সময় আঘাতপ্রাপ্ত বা থেতলানো, আবার কোনটি সুস্থ ও সতেজ, কোনটি মিষ্টি ঘ্রাণ যুক্ত, আবার কোনটির কোন ঘ্রাণ নেই ইত্যাদি । হাতের সাহায্যে ফল বাছাই করলে বাছাই কাজটি অনেকাংশেই নিখুঁতি ও ভালো হয় ।
খ) মেশিনের সাহায্যে বাছাই করতে হলে ফল বাছাইয়ের আকৃতি নির্ধারণী রিং ব্যবহার করা হয় । ফল ভেদে বিভিন্ন মাপের নির্ধারণী রিং হতে পারে । যেমন- ৬০, ৬৪, ৭০, ৭৫, ৮০, ৮৫ সেমি. সাইজের রিং মেশিনে ফল বাছাই ও গ্রেডিং সহজে এবং দ্রুত করা যায় । কিন্তু কোন ফল থেতলানো বা রোগ ও পোকামাকড়ে আক্রান্ত থাকলে সেগুলো পর্যবেক্ষণ করে হাতে আলাদা করে নিতে হয় । এমনকি ফলের গায়ে ময়লা থাকলে তা হাত দিয়ে আলাদা করে নিতে হয় । মেশিনে বাছাই করা ফল কনভেয়ারের মাধ্যমে বিভিন্ন আকারের প্যাকিং বাক্সে স্থানান্তরিত হয়, যা আগে হতে নির্ধারণ করা থাকে ।
ফল বাছাইকরণের সুবিধা
১ । বিভিন্ন আকারের ফল আলাদা আলাদা করা থাকে, তাই দাম নির্ধারণ করা সহজ হয় ।
২ । আঘাত প্রাপ্ত, রোগ ও পোকামাকড়ে আক্রান্ত ফল আলাদা আলাদা থাকে, তাই ফল নষ্ট হয় না ।
৩ । ফল বাছাই করার জন্য শ্রমিক নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয় ।
৪ । বিভিন্ন আকারের ফল বিভিন্ন প্যাকিং বাক্সে সর্বোচ্চ সংখ্যায় সাজানো হয় ।
৫। প্যাকিং-এর জন্য ব্যবহৃত প্যাকেজের সংখ্যা দেখে ফলের সংখ্যা নিরুপণ করা হয় ।
৬ । ফল বাছাইকরণের মাধ্যমে ফলের মান নির্ণয় করা সহজ হয় ।
৭ । ফলের আকার এবং পরিপক্বতার ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে তা দূরে পাঠানো যাবে কিনা ।
কেননা বড় ফলের সাথে ছোট ফল একত্রে থাকলে বড় ফলের চাপে ছোট ফল নষ্ট হতে পারে ।
ফল বাছাইকরণে সতর্কতা ফল বাছাইয়ের পূর্বে বিবেচ্য বিষয় :
১ । ফল বাছাইকরণের স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর, ঠান্ডা, ছায়াযুক্ত ও যথেষ্ট বাতাস চলাচল সম্পন্ন । হতে হবে।
২। ফল বাছাইকরণের সময় ভালো ফলের সাথে আঘাত প্রাপ্ত, রোগাক্রান্ত বা পোকামাকড়ে আক্রান্ত ফল একত্রে রাখলে নষ্ট ফল দ্রুত পচে তা ভালো ফলকে নষ্ট করতে পারে । ভালো ফল এবং নষ্ট ফল পৃথক রাখতে হবে।
৩ । বাছাই করার সময় ফল এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় ছুড়ে না ফেলে আস্তে আস্তে রাখতে হবে ।
৪ । বাছাই করার সময় নিচে চট বা নরম জিনিস বিছায়ে নিয়ে তার উপর ফল নাড়াচাড়া করা উচিত । তাতে ফল কম আঘাত পাবে ।
৫ । যতদূর সম্ভব কম সংখ্যক ফল একত্রে স্তুপ করা উচিত । কেননা বেশি উঁচু করে ফলের তুপ করা হলে চাপে নিচের ফল নষ্ট হতে পাবে ।
৬ । বাছাই করার সময় উচ্চমান সম্পন্ন ফলের সাথে নিম্নানের ফলের ৫ থেকে ১০ ভাগের বেশি যেন মিশ্রণ না হয় । সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে ।
ফলের আকার অনুযায়ী গ্রেডিং
বাছাইয়ের পর ফলের আকার ও মান অনুযায়ী ফল শ্রেণিবিন্যাস করতে হবে । কারণ ভালো আকার ও ভালো মানের । ফল বেশি অর্থায়নে সাহায্য করে । বৃহৎ ও উৎকৃষ্টতর গুণসম্পন্ন ফল প্রায় সর্বদাই ক্ষুদ্র ও নিকৃষ্ট ফল অপেক্ষা অধিক অর্থ আনায়ন করে থাকে । সর্ব আকারের ও প্রকারের ফলকে একই সঙ্গে না রেখে ও গুলোকে আকার ও গুণ অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করে নিলে বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের পক্ষেই সঠিক মূল্য নির্ধারণের সুবিধা হয় এবং তাতে কারারেই ঠকবার সম্ভাবনা থাকে না । সুতরাং বিক্রয়ের জন্য ফল বাক্সবন্দী করা অথবা স্থানান্তরিতকরণের পূর্বেই সেগুলোকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে নেয়া উত্তম । একই বস্তা, ঝুড়ি বা বাক্সের নিচে ছোট এবং উপরে প্রদর্শনের জন্য বড় আকারের ফল রাখার প্রথাটি একান্তভাবে বর্জনীয় । ফলকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট মানে বিভক্তকরণ (Standardization) একটি উত্তম পদ্ধতি ।
অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
১। ফলের পরিপক্বতা কীভাবে নির্ণয় করা যায়?
২। অপরিণত বয়সে ফল পরিপক্ক হওয়ার কারণ কী ?
৩ । উচ্চমান ও নিম্নমান ফলের মিশ্রণ কত ভাগ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য ?
৪ । পরিপক্ক হওয়ার পর ফল সাধারণত কতভাবে সংগ্রহ করা যায় ?
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
১। ফল বাছাইকরণে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় লেখ।
২। ফলের পরিপক্বতার লক্ষন কাকে বলে?
৩। ফলের পরিপক্বতার ও পাকার মধ্যে পার্থক্য কী ?
৪ । গ্রেডিং কেন করা হয় ?
৫ । ফল বাছাইকরণের সুবিধাগুলো লেখ ।
রচনামূলক প্রশ্ন
১ । ফল বর্ধনের ধাপ গুলো কি কি এবং কোন কোন অবস্থায় ফলের পরিপক্বতা নিরুপণ করা হয় লেখ ।
২। ফল সংগ্রহ, বাছাই ও বাজারজাতকরণ সংক্ষেপে আলোচনা কর ।
৩ । ফল কীভাবে সংগ্রহ করা যায় এবং ফল সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা কর ।
৪ । ফলের পরিপক্বতা কীভাবে নিরূপণ করা যায় ? আম, কাঁঠাল ও পেয়ারার পরিপকৃতা পদ্ধতি লেখ ।
আমের চাষ
আম বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও উপাদেয় ফল । আমকে ফলের রাজা বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে । বাংলাদেশে প্রায় সব জেলাতেই আমের চাষ হয় । কিন্তু উৎকৃষ্ট মানের আম উৎপাদান প্রধানত উত্তর পশ্চিমের জেলাগুলোতে হয়ে থাকে । যেমন- বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর ও কুষ্টিয়া । বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৫ হাজার হেক্টর জমিতে আমের চাষ হয় এবং মোট উৎপাদন ১ লাখ ৯০ হাজার টন ।
জমি ও মাটি নির্বাচন
যে কোন ধরনের মাটিতেই আমের চাষ করা যায় । গভীর, সুনিষ্কাশিত, উর্বর দোয়াশ মাটি আম চাষের জন্য উত্তম । উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি আম চাষের জন্য নির্বাচন করতে হয় । তবে সুনিষ্কাশিত ২.৫-৩.০ মিটার নিচু পানিতল বিশিষ্ট, সামান্য অম্লীয়, উর্বর দোঁআশ মাটি আম চাষের জন্য সর্বোত্তম । অত্যধিক বেলে ও কাদামাটি এবং ক্ষারীয় মাটি আম চাষের জন্য অনুপযুক্ত । আম গাছ যথেষ্ট মাত্রায় জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। সব সময় সাতসেঁতে থাকে এরূপ মাটিতে আম ভালো হয় না। জলাবদ মাটিতে গাছের বৃদ্ধি, ফুল ও ফল ধারণ ব্যহত হয় । ৫.৫-৭.৫ অম্লমান (অর্থাৎ পিএইচ) সম্পন্ন মাটিতে আম ভালো হয় । এঁটেল মাটিতে পানি নিষ্কাশনের ভালো ব্যবস্থা থাকলেও আম চাষ করা যায় । প্রচুর সূর্যের আলো পড়ে, খোলামেলা এমন উঁচু জমি আম চাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে। শীতকালে প্রয়োজনে সেচ প্রদান করা যায় এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে। আবার বর্ষাকালে জমিতে যাতে পানি না দাঁড়াতে পারে সে জন্য পানি নিকাশের নালা থাকতে হবে ।
জমি ও গর্ত তৈরি
বাগান আকারে আমের চাষ করতে হলে এপ্রিল-মে মাসে কয়েক পশলা বৃষ্টি হলে প্রথমেই নির্বাচিত জমি লাঙ্গল দ্বারা ৩ থেকে ৪ বার গভীরভাবে চাষ দিয়ে কর্ষণ করে নিতে হবে । আচড়ার সাহায্যে আগাছা পরিস্কার করে মই দ্বারা ঢেলা ভেঙে জমি সমতল করে নিতে হবে এবং জমিতে যেন পানি না দাঁড়ায় তার জন্য যথাযথ সেচনালা তৈরি করতে হবে । বাগান আকারে গাছ লাগাতে হলে ষড়ভুজ বা বর্গাকার অনুসারে নকশা তৈরি করলে ভালো হয় । কলমের চারা হলে দুরত্ব কম দিতে হবে এবং বীজের চারা হলে দূরত্ব বেশি দিতে হবে । আর্দ্র এলাকার উর্বর পলিমাটিতে বড় জাতের গাছ ১২ মি. ×১২ মি. দূরত্বে লাগাতে হবে। শুষ্ক এলাকার উর্বর পলি মাটিতে ৯মি.×৯মি. অথবা ১০.৫ মি.×১০.৫ মি. দূরত্ব রাখা ভালো। তবে বেঁটে জাতের ক্ষেত্রে অনেক সময় দূরত্ব আরো কমানো যেতে পারে ।
সার প্রয়োগ
চারা রোপণের পূর্বে তৈরি গর্ত ভরাট করার সময় মাটির সাথে প্রতি গর্তে নিম্নোক্ত পরিমাণ সার মিশিয়ে দিতে হবে । গর্তের মাটির সাথে সার মিশানোর সময় রাসায়নিক সার গর্তের উপরের মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ভের নিচে এবং জৈব সার গর্ভের নিচের মাটির সাথে মিশিয়ে গর্তের উপরের অংশে দিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে ।
সারের পরিমাণ
সারের নাম | প্রতি গর্তে সারের পরিমাণ |
| জৈব সার | ১৮-২২ কেজি |
| ইউরিয়া | ১০০-২০০ গ্রাম |
| টিএসপি | ৪৫০-৫৫০ গ্রাম |
| এমপি | ২০০-৩০০ গ্রাম |
| জিপসাম | ২০০-৩০০ গ্রাম |
| জিংক সালফেট | ৪০-৬০ গ্রাম |
সম্ভব হলে গর্ত প্রতি ২ কেজি পচা নিমের খৈল দিতে হবে । সার মিশানোর অন্তত ১০ দিন পর চারা রোপন করা ভালো । গর্তের মাটি শুকনা থাকলে চারা রোপনের পূর্বে অর্থাৎ সার মিশানোর পরই পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে ।
চারা রোপণ ও পরবর্তী পরিচর্যা
বর্ষার সময় অর্থাৎ মে - জুন মাসে চারা রোপন করা উত্তম । তবে অতিরিক্ত বৃষ্টি বা বর্ষার সময় চারা রোপণ না করাই ভালো । মেঘাচ্ছন্ন দিনে বিকালে চারা রোপণ করা সবচেয়ে ভালো । চারা রোপণের জন্য তৈরি গর্তের ঠিক মাঝখানে চারটি খাড়াভাবে বসায়ে গোড়ার চারপাশের মাটি সামান্য চেপে দিতে হবে । চারা রোপণের পর পরই হালকা সেচ দিতে হবে ।
চারায় অতিরিক্ত পাতা থাকলে কিছু পাতা কেটে দেয়া ভালো । এতে গাছ সবল হয় এবং আকৃতিও সুন্দর হতে পারে । রোপণের পর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বুঝে ২-৩ সপ্তাহ প্রতি দিন বা একদিন পর পর ১ বার করে বিকেলে পানি সেচ দিলে ভালো হয় । চারা সবল বা দুর্বল যাই হউক রোপণের পর বাঁশের খুঁটি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে । আম বাগান আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। এ জন্য মাঝে মাঝে জমি চাষ করা ভালো। চারা রোপণের পর পরবর্তীতে বৃষ্টি না হলে প্রথম ৮ মাস বা দেড় বছর পর্যন্ত শুকনো মৌসুমে ৭ দিন পর পর সেচ দিতে হবে । এরপর ৫ বছর পর্যন্ত ১৪/১৫ দিন পর পর সেচ দিতে হবে । কলমের চারা রোপণের বছরই মুকুল দিতে পারে । তবে প্রথম বছর মুকুল জন্মালে তা ভেঙে দিতে হবে । কেননা মুকুল গুলো ভেঙে না দিলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং গাছের কাঠামো শক্ত হতে পারে । গাছের বৃদ্ধির জন্য ৩-৪ বছর পর্যন্ত মুকুল ভেঙে দেয়া উচিত । গাছ যাতে ভালোভাবে বেড়ে উঠতে পারে সে জন্য সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন ।
সারণি -১ বিভিন্ন বয়সে আমের গাছ প্রতি সার প্রয়োগের পরিমাণ সারের নাম
গাছ রোপণের বছর ২৫০ গ্রাম ইউরিয়া সমান দুই ভাগ করে একভাগে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে অর্থাৎ বর্ষার শুরুতে একভাগ অশ্বিণে অর্থাৎ বর্ষার শেষে গাছের চারদিকে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে । গাছ গুলো বৃদ্ধির সাথে সাথে জৈব রাসায়নিক সারের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে যা সারণি-১ এ দেখানো হলো । উলেখিত সার দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে । প্রথম কিস্তিতে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং দ্বিতীয় কিস্তিতে আশ্বিন মাসের দিকে প্রয়োগ করতে হবে । মাটিতে যথেষ্ট রস না থাকলে সার দেওয়ার পর সেচ দিতে হবে । ছোট গাছের গোড়া থেকে ৪০-৫০ সে.মি., মাঝারি বয়সী গাছে গোড়া থেকে ২-৩ মি. দূরে এবং বড় গাছের বেলায় দুই গাছের মধ্যবর্তী স্থানে সার প্রয়োগ করতে হবে । গাছ বড় হয়ে গেলে মধ্যবর্তী স্থানে সার প্রয়োগ করে টিলার (Power tiller) দিয়ে চাষ দিয়ে মাটির সাথে সার মিশিয়ে দিতে হবে । জিপসাম ও জিংকসালফেট প্রতি বছর না দিয়ে এক বছর পর পর প্রয়োগ করা ভাল ।
মাধ্যমিক পরিচর্যা
আম বাগানে সাধারণত প্রতি বছর দুবার চাষ দেয়া দরকার। প্রথম বার জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে এবং দ্বিতীয় বার আশ্বিন কার্তিক মাসে । গাছের গোড়ার দিকে ১ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত কাণ্ডের মধ্যে ডালপালা রাখা উচিত নয় । প্রধান কাণ্ডের ১ মিটার উপরে চারপাশে গজানো ৪/৫ টি মজবুত ডাল রেখে বাকীগুলো কেটে দিতে হবে। ফল পাড়ার সময় যে সকল মুকুল দণ্ডে আম থাকে সেগুলো ভেঙ্গে দিতে হবে । আম পাড়ার পর মরা, রোগাক্রান্ত ও অপ্রয়োজনীয় ডালা ছেটে দিতে হয় । ইহা গাছের বৃদ্ধির সহায়ক হয় । গাছের ভিতর যেগুলো ফল দেয় না অথচ ছায়াময় ও ঝাপালো হয় সেগুলো কেটে দিলে ভালো হয় । কেননা এগুলো পোকা মাকড়ের আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে।
সেচ
গাছে মুকুল হওয়ার আগে সেচ দিলে বা বৃষ্টিপাতে গাছের মারাত্মক ক্ষতি হয় । কেননা সেক্ষেত্রে মুকুল না হয়ে নতুন পাতা গজাতে পারে । নতুন পাতা গজালে সে মৌসুমে আর মুকুল হবে না । আমের গুটি মটরদানার মত হলে ১০-১৫ দিন পর পর ৩-৪ বার সেচ দিলে গুটি ঝরা বন্ধ হয় এবং আমের আকার বড় হয় । আম গাছে সেচ দেয়ার ইহাই উত্তম সময় । ঐ সময় বৃষ্টি হলে সেচ দেয়ার প্রয়াজন নেই ।
পোকা ও রোগ বালাই দমন
আম বা আম গাছ নানা ধরনের পোকা মাকড় ও রোগবালাই দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে । এক এক অঞ্চলে এক এক রকমের ক্ষতিকর পোকার আক্রমণ লক্ষ করা যায় । আমের বিভিন্ন কিটপতঙ্গের মধ্যে ১। পাতা ও ফল শোষক (Mango-hopper) (২) কাণ্ডের মাজরা পোকা (৩) ডগার মাজরা পোকা (৪) ফলের মাছি পোকা (৫) ফলের ভোমর পোকা এবং (৬) পাতার বিছা পোকা (Mango defoliator) বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য ।
পাতা ও ফল শোষক (Mango hopper):
এই পোকা গ্রীষ্ম মৌসুমে এবং ফুলের ঋতুতে অধিক সংখ্যক দেখা যায় । এদের বাচ্চা ও পূর্ণবয়স্ক পোকা ফুলের মঞ্জুরীর রস চুষে পান করে । তাতে ফুল ও ছোট ফল ঝরে পড়ে । মুকুলেও রস চোষার সাথে সাথে এ পোকা মলদ্বার দিয়ে প্রচুর পরিমাণ আঁঠালো মধুরস ত্যাগ করে যা মুকুল ও ফল গাছের গাছের পাতায় আটকে যায় । এই আঁঠালো পদার্থে ফুলের পরাগ রেণু আটকে গিয়ে ফুলের পরাগায়ণ
ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত করে। পাতা ও ফুল আটকানো মধু রসে Shooty mould fungus (শুটি মোল্ড) জন্মায় এবং ফুল ও পাতা কাল বর্ণ ধারণ করে । ফলে সালাকে সংশেষণ প্রক্রিয়া ব্যহত হয় । এতে আমের ফুল ঝরে পড়ে আমের উৎপাদন ১০০ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে। জানুয়ারির শুরুতে এবং গাছের পুষ্পিত অবস্থায় অর্থাৎ আম গাছে মুকুল আসার ১০ দিনের মধ্যে একবার এবং এর একমাস পর আর একবার প্রতিলিটার পানির সাথে এক মি:লি: সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড / ফিনম / বাসাথ্রিন) ১০ ইসি অথবা ডেসিস ২.৫ ইসি অথবা ০.৫ মি.লি. সুমিসাইডিন ২০ ইসি মিশিয়ে আম গাছের কাণ্ড, ডাল, পাতা, ও মুকুল ভালো ভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করলে আমের পাতা ও ফল শোষক পোকা অর্থাৎ আমের হপার দমন করা যায়।
কাণ্ডের মাজরা পোকা
এ পোকার কীড়া কাণ্ড ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে নরম অংশ খেতে থাকে। এতে আক্রান্ত কাণ্ডের উপরের অংশ মারা যেতে পারে । আক্রান্ত শাখা সহজেই ভেঙে যায় । বাঁকানো তার দিয়ে গর্ত থেকে পোকা বের করে মারতে হবে অথবা গর্তে বাইড্রিন/ লোসিড কিংবা আলকাতরা ঢুকিয়ে কাদা দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে দিতে হবে ।
ফলের ভোমরা পোকা: উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় এ পোকার আক্রমণ বেশি হয় । কোন কোন সময় প্রায় সমগ্র ফলই আক্রান্ত; হয় ও খাওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়ে। স্ত্রী পোকা ফলের গায়ে ছিদ্র করে তাতে ডিম পাড়ে। ছিদ্রের ক্ষতর শুকিয়ে যাওয়ার পর ছিদ্র চেনা যায় না। এ পোকা দমনের জন্য বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। প্রতি লিটার পানিতে ২ মি.লি. ডায়াজিনন ৫০ ইসি অথবা ৬০ ইসি বা লিবাসিড ৫০ ইসি মার্চের মাঝামাঝি সময় কাণ্ড ও ডালের বাকলে স্প্রে করতে হয় ।
আমের রোগ:
নিম্নে আমের প্রধান প্রধান রোগের নাম উল্লেখ করা হলো। আমের রোগের মধ্যে ১। ফোস্কা পড়া রোগ ২) পাউডারী মিলডিউ ৩) সুটি মোল্ড ৪) বাকটিপ প্রধান।
ফোস্কা পড়া বা অ্যানথ্রাকনোজ
রোগের আক্রমণে পাতা, কাণ্ড, ফুল ও ফল প্রভৃতির উপর বাদামি বা ধূসর বাদামি ফোস্কা পড়ে । এতে ফুল ও গুটি ঝরে যায় এবং ফলের উপর কালো দাগ পড়ায় তার বাজার মূল্য কমে যায় । ফেব্রুয়ারি- এপ্রিল মাসে ২-৩ বার বোর্দো মিশ্রণ (৬:৬:১০০) দ্বারা গাছকে ভালোভাবে ভিজিয়ে দিয়ে এ রোগ দমন করা যায় ।
পাউডারি মিলডিউ
এর আক্রমণে পুষ্প মঞ্জুরী ও শাখা প্রশাখার উপর সাদা গুড়ার মত ছত্রাকের স্পোর বা বীজকণা দেখা যায় । এর ফলে ফুল ও গুটি শুকিয়ে ঝরে পড়ে। ফুল ফোটার পূর্বে, ফুল ফোটার পর ও ফল ধরার পর প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মি.লি. টিল্ট বা ২ গ্রাম থিওভিট মিশিয়ে গাছে প্রয়োগ করে এ রোগ দমন করা যায়। এ ছাড়া আমের অন্যান্য রোগ গুলো হলো: ডগামরা, রেডরাস্ট, কালদাগ, পিংক রোগ, ফল পঁচা রোগ ইত্যাদি ।
ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ
সাধারণত ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে আম গাছে ফুল আসে। ফুল হওয়ার পর থেকে আম পরিপক্ক হতে ৪-৫ মাস সময় লাগে । পাকার লক্ষণ দেখে গাছ হতে আম পাড়তে হয় । যেমন- বোটার নিচের অংশ হলুদাভ রং ধারন, আমের চামড়ার রং হালকা সবুজ হওয়া, আমের বোটা ভাঙলে কষ বিন্দু বিন্দু আকারে জমা হওয়া । আম গাছের সবগুলো ফল এক সাথে পরিপক্ব হয় না। বাগানের আম এবং বাড়ি হতে দুরবর্তী স্থানে অবস্থিত গাছের আম একসাথে পাড়তে হয়। গাছ ঝাঁকি দিয়ে আম পাড়া উচিত নয়। কেননা তাতে আম আঘাত প্রাপ্ত হয়ে তাড়াতাড়ি পঁচে যায় । তাই যতদূর সম্ভব হাত দিয়ে আম পাড়া উত্তম । উঁচু ডালের আম পাড়তে হলে হালকা, শক্ত ও সাজা ২-৬ মিটার বাঁশের সরু দণ্ড নিতে হয়। বাঁশের সরু দণ্ডের মাথায় একটি চাকের সাথে দড়ির তৈরি জালি বাঁধতে হবে । বাঁশের সরু দণ্ডের মাথায় একটি চাকের সাথে দড়ির তৈরি জালি বাঁধতে হবে। এরপর জালির চাকের মধ্যে বাধায়ে আমের বোটায় টান দিলে জালে আম আটকাবে। আম পাড়ার পর ছোট, মাঝারি ও বড় আলাদা করে বাছাই করতে হবে। বাঁশের ঝুড়িতে আম পাতা বিছায়ে সারি করে আম সাজিয়ে দূরে অক্ষত ভাবে নেয়া যায় । তবে আমের প্রতি স্তরে পাতা দিতে হবে ।
ফল সংরক্ষণ
সাধারণত বেশিরভাগ আম পাকার পর ৭ দিন রাখা যায়। পরিপক্ক আম পেড়ে শক্ত ও সবুজ অবস্থায় বাঁশের ঝুড়ি বা বাস্কেটে ভালভাবে প্যাকিং করে ৭০- ৯° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এবং ৮৫-৯০ শতাংশ আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ৪-৭ সপ্তাহ ভালোভাবে রাখা যায় । পরিপক্ক আম তরল মামের আবরন দিয়ে ঠান্ডা ঘরে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশিদিন রাখা যেতে পারে । কাঁচা আম হতে আবার আমসি, আমসত্ত্ব, আঁচার, কাসুন্দি, ইত্যাদি খাদ্য তৈরি করে সংরক্ষণ করা যায় । পাকা আম থেকে জ্যাম, ফুট জুস, ফুট সিরাপ, জেলি, আমসত্ত্ব, প্রভৃতি প্রস্তুত করা যায়। শাঁসযুক্ত পাকা আম বাতেল বা টিনে সিরাপের মধ্যে সংরক্ষিত করা যায়। ৫০°-৫২° সে. তাপমাত্রায় গরম পানিতে ১০ মিনিট ভিজিয়ে রেখে পরে তুলে রাখলে বেশি দিন আম সংরক্ষন করা যায় ।
কাঁঠালের চাষ
কাঁঠাল পৃথিবীর বৃহত্তম ফল এবং এটি আমাদের জাতীয় ফল । সাধারন মানুষের অত্যন্ত প্রিয় ফল । কাঁঠালকে গরিবের খাদ্য বলা হয় । কেননা এত বেশি পুষ্টি উপাদান আর কোন ফলে পাওয়া যায় না। কাঁঠাল পাকা ও কাঁচাউভয় অবস্থায় খাওয়া যায় । আঁঠাল এমন একটি ফল যার প্রত্যেকটি অংশ ব্যবহৃত হয়। কাঁচা কাঁঠাল সবজি হিসেবে ব্যবহার হয় । কাঁঠাল গাছ বহুবর্ষজীবী চিরহরিৎ বৃক্ষ। এ গাছ ১০-১৫ মি. উঁচু হয়ে থাকে। স্ত্রী ফুল ও পুরুষ ফুল একই গাছে পৃথক পৃথক ভাবে ধরে। কাঁঠালের ফল বহু ফলের সমষ্টি এবং সরোসিস নামে পরিচিত। একটি কাঁঠালের মধ্যে অনেক কোয়া থাকে । প্রত্যেকটি কোয়াই একটি ফল। কাঁঠাল গাছের পাতা, কাণ্ড, ফল, বীজ সব কিছুই মূল্যবান এবং বহুলভাবে ব্যবহৃত হয় ।
মাটি ও জমি নির্বাচন
প্রায় সব ধরনের মাটিতেই কাঁঠালের চাষ করা যায় । পানি দাঁড়ায় না এমন উঁচু ও মাঝারি উঁচু সুনিষ্কাশিত উর্বর জমি কাঁঠালের জন্য উপযোগী। দোঁয়াশ, বেলে দোঁয়াশ, এটেল ও কাকুরে মাটিতেও এর চাষ করা যায়। এটেল দোয়াশ মাটি কাঁঠাল চাষের জন্য সবচেয়ে উত্তম । তবে গভীর সুনিষ্কাশিত পলি দোয়াশ মাটিতে কাঁঠালের ফলন গুলো হয় । কাঁঠাল গাছ বেশি ক্ষার বা অম্ল পছন্দ করে না । তবে সামান্য অম্ল লাল মাটিতে কাঁঠাল ভালবদ্ধতার ব্যাপারে অত্যন্ত সংবেদনশীল। গাছের গোড়ায় কয়েকদিন দাড়ানো পানি থাকলে গাছ মারা যায় । এইজন্য যে সব স্থান ব্যাকালে বন্যার পানিতে পাবিত হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান সেখানে কাঁঠাল গাছ লাগানো উচিত নয় । মাটি বেশি গভীর হলে কাঁঠাল গাছের জন্য ভাল। কেননা এর শিকড় মাটির খুব গভীরে যায়। গাছের শিকড় মাটির নিচে পানির তলের সংস্পর্শে এলে গাছ মারা যেতে পারে। এমন কি বাঁচলেও সহজে ফল ধরতে চায় না । ভূ-গর্ভস্থ মাটির নিচে পানির তল ২ মি: মিটারের বেশি নিচে হলে ভাল । সারা দিন আলো পায় এমন উঁচু জমি কাঁঠালের পছন্দনীয় তবে আংশিক ছায়া তলেও চাষ করা যায় ।
গাছ জমি ও গর্ত তৈরি
আগাছা পরিষ্কার করে গভীর ভাবে কর্ষন করে কয়েকটি চাষ দিয়ে ভালোভাবে জমি তৈরি করতে হবে। চারা লাগানোর পূর্বে জমিতে নালা কেটে পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। চারা লাগানোর জন্য বর্গাকার ও ষড়ভূজ রোপণ পদ্ধতি অনুসরণ করে রোপণের ১০ দিন পূর্বে ১২ মি. দূরে দূরে ১ মিটার দৈর্ঘ্য ১ মিটার গভীর ও ১ মিটার প্রস্থ গর্ত তৈরি করতে হবে। গর্তের উপরের দুই-তৃতীয়াংশে মাটি আলাদা রাখতে হবে। উপরের এই দুই-তৃতীয়াংশে মাটির সাথে জৈব সার মিশিয়ে গর্ভের নিচের দিক এবং গর্ভের নিচের অংশের মাটির সাথে রাসায়নিক সার নিম্নোক্ত হকে দেখানো পরিমাণ মিশিয়ে গর্তের উপরের দিক ভরাট করে ১০-১৫ দিন রাখতে হবে । মাটি শুকনা থাকলে প্রয়োজনে পানি দিয়ে পর্বের মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে। তবে গর্ভের নিচের অংশের মাটির সাথে রাসায়নিক সার মিশিয়ে মাটির মধ্যে হালকা কোপ দিয়ে ৫০০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫০ গ্রাম এম পি সার মিশিয়ে দিতে হবে। এর ১০-১৫ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।
সারের নাম | প্রতি গর্তে সারের পরিমাণ |
| গোবর/কম্পোস্ট | ২৫-৩৫ কেজি |
| টিএসপি | ১৯০-২১০ গ্রাম |
| এমপি | ১৯০-২১০ গ্রাম |
সার প্রয়োগ
বড় কাঁঠাল গাছে সার দেওয়ার প্রচলন কম । তবে সঠিক পরিমাণে সার দিলে ফলন ভালো হয় । বিভিন্ন বয়সের গাছে সার প্রয়োগের পরিমাণ নিচের সারণিতে দেখানো হলো। সারণি ও বিভিন্ন বয়সে গাছে বিভিন্ন সার প্ররোপের পরিমাণ
| সার | ৫ বছর পর্যন্ত | ৬-১০ বছর পর্যন্ত | ১০ বছরের উর্ধ্বে |
| গোবর (কেজি) | ১০-১৫ | ১৫-২০ | ২০-৩০ |
| ইউরিয়া (গ্রাম) | ২৫০ | ৫০০ | ১০০০ |
| টিএসপি (গ্রাম) | ২৫০ | ৫০০ | ১০০০ |
| এমপি | ২৫০ | ৫০০ | ১০০০ |
সম্পূর্ণ গোবর সার ও টি এসপি সার এবং অর্ধেক ইউরিয়া ও এমপি সার বর্ষার শুরুতে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে গোড়া থেকে অন্তত ৫০ সে:মি: দূরত্বে গাছের চারিদকে ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে । বাকি অর্ধেক ইউরিয়া ও এমপি সার বর্ষার শেষে ভাদ্র আশ্বিন একইভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সার ডিবলিং পদ্ধতিতে ও প্রয়োগ করা যেতে পারে। গাছের বয়স যতই বাড়বে গাছের গোড়া হতে সার দেয়ার দূরত্ব ততই বাড়াতে হবে । ২০-২৫ বছরের পূর্ণ বয়স্ক কাঁঠালের বাগানে দুটো সারির মাঝখান দিয়ে সার ছিটিয়ে চাষ দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়াই উত্তম। তবে মাটিতে তেমন রস না থাকলে সার প্রয়োগের পর সেচ দিতে হবে । যেন কোন অবস্থাতেই জলাবদ্ধতা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে ।
রোপন পরবর্তী পরিচর্যা
কাঁঠালের বাগান আগাছামুক্ত রাখতে হবে। গাছের গোড়া বছরে দুবার পরিষ্কার করা ভালো । চারা লাগানোর পর ৩-৪ বছর পর্যন্ত গোড়া পরিষ্কার করে গোড়ায় হালকা মাটি দিয়ে চেপে দিতে হবে। সেপ্টেম্বর মাসে একবার এবং এপ্রিল মাসে একবার এ ব্যবস্থা অনুশীলন করা ভালো । চারার গোড়া হতে ২-৩ মি: বাড়ার পর মাথা কেটে দেয়া যায়। এরপর মাথার চারদিকে ডাল বের হলে তা রেখে দিতে হবে। শুকনো রোগাক্রান্ত এবং নিচের দিকে ঝুলে থাকা ডাল ছেটে দিতে হবে । ফল পাড়ার কিছুদিন পর কাণ্ড সমান করে বোঁটা কেটে ফেলতে হবে । গাছের ভেতরের দিকের ছোট ছোট শাখা প্রশাখা ছেটে দিলে আলো বাতাস সহজে ঢুকতে পারবে এবং গাছ তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পাবে। তবে ডাল ছাটার পর রোগ ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ ঠেকাতে বোর্দোমিক্সার বা ডায়থেন এম-৪৫ ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত । সাধারণত ৭-৮ বৎসরের গাছে ফল ধরে, গাছ বয়স্ক হলে গুড়িতে ও পরে গোড়ার দিকে ফল ধরে। ডিসেম্বর হতে ফেব্রুয়ারি মাসে ফুল ধরে এবং মে হতে জুলাই মাসে ফল থাকে । গাছে প্রথম দিকের ফল বড় হয় এবং পরের দিকের ফল ছোট হয়। এক বছর বেশি ফল দিলে পরের বছর ফল কম দেয় । তবে বেশি ফলন পাওয়ার জন্য ফুল আসার সময় ২-৩ বার সেচ দেওয়া যায়। বর্ষার পর গাছের গোড়ার চারপাশের মাটি সরায়ে ৫-৭ দিন খোলা রেখে সার ও সেচ দিলে উপকার হয় । ফল না ধরলে অনেক সময় গাছের নিচে ধোয়া দেয়া হয় । গাছে কখনও ফল ফাটতে দেখা দিলে কিছু মুল ছাটাই করে দেয়া যেতে পারে। এছাড়া দা দ্বারা কাণ্ডের উপর স্থানে স্থানে কোপ দিয়ে কষ বের করে দিলে উপকার পাওয়া যায়।
পোকা ও রোগ বালাই দমন
কাঁঠালের মুচি ও ফলের মাজরা পোকা প্রধান ক্ষতিকর পোকা হিসেবে গণ্য করা হয়। এ পোকার আক্রমণে মুচি(ফুল) । ঝরে যায় । সুতরাং মুচি আসার সময় প্রতি লিটার পানিতে ১.০ মি:লি: সাইপার মেথ্রিন/রিপকর্ড/ সিমবুস ১০ ইসি বা ১ মি: লি: ডেসিস ২.৫ ইসি বা ০.৫ মি:লি: ফেনভ্যালিরেট (সুমিসাইডিন) ২০ ইসি বা ২.০ মি: লি: ফেনট্রোথিয়ন (সুমিথিয়ন) ৫০ ইসি বা ডায়াজিনন ৫০ ইসি স্প্রে করে ফুল বা মুচি ভিজিয়ে দিতে হবে । ১৫ দিন পর পর এক বা দুবার স্প্রে করলেই এ পোকা দমন করা যাবে ।
রোগ দমন
ফলা পঁচা রোগ কাঁঠালের একটি মারাত্মক রোগ। এ রোগের জীবাণু পুরষ ফুল এবং কচি ফলে আক্রমণ করে । এর ফলে ফল ঝরে পড়ে । ঝরে পড়া ফল ও ফুল সমূহ বাগান থেকে সংগ্রহ করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে । বাগান আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। এবং রোর্দা মিকচার দিয়ে স্প্রে করে সব ফুল ভিজিয়ে দিতে হবে ।
ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ
গাছে খুব বেশি ফল ধরলে কিছু ফল সবজি খাবার জন্য কেটে নেয়া ভালো এতে বাকি ফলের আকৃতি বৃদ্ধি পায় । গ্রীষ্মের শেষে জুন মাসে ফল পাকে । ফল পুষ্ট হলে গায়ের কাপগুলো গোলাকার হয় এবং খোসার রং সবুজ পীত হয় ।
পুষ্ট ফল বোঁটা সমেত পেড়ে ঘরের গরম জায়গায় রেখে দিলে ৪-৭ দিনের মধ্যে পেকে যায় । ফল দ্রুত পাকার জন্য পাড়া ফলের বোটাতে লবণ বা চুন দেয়া হয়। কাঁচা অবস্থায় লাঠি দিয়ে আঘাত করলে ঠন ঠন শব্দ হয় । আর পাকা অবস্থায় ডেব ডেব শব্দ হয় । দূরবর্তী স্থানে পাঠাতে হলে পুষ্ট ফল পেড়ে তখনই গাড়িতে সাজাতে হবে । তবে বড় কাঁঠাল নিচের দিকে এবং ছোট কাঁঠাল উপরের দিকে দিয়ে সাজাতে হয়। এ সময় গাড়িতে খড় বিছিয়ে দিতে হয় অন্যথায় ঝুঁকিতে কাঁঠালের কাঁটায় দাগ পড়ে এবং তাতে কাঁঠালের মান কমে যায় । সাধারণত কাঁঠাল হিমাগারে রাখা হয় না। তবে ১১° - ১২° সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও শতকরা ৮৫-৯০ ভাগ আপেক্ষিক আদ্রতায় ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত রাখা যেতে পারে। পাকা ফলের কোয়া থেকে রস, সিরাপ, জেলি, ক্যান্ডি তৈরি করে রাখা যায় ।
কুল চাষ
স্বাদ ও পুষ্টি মানের বিচারে কুল একটি উৎকৃষ্ট ফল। এদেশের সব শ্রেণির লোকের নিকট এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ফল । পৃথিবীতে উৎপাদিত কুল দুই প্রকার, যথা- ১। চীনা কুল এবং ২। ভারতীয় কুল । চিনা কুল গাছ ক্ষুদ্রাকার, সরল এবং পত্র পতনশীল, বসন্তকালে ফুল ধরে এবং শরৎকালে পাকে। ভারতীয় কুল মাঝারি আকারের ও ছড়ান প্রকৃতির, শরৎকালে ফুল ধরে এবং শীতকালে ও বসন্তের প্রারম্ভে ফল পাকে। এটা কিছু পরিমান পত্র পতনশীল । দীর্ঘাকৃতি ও সুমিষ্ট নারিকেলী কুলকে জিজিফাস যুযুবা এবং অম্লমধুর ও নাম গোত্রহীন কুলকে জিজিফাস ভালগারিস নামে অভিহিত করা হয়। কুলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি আছে ।
জমি ও মাটি নির্বাচন
কুল গাছ অত্যন্ত কষ্টসহিঞ্চ। তাই যে কোন প্রকার মাটিতে ইহা জন্মানো যায়। যদিও এর উপযোগী অম্ল ক্ষারত্বের সীমারেখা দীর্ঘ, তবু নিরপক্ষ কিংবা ক্ষার মাটিতে এটি অপেক্ষাকৃত ভালো জন্মে । ভারী ও সামান্য ক্ষারযুক্ত বেলে দোঁআশ মাটি কুলের জন্য সর্বোত্তম। কুল গাছ লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা উভয়ই সহ্য করতে পারে। তথাপিও পানি নিকাশের ভালো ব্যবস্থা থাকলে ভালো হয় । কুল গাছ প্রচণ্ড খরা ও বর্ষা সহ্য করতে পারে । কুল চাষের জন্য তেমন বৃষ্টিপাতের দরকার হয় না। তাই উঁচু জমি ও কম বৃষ্টিপাত এলাকায় সহজেই কুল চাষ করা যেতে পারে। প্রচুর আলো বাতাস পায় এমন স্থান কুল চাষের জন্য নির্বাচন করা উচিত।
জমি ও গর্ত তৈরি
জমিতে ৪-৫ বার লাঙল দিয়ে চাষ ও মই দিয়ে আগাছামুক্ত ও সমতল করে নির্দিষ্ট জায়গাতে গর্ত তৈরি করতে হবে । চারা রোপণের ২-৩ সপ্তাহ আগে চারা রোপনের নির্ধারিত স্থানে ৬-৭ মিটার দূরে দূরে ১×১×১ মিটার আকারে গর্ত খনন করতে হবে। প্রতিটি গর্তের উপরের অংশের মাটির সাথে রাসায়নিক এবং নিচের অংশের মাটির সাথে জৈব সার মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে ২-৩ সপ্তাহ রাখতে হবে ।
ছক: গর্ত প্রতি সারের পরিমাণ সারের নাম
সারের নাম | গর্ত প্রতি সারের পরিমাণ |
| পঁচা গোবর | ২০-২৫ কেজি |
| টিএসপি | ২০০-২৫০ গ্রাম |
| এমপি | ২৪৫-২৫৫ গ্রাম |
| ইউরিয়া | ২০০-২৫০ গ্রাম |
তবে চারা রোপণের এক মাস পূর্বে গর্ত খনন করা উচিত। মাটি খুব উর্বর হলে রাসায়নিক সার না দিলেও চলে।
সার প্রয়োগ
নিয়মিত ভালো ফলন পেতে হলে সঠিক পরিমাণে সার প্রয়োগ করতে হবে ।
এ সমস্ত সার একবারে না দিয়ে ২-৩ বারে দিতে হবে । প্রথম বার সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে এবং দ্বিতীয় বার এপ্রিল-মে মাসে গাছের গোড়ার চারদিকে কুপিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে । ফল ধরার পর, ফল পাড়ার পর ও বর্ষার পর এই তিন বারেও উল্লিখিত সার দেওয়া যেতে পারে । গাছের বয়স বাড়ার সাথে সাথে গাছের গোড়ায় সার দেয়ার দূরত্ব ও বাড়াতে হয় । সার দেয়ার পর শুষ্ক মৌসুমে পানি সেচ দিতে হবে ।
রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা
কুলের বাগানে প্রয়োজনমত আগাছা পরিষ্কার, পানি সেচ ও নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে । নিয়মিত ভালো ফলন পেতে হলে সঠিক পরিমাণে সার প্রয়োগ করতে হবে । নভেম্বর- ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত নিয়মিত সেচ দিলে ফল বড় হয় এবং ফলন বেশি হয় । কুল গাছে ডাল ছাটাই করা খুব প্রয়োজন । ডাল ছাঁটাই এর পর খুব তাড়াতাড়ি নতুন শাখা প্রশাখা গজায় । বছরে দুইবার ডাল ছাঁটাই করা ভালো । ফল পাড়ার পর পরই বেশি করে একবার এবং ফুল আসার আগে হালকা করে আর একবার হেঁটে দিলে ফলন বেশি হয় । কুল গাছ অত্যন্ত কস্ট সহ্য করতে পারে । সে জন্য এতে ভারী ছাঁটাই দরকার হয় । কুল গাছ নতুন ডালে ফুল আসার প্রবণতা বেশি তাই ছাঁটাই করার পর নতুন করে শাখা-প্রশাখা গজায় বিধায় পরবর্তী বছর ফলন বেশি হয় । লক্ষ রাখতে হবে কুল বাগানের আশে পাশে যেনগাছ না থাকে । কেননা জলী গাছ রোগ জীবাণ ও ফলের মাছি পোকার আবাসস্থল হিসেবে কাজ করে ।
ছাঁটাইকরণ
গাছের প্রাথমিক অবস্থায় একটি শক্ত ও মজমুত কাঠামো তৈরি করে নিতে হবে। এ জন্য প্রধান কাণ্ডকে কমপক্ষে ৭৫ সে.মি. লম্বা করে তালোর পর মাথা কেটে দিতে হবে । এরপর চারদিক দিয়ে বহু নতুন শাখা বের হয়ে গাছ ঝোপালো হবে । প্রধান কাণ্ড হতে বের হওয়া ৬-৮ টি ভালো শাখা রেখে বাকিগুলো কেটে দিতে হবে । শাখা কেটে পাতলাকরণের সময় এক শাখা হতে অন্য শাখা ১৫-২০ সে:মি: দূরে রাখতে হবে । তাছাড়া মরা, শুকনা, রোগাক্রান্ত ও সরু হয়ে নুয়ে পড়া শাখাগুলো কেটে দিতে হবে । ফল পাড়ার পর খরার সময় যখন পাতা ঝরে যায় তখন ছাঁটাই করা উচিত । এপ্রিল হতে মে মাসে সাধারণত পাতা ঝরে গাছ শুকনা কাঠির মত হয় ।
পোকা মড়ক ও রোগ বালাই দমন
ফলের মাছি পোকা ফলে ডিম পাড়ে এবং ফলের ভেতর শুক্রকীটের উপস্থিতি ফলকে খাওয়ার অযোগ্য করে তোলে । কোন কোন ক্ষেত্রে গাছের সব ফলই আক্রান্ত হয়। প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১০-১৫ মি:লি: ডায়াজিনন মিশিয়ে ফল পাকার আগে মাঝে মাঝে সিঞ্চন করলে উপকারে আসে। ফল ছিদ্রকারী পোকা কুলের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর।
বয়স্ক পোকা ফলের বোটার কাছ ডিম পাড়ে এবং শুককীট ফলের ভেতর সুড়ঙ্গ তৈরি করে শাস খেতে খেতে অগ্রসর হয় । এতে ফল খাওয়ার উপযোগী থাকে না । গাছে ফল ধরার পর থেকে কিছু দিন পর পর ১০ লিটার পানিতে ১০-১৫ মি. লি. ডায়াজিনন প্রয়োগ করে এ পোকা দমন করা যায়। কুলের উইভিল ও বিছা পোকা অনেক সময় বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উভয় পোকাই প্রধানত পাতা খায় । যে কোন কীটনাশক প্রয়োগ করে দমনকরা যায় ।
ফলের পচন – এ রোগের আক্রমণে ফলের অপ্রান্তে প্রথমে বাদামি রঙের দাগ পড়ে। পরে এ দাগগুলো সমগ্র - ফলকে ঘিরে পচিয়ে ফেলে। এ রোগ প্রতিকারের জন্য ৫ চামচ ডাইথেন এম-৪৫ ২.৫ গ্যালন পানিতে মিশিয়ে। ১০ দিন । অন্তর গাছে ছিটানো যেতে পারে।
রোগ বালাই- পাউডারী মিলডিউ ও এ রোগের আক্রমণে গাছের পাতা ও ফলের উপর সাদা পাউডারের মতো একটি বস্তু জমা হয় এবং আক্রান্ত ফল ঝরে পড়ে। ফল ধরার মৌসুমে এ রোগ দেখা যায় । বোর্দোমিশ্ৰণ অথবা সালফার গুড়া প্রয়োগ করে এ রোগ দমন করা যায় ।
ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ
বীজের গাছে ফুল আসতে ৩-৪ বছর সময় লাগে। কিন্তু কলমের গাছ রোপণের ২-৩ বছরের মধ্যেই ফল পাওয়া যায়। সেপ্টেম্বর- অক্টোবর মাসে ফুল আসে এবং ফল পাকতে ৪-৫ মাস সময় লাগে । জাত ভেদে জানুয়ারি-মার্চ মাসে ফল পাকে । খুব পাকা ফল বা অপব্ধ ফল কখনও সংগ্রহ করা উচিত নয় । ফলে হালকা সবুজ বা হলুদ রং ধরতে থাকলেই ফল সংগ্রহ করতে হয়। শখায় ঝাকানি দিয়ে মাটিতে ফেলে ফল সংগ্রহ করলে অনেক ফল ফেটে গিয়ে দ্রুত নষ্ট হয় । ঝাকানি দেয়া অপরিহার্য হলে নিচে জাল পেতে ফল সংগ্রহ করা যেতে পারে ।
তাজা ফল ছায়াযুক্ত ও ঠান্ডা ঘরে সাধারণত এক সপ্তাহ পর্যন্ত ভালো ভাবে রাখা যায় । এক ডিগ্রি সেলসিয়াস । তাপমাত্রায় এক থেকে দেড় মাস সংরক্ষন করা যায়। কুলের টক, আচার, জেলি তৈরি করা হয় । পাকা ফল রোেদ শুকিয়ে রস কমিয়ে ও কুল সরাসরি রাখা যায় । পরে খাওয়ার জন্য কয়েকদিন কড়া রোদ ছড়িয়ে রাখলে বরই শুকিয়ে যায় । শুকনা বরই দিয়ে ভালো আচার তৈরি করা যায় ।
অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
১। বাংলাদেশে কত হেক্টর জমিতে আম চাষ হয়ে থাকে ?
২। সাধারণত কত অম্লমান সম্পন্ন মাটিতে আম ভালো হয় ?
৩। কাঁঠাল কোন অবস্থায় খাওয়া যায় ?
৪। কাঁঠাল কোন ধরনের ফল ?
৫। কুল সাধারণত কোন ধরনের মাটিতে চাষ করা হয় ?
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
১। কাঁঠালের চারা রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা সম্পর্কে লেখ ।
২। আম চাষের জন্য কি ধরনের জমি ও মাটির প্রয়োজন ?
৩। আমের চারার জন্য গর্ত তৈরি ও গর্তে ব্যবহৃত সারের নাম ও পরিমাণ লেখ ।
৪ । নিকৃষ্ট কুল গাছকে মিষ্টি গাছে রূপান্তর সম্বন্ধে ব্যাখ্যা কর।
৫। কাঁঠাল গাছে সার প্রয়োগ সম্পর্কে বর্ণনা কর ।
৬। কাঁঠাল চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জমিও মাটির ধরন সম্পর্কে লেখ ।
রচনামূলক প্রশ্ন
১। আম/কাঁঠাল/কুল গাছের জমি তৈরি, গর্ত তৈরি, সার প্রয়োগ ও অন্তর্বর্তী পরিচর্যা সম্পর্কে লেখ ।
২। কুল চাষের গুরুত্ব ও ব্যবহার সম্বন্ধে লেখ ।
৩। কুল গাছ ছাঁটাই সম্বন্ধে বর্ণনা কর ।
৪। কাঁঠালের গুরুত্ব ও ব্যবহার সম্বন্ধে লেখ।
৫ । আম বাগানে সার প্রয়োগের মাত্রা ও গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা কর ।
৬ । আম/কাঁঠালের ফল ও গাছের পোকা ও রোগ বালাই দমনের কৌশল বর্ণনা কর ।
ফলসমূহকে গাছের প্রকৃতি এবং উৎপাদনের পদ্ধতির দিক হতে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে ।
যথা- ১) অবৃক্ষ জাতীয় ফল এবং
২) বৃক্ষ জাতীয় ফল ।
অবৃক্ষ জাতীয় ফলের মধ্যে গুল্মজাতীয় (herbaceous) ফুটি, তরমুজ, স্টবেরি, আনারস ইত্যাদি । সিওডোস্টেম বা নকল কাণ্ড বিশিষ্ট কলা এবং রসালো কাণ্ড বিশিষ্ট পেঁপে প্রধান। বৃক্ষ জাতীয় ফলের মধ্যে সাইট্রাস গােেত্রর লেবু এবং মায়াটাসী গােেত্রর পেয়ারা প্রধান ফল ।
কলা চাষ
পৃথিবীতে প্রথম যে কটি ফলের আবাদ শুরু হয় কলা তার মধ্যে অন্যতম । মহামতি আলেকজান্ডার খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে সিন্ধু নদের উপত্যকায় কলার চাষ দেখতে পান । উষ্ণ ও আদ্র অঞ্চলের ফসল হচ্ছে কলা । এশিয়ার উষ্ণ ও আদ্র দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলেই কলার উৎপত্তিস্থল বলে অনেকে মনে করেন । অনেকের মতে আসাম-মিয়ানমার । ইন্দোচীন অঞ্চলই কলার উৎপত্তি স্থল। কলা যে বাংলাদেশের সর্ব প্রধান ফল কেবল তাই নয়, কলা পৃথিবীর সর্ব প্রধান ফল । বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৪০ হাজার হে, জমিতে কলার চাষ হয়। বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৬ লক্ষ ২৮ হাজার টনের বেশি ।
জমি নির্বাচন
প্রচুর রৌদ্রযুক্ত, সুনিষ্কাশিত, জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ উর্বর দোঁআশ ও বেলে দোঁআশ মাটি কলা চাষের উপযোগী । কাকর, বেলে, ক্ষারীয় বা লবণাক্ত মাটি কলা চাষের অনুপযুক্ত। বাংলাদেশের পলি মাটিতে কলার ফলন সবচেয়ে ভালো হয় । যদিও কলা ফসল আবাদের জন্য অনেক পানির প্রয়োজন হয়, কিন্তু কলা জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে । কলার শিকড় যেহেতু মাটির ভিতর ৯০ সে. মি. পর্যন্ত প্রবেশ করে বেশীর ভাগ শিকড় মাটির ৪৫ সে:মি:-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তাই জৈব সার সমৃদ্ধ এবং পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত উঁচু জমি যেখানে বন্যার পানি আসেনা এবং বৃষ্টির পানি জমেনা কলা চাষের জন্য সবচেয়ে ভালো। ব্যবস্থাপনা ভালো হলে কলা চাষের জন্য মাটি কোন সমস্যা নয়। তবে মাটির পিএইচ ৪.৫ থেকে ৭.৫ এর মধ্যে হওয়া চাই।
গাছ রোপণের জন্য জমি ও গর্ত তৈরিকরণ
কলা আবাদের জন্য বারবার চাষ দিয়ে জমি ভালোভাবে তৈরি করে নিতে হয় । জমি তৈরির পর ষড়ভূজি রোপণ প্রণালি অনুসরণ করে জাত ভেদে ২×২ মি. বা ২×২.৫ মি: দূরত্বে কাঠি পুতে সাকার রোপণের জায়গা চিহ্নতি করা হয় । কাঠিকে কেন্দ্র করে ১মি.×১মি.×০.৭ মি. আকারের গভীর করে গর্ত খুড়তে হবে । এ সময় গর্ভের উপরের মাটি আলাদা রাখতে হবে। ১০-১৫ দিন গর্তটি উন্মুক্ত ফেলে রাখাই ভালো । প্রথমে জৈবসার আলাদা করে রাখা উপরের মাটির সাথে মিশিয়ে গর্তে ফেলতে হবে। এরপর মাটি দিয়ে গর্তটি সম্পূর্ণ ভরে ফেলতে হবে।
চারার সংখ্যা : কলার জাত ভেদে রোপণ দূরত্ব ও হেক্টর প্রতি চারার সংখ্যা দেয়া হলো ।
| কলার জাত | গাছের উচ্চতা (সে.মি.) | রোপণের দূরত্ব (সে.মি.) | হেক্টর প্রতি চারার সংখ্যা |
| ১. অমৃত সাগর | ২১০-২৭০ | ১৮০ × ২৪০ | ২৩১৫ |
| ২. সবরী | ৩০০-৩৫০ | ২৪০ × ২৭০ | ১৫৪৩ |
| ৩. চাপা | ২৭০-৩৫০ | ২৪০ × ২৭০ | ১৫৪৩ |
| ৪. করবী | ২৪০-৩০০ | ২৪০ × ২৭০ | ১৫৪৩ |
| ৫. আনাজী | ২৭০-৩৪০ | ২৪০ × ২৭০ | ১৫৪৩ |
| ৬. কাবুলী | ১৫০-১৮০ | ১৫০ × ১৮০ | ৩৭০৪ |
চারা নির্বাচন ও রোপণ
কলা গাছের গোড়া থেকে যে তেউড় বের হয় তা দিয়ে এর বংশ বিস্তার করা হয়ে থাকে। কলার অসি চারা ও পানি চারা এই দুধরনের তেউড় বা চারা পাওয়া যায়। রোপণের জন্য অসিচারা উত্তম । কারণ এ চারা গাছের গোড়া হতে উঠে এবং পাতা সোজা, সরু ও শক্ত পড়নের হয়। চারার মূল গ্রন্থি সবল এবং মোটা থাকে। রোপণের পর এগুলো কম মরে এবং দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হয়। পানি চারা সাধারণত পুরাতন গাছের পোড়া হতে পায় । এ চারা শক্ত ও ঘন চারার মাঝ খান দিয়ে গঙ্গার। চারার পাতা চওড়া, ছড়ানো, দুর্বল পড়নের হয়। এ চারার গোড়া চিকন এবং শিকড় দুর্বল প্রকৃতির হয়। জমিতে প্রতিষ্ঠিত হতে বেশি সময় লাগে, এমনকি রোপণের পর মরে যেতে পারে।
তবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উভয় প্রকার চারার মধ্যে ব্যবধান থাকে না। কলার চারা অনেক বড় হওয়ার পরও রোপণ করা চলে তবে ছোট আকারের চারা উৎকৃষ্ট । বড় চারা প্রতিষ্ঠিত হতে বেশি সময় নেয় এবং এগুলোতে ফলনও তুলনামূলক কম । ৫-৫০ সে.মি. দীর্ঘ ও পুরু গোড়া বিশিষ্ট চারা রোপণের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট । বর্তমানে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে চারা উৎপাদিত করে রোপণ করা হচ্ছে। মাতৃগাছ হতে আলাদা করার পর নির্বাচিত চারা দেরী না করেই রোপণ করা উচিত। রোপণের পূর্বে চারার গোড়ার সমস্ত পুরাতন শিকড় ছাঁটাই করে ডাইথেন এম ৪৫(০.২%) সলিউশনে ডুবিয়ে ছান্নায় শুকিয়ে নিতে পারলে খুব ভাল হয়। এরপর কন্দ গুলো মাটির ২০-২৫ সে.মি. গভীরে রোপণ করতে হবে ।
চারা রোপণের সময়
সেপ্টেম্বর -অক্টোবর (আশ্বিন-অগ্রহায়ণ) বা জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি (মাঘ-চৈত্র) কন্দ বা সাকার রোপণের জন্য উত্তম সময় । তবে সেচের ব্যবস্থা না থাকলে এবং বৃষ্টি নির্ভর হলে মৌসুম বৃষ্টির পর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে কলার সাকার বা কন্দ রোপণ করা ভালো। শুকনো মৌসুমে বিশেষ করে জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি মাসে রোপণের পরপরই একটি সেচ খুবই উপকারী।
চারা প্রস্তুত ও রোপণ
চারা লাগানোর আগে পোড়া থেকে পুরাতন শিকড় এবং ১০-১৫ সে.মি. উপরের অংশ কেটে ফেলতে হবে। চারার গোড়ার মাতৃগাছের সাথে সংযোগকৃত দিকটি দক্ষিণ দিক রেখে রোপণ করতে হবে। এতে করে তার বিপরীত দিকে কলার কাদি হবে এবং সরাসরি কলার রোদ লাগতে পারবে না। এর ফলে কলার রং বিবর্ণ হওয়ার সুযোগ পাবে না এবং ঝড়ে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে ।
কলার চারা মাদার এমন ভাবে লাগাতে হবে যাতে চারার গোড়া বা মাথোর উপরের অংশ মাটির সমতল বরাবর থাকে এবং বাকি অংশটুকু মাটির নিচে থাকে । চারা সোজা হয়ে উঠার জন্য মাথোর চারদিকে মাটি চেপে দিতে হয় । প্রতি সারি মালার মাঝখান দিয়ে ৩০ সে.মি. চওড়া ও ২০ সে.মি. গভীর করে নালা তৈরি করে দিতে হয় । মালার মাটি দুই পাশে উঠিয়ে দিলে কলা গাছের সারি বেডের মত হয়। তাতে বৃষ্টি হলে গাছের গোড়ার পানি দাঁড়াতে পারবে না । এমনকি অতিরক্তি বৃষ্টির পানি ঐ নালা দিয়ে সহজেই বের হয়ে যেতে পারবে ।
সার প্রয়োগ কৌশল
রোপণের ১ মাস পূর্বে গর্তে এবং রোপণের পর সুষম সার প্রয়োগ করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। সারের হিসাব গাছ প্রতি করাই ভালো । জৈব বা গোবর সার ১২-১৫ কেজি, ইউরিয়া ১২০ গ্রাম টিএসপি ২৫০ গ্রাম এমপি ১২০ গ্রাম, জিপসাম ১১০ গ্রাম এবং জিংক সালফেট ২৫ গ্রাস দেয়ার সুপারিশ করা হয় । জমি তৈরির শেষ পর্যারে গাছ প্রতি হিসাব করে অর্ধেক গোবর সার জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ২x২ মি. দূরত্বে সাকার রোপণ করলে ২৫০০ গাছের জন্য ৩০ টন গোবর সার প্রয়োজন । এর অর্ধেক জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি অর্ধেক গোবর সার এবং সম্পূর্ণ টিএসপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট চারা রোপণের আগে গর্তের উপরের ২৫ সে.মি. মাটির সাথে মিশাতে হবে। চারা রোপণের ২ মাস পর থেকে শুরু করে ইউরিয়া ও এমপি সার সমান হয় কিস্তিতে দু মাস পর পর উপরি প্রয়োগ (Top dressing) করতে হয়। এগুলো কলা বাগানে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশাতে হয়। মাটিতে “লো” থাকলেই সার ছিটাতে ও মিশাতে হয় ।
নচেৎ সার প্রয়োগের পর সেচ দিতে হবে । বি এ আর সি কর্তৃক প্রণীত সার ম্যানুয়েল অনুযায়ী কলা চাষে নিম্ন সারণি অনুসারে সার প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে ।
সারণি: কলার চারা লাগানোর প্রাক্কালে সার প্রয়োগের পরিমাণ
উলেখিত সারের সুপারিশ অনুসারে ৫০% গোবর বা আবর্জনা পচা সার জমি তৈরির সময় এবং বাকি ৫০% গর্ভে দিতে হবে। এ সময় অর্ধেক টিএসপি গর্তে প্রয়োগ করতে হবে। রোপণের দেড় থেকে দুই মাস পর ২৫% ইউরিয়া ৫০% এমপি ও বাকি টিএসপি জমিতে ছিটিয়ে ভালো ভাবে কুপিয়ে মাটির সাথে মিশায়ে দিতে হবে । এর দুই থেকে আড়াই মাস পর গাছ প্রতি বাকী ৫০% এমপি ও ৫০ % ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে । ফল আসার সময় অবশিষ্ট ২৫% ইউরিয়া জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে ।
গাছ রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা
কলা গাছের জন্য গাছ রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু কলা গাছ লাগালে থেকে কলা পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত অনেক সময় লাগে, সেহেতু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বহুবিধ পরিচর্যার মাধ্যমে ভালো ফলন আশা করা যেতে পারে। রোপণ পরবর্তী পরিচর্যার বিভিন্ন দিক নিচে আলোচনা হলো ।
ক) আগাছা পরিষ্কার: কলা বাগান সব সময় আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। কলার শেকড় মাটির উপরিভাগে ১৫-২০ সে:মি: এলাকায় কেন্দ্রীভূত থাকে । তাই আগাছা দমনের জন্য কোদাল ব্যবহার করলে অগভীর কোপ দিতে হবে। বয়স্ক পাতা শুকিয়ে গেলে কেটে ফেলা উত্তম। কারন এগুলো পাকা মাকড় ও রোগ বিস্তারে সহায়ক ।
খ) সেচ ও নিকাশ: শুক মৌসুমে ক্ষেতে ২-৩ বার করে পাবন সেচ দিতে হবে। নতুবা গাছ দুর্বল হয়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত ফলন কমে আসবে! বর্ষাকালে বাগানে যাতে পানি জমে না থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে । পানি বের করার জন্য নির্দিষ্ট দূরত্বে নালা কেটে দিতে হবে ।
গ) তেউর উৎপাটন: চারা রোপণের কয়েক মাস পরই এর গোড়ার চারি পার্শ্বে তেউড় বের হতে থাকে । এসব চারা কলা গাছে থারে বের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কয়েকদিন পর পর মাটি বরাবর ৫ সে.মি. উপরে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কেটে দিতে হবে । মুড়ি ফসল উৎপাদন করতে চাইলে ফুল আসার সময় প্রতি গাছে একটি ভাল চারা রেখে বাকি গুলো কেটে দিতে হবে।
ঘ) গাছে ঠেকনা দেয়া: গাছে থাড়ে আসার পরপরই কঁদি যখন বড় হয় তার ভারে অথবা ঝড়ের দরুন মাঝারি ও দীর্ঘকায় জাতের কলা গাছ যাতে পড়ে বা ভেঙ্গে না যায় সেজন্য বাঁশের খুটি দ্বারা বাতাসের বিপরীত মুখে গাছে ঠেস দিতে হয়।
ড) মাটি তোলা: বর্ষাকালে যখন অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে গাছের গোড়া থেকে মাটি ধুয়ে যায় এবং গোড়ার শিকড় বেরিয়ে পড়ে তখন গোড়ায় মাটি তুলে দেওয়া উচিত । গাছের গোড়ায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হলে মূল পচে যেতে পারে । এ জন্য সারির দু পাশে নালা তৈরি করে গাছের গোড়ার মাটি তুলে দিতে হয়।
চ) থোর অপসারণ: কাঁদি ঢাকা ও মোচা থেকে কলা বের হওয়ার পর শেষোক্ত কলার ৪-৫ সে.মি. নিচে খোড় (ফুল/মোচা) কেটে দিতে হবে। সুর্যালাকে, গরম বাতাস, ধুলাবালি, পাকামাকড়, পাখি ইত্যাদির হাত থেকে কঁদিকে রক্ষা ও কলার রং উজ্জ্বল রাখার জন্য নীল পলিথিন বা অন্য কোন স্বচ্ছ ব্যাগ দ্বারা কঁদি ঢেকে দিতে হৰে ।
পোকামাকড় ও রোগ বালাই দমন
কলার পাতা ও ফলের বিটল পোকা
কলার পাতা যখন কঁচি অবস্থায় থাকে তখন এ পোকা কচি পাতা খেয়ে থাকে। তারপর কলার মোচা বের হওয়ার সাথে সাথে পাতা ছেড়ে কচি কলা আক্রমণ করে এবং কলার খোসা ফেঁছে খায় । এতে কচি কলার গায়ে দাগ পড়ে । কলা বড় হওয়ার সাথে সাথে দাগগুলো আকারে বড় হয় এবং কালচে বাদামি রং ধারণ করে । আক্রান্ত কলা দেখতে কুৎসিত হয় এবং বাজারদর কমে যায় ।
কলাকে রক্ষা করতে হলে ছড়িতে কলা বের হওয়ার পূর্বেই ৪২ ইঞ্চি লম্বা ও ৩০ ইঞ্চি গ্রন্থের দুমুখ ভালো একটি পলিথিন ব্যাগের এক মুখ মোচার ভেতর ঢুকিয়ে বেধে দিতে হবে। অন্য মুখ খোলা রাখতে হবে। বাতাস চলাচলের জন্য পলিথিন ব্যাগটিতে ২০-৩০টি ২ সে:মি: বাসের ছিদ্র রাখা বাঞ্চনীয়। ডাইএলড্রিন/এলড্রিন পানির সাথে মিশিয়ে গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করলে ভাল প্রতিকার পাওয়া যায়। রাষ্ট্রট্রিপ এর আক্রমণে ফলের উপর ধূসর লাল বনের বলয় সৃষ্টি হয় এবং ফলের খোল ফেটে যায়। কলার ছড়া পাতলা চট অথবা পলিথিন দ্বারা ঢেকে রাখলে ভাল ফল পাওয়া যায় । ছড়াতে ১৫ দিন পর পর ডায়াজিনন (২%) সিঞ্চন করলেও উপকার পাওয়া যায় ।
পানামা: এটি একটি ছত্রাক জাতীয় মারাত্মক রোগ। এ রোগের আক্রমণে প্রথমে বয়স্ক পাতার কিনারা হলুদ হয়ে যায় এবং পরে কচি পাতাও হলুদ রং ধারণ করে । পরবর্তীতে পাতা বোটার কাছে ভেঙে গাছের চারি দিকে ঝুলে থাকে এবং মরে যায় কিন্তু সবচেয়ে কচি পাতাটি গাছের মাথায় খাড়া হয়ে দাড়িয়ে থাকে । অবশেষে গাছ মরে যায় । কখনও কখনও গাছ লম্বা লম্বিভাবে ফেটেও যায় । আক্রান্ত গাছ গোড়াসহ উপড়িয়ে মাটি চাপা দিতে হবে এবং আক্রান্ত জমিতে ৩/৪ বছর কলা চাষ কধ রাখতে হবে ।
কলার বানচি টপ - ভাইরাস রোগ
ইহা একটি ভাইরাস জাতীয় রোগ এবং কলার জন্য খুবই ক্ষতিকর । এ রোগের আক্রমণে গাছের বৃদ্ধি হ্রাস পায় এবং পাতা গুচ্ছা কারে বের হয় । পাতা আকারে খাটো, অপ্রশস্থ এবং উপরের দিকে খাড়া থাকে । কচি পাতার কিনার উপরের দিকে বাঁকানো এবং সামান্য হলুদ রঙের হয়। অনেক সময় পাতার মধ্য শিরা ও বোটায় ঘন সবুজ দাগ দেখা যায় । আক্রান্ত গাছ গোড়াসহ উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এ রোগ বিস্তারের সহায়ক জাব পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য অনুমোদিত মাত্রায় কীটনাশক (সেভিন ব্যবহার করতে হবে ।
পাতার দাগ বা সিগাটোকা রোগ
এ রোগের আক্রমণে প্রাথমিকভাবে ৩য় ও ৪র্থ পাতায় ছোট ছাট হলুদ দাগ দেখা দেয়। ক্রমশ দাগগুলো বড় হয় ও বাদামি রং ধারণ করে । এভাবে একাধিক দাগ মিলে বড় দাগের সৃষ্টি করে এবং তখন পাতা পুড়ে যাওয়ার মত দেখায় । রোগের প্রাথমিক অবস্থায় বোর্দো মিশ্রণ প্রয়োগ করে দমন করা যায়। জমিতে সুষ্ঠ নিকাশ ব্যবস্থা ও আগাছা পরিষ্কার রাখতে হবে । ফল সংগ্রহের পর রোগাক্রান্ত পাতা পুড়ে ফেলতে হবে ।
ফল সংগ্রহ ও সরক্ষণ
কলার জাত, রোপণের সময়, আবহাওয়া ও পরিচর্যার উপর চারা রোপণ হতে কাঁদি কাটা পর্যন্ত সময়ের তারতম্য ঘটে । রোপণের পর থেকে শুরু করে ফুল বের হওয়ার পর কলা আহরণের উপযুক্ত হতে ১০০ থেকে ১৩০ দিন সময় লাগে । কলা পরিপক্ক হলে এর শিরাগুলো সমান হয়ে যায় এবং ফ্যাকাশে সবুজ রং ধারণ করে। কলা পাকার অপেক্ষা করে এ সময়ে কঁদি কেটে নামানা েহয় এবং কলা গাছ কেটে দূরবর্তী স্থানে নিয়ে ফেলে দিতে হয় । এরপর ফলগুলো এক এক করে পৃথক করে ঘরে খড়ের ওপর এক বা দুসারিতে করে সাজিয়ে আবার খড় দিয়ে ঢেকে দিতে হয় । এতে কলা সমানভাবে পাকে এবং চমৎকার রং হয় । হেক্টর প্রতি সাধারণত ২০-২৫ টন ফলন পাওয়া যায় ।
পেঁপে চাষ
পেঁপে চিরহরিৎ শ্রেণির গাছ এবং সারা বছরই ফুল ও ফল দিয়ে থাকে । পৃথিবীর বহু দেশেই পেঁপের চাষ হয় । বাংলাদেশেও পেঁপে খুবই জনপ্রিয় । পেঁপের কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে । প্রথমত: এটা স্বল্প মেয়াদি, দ্বিতীয়ত, এটা কেবল ফলই নয় সবজি হিসেবেও এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে । তৃতীয়ত, পেঁপে অত্যন্ত সুস্বাদু, পুষ্টিকর এবং ঔষধি গুণসম্পন্ন । চতুর্থত, বাংলাদেশে যেখানে দীর্ঘমেয়াদী ফল লাগানোরে স্থানের অভাব প্রকট, সেখানে যে কোন কৃষকের পক্ষে দুচারটা পেঁপে গাছ লাগানো সম্ভব ।
মাটি ও জমি নির্বাচন
সাধারণত উঁচু বেলে দোঁ-আশ বা দো-আশ মাটিতে পেঁপের ফলন ভালো হয় । পেঁপে চাষের জন্য পানি সেচের ভাল ব্যবস্থা থাকা চাই । তবে যেখানে পানি দাড়ানোর সম্ভাবনা আছে সে সব জমিতে পেঁপের চাষ করা উচিত নয় । কারণ গাছ কয়েক ঘণ্টা পানি দাড়ানো অবস্থা সহ্য করতে পারে না । মাটির গভীরতা বেশি হলে গাছ দ্রুত বাড়ে তবে অপেক্ষাকৃত অগভীর জমিতেও পেঁপে চাষ করা চলে । অধিক অম্ল বা অধিক ক্ষার মাটিতে পেঁপে ভালো হয় না । মাটির পিএইচ ৭.০ এর কাছাকাছি পেঁপে চাষের জন্য ভালো ।
জমি ও গর্ত তৈরি
উঁচু, খোলামেলা, নিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পন্ন জমি, জো বুঝে ৩/৪ বার চাষ ও মই দিয়ে ভালোভাবে তৈরি করতে হবে । আগাছা ভালো করে পরিষ্কার করে মাটি ঝুরঝুরে ও সমতল করতে হবে। গর্ত খনন: ষড়ভুঞ্জী রোপণ পদ্ধতি অনুসরণ করে জাত ভেদে ২×২ মি: দূরে ৬০×৬০×৬০ সে. মি. আকারের গর্ত খনন করে গর্তে ২০-২৫ কেজি পচা গোবর, ১ কেজি খৈল, ২০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৩০০ গ্রাম টিএসপি ও ২০০ গ্রাম এমপি সার প্রয়োগ করতে হতে । মাদা তৈরি করে পানি দিয়ে ভিজিয়ে ১০-১৫ দিন রাখার পর চারা রোপণ করা উচিত। এতে গর্তের রোগ জীবাণু ও পোকা নষ্ট হয় । এরপর গর্তের মাটির সাথে মৌল সার মিশিয়ে গর্তে প্রয়োগ করা হয় । মাটিতে রস থাকলে এক সপ্তাহের মধ্যে মৌল সারের বিক্রিয়া শেষ হয়ে যায় । চারা লাগানোর পূর্বে গর্তের মাটি কুপিয়ে জমির সমতল হতে ১৫ সি.মি. উঁচু করে মাদা তৈরি করতে হয় । তাতে বৃষ্টির পানি সহজে গড়ায়ে যাবে এবং গাছের বৃদ্ধির জন্য সহায়ক হবে । কেননা পেঁপে গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না ।
বীজের হার
দুই মিটার দূরে দূরে সারি করে প্রতি সারিতে ২ মিটার দূরত্বে চারা রোপণ করলে ১ হেক্টর জমিতে ২৫০০ গাছের জন্য ৭৫০০ টি চারার প্রয়োজন হয়। সদ্য সংগৃহীত বীজ হলে ১৪০-১৬০ গ্রাম বীজ দিয়ে প্রয়োজনীয় চারা তৈরি করা যায় । পুরাতন বীজ হলে ২৫০-৩০০ গ্রাম বীজ লাগবে ।
চারা তৈরি
বীজ থেকে তৈরি চারা গাছ লাগিয়ে পেঁপে চাষ করা হয়। বীজ তলায় বীজ বুনার দুইমাস পর চারাগুলো ১০ সে:মি: : বড় হলে জমিতে রোপণ করা যেতে পারে । পলিথিন ব্যাগে চারা তৈরি করলে রোপণের পর চারা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৫×১০ সে:মি: আকারের পলি ব্যাগে সমপরিমাণ বালি, মাটি ও পঁচা গোবর মিশ্রণ ভর্তি করে ব্যাগের তলায় ২ ৩ টি ছিদ্র করতে হবে। তারপর এতে সদ্য সংগৃহীত বীজ হলে ১টি এবং পুরাতন বীজ হলে ২-৩ টি বীজ বপণ করতে হবে। একটি ব্যাগে একের অধিক চারা রাখা উচিত নয় । ২০-২৫ দিন বয়সের চারা গাছে ১-২ % ইউরিয়া মিশ্রিত পানি স্প্রে করলে চারার বৃদ্ধি ভালো হয়
চারা রোপণ পদ্ধতি
দেড় থেকে ২ মাস বয়সের চারা রোপণ করা হয় । ২ মিটার দূরে দূরে ৬০×৬০×৬০ সে.মি. আকারের গর্ত করে রোপণের ১৫ দিন পূর্বে গর্তের মাটিতে সার মিশাতে হবে । পানি নিষ্কাশনের জন্য দুই সারির মাঝখানে ৫০ সে:মি: নালা রাখতে হবে।
রোপণের সময়
চারা রোপণের জন্য সেচের সুবিধা থাকলে সেপ্টেম্বর- অক্টোবর (আশ্বিন) এবং জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি (মাঘ উপযুক্ত সময় । নচেৎ মৌসুমী বৃষ্টি শুরু হলে জ্যৈষ্ঠ মাস উত্তম। প্রতিটি গর্তে ৩টি করে চারা ২০ সে.মি. দূরত্বে ত্রিভূজাকারে রোপণ করতে হবে । চারা বিকালে রোপণ করাই ভালো। রোপণের পরপরই সেচ দেয়া ভালো । এরপর যতদিন না চারা লেগে উঠে তত দিন সেচ দেয়ার প্রতি যত্নবান হতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর সেচের প্রয়োজন হতে পারে।
সার প্রয়োগ পদ্ধতি: প্রতিটি পেঁপে গাছে নিম্নরূপ সার ব্যবহার করতে হবে
সারণি: পেঁপে চাষে সার প্রয়োগের পরিমাণ
পেঁপে চাষের জন্য গাছ প্রতি ১০ কেজি জৈব সার, ৪৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ৪৫০ গ্রাম এমপি ২৪০ গ্রাম জিপসাম, ৬ গ্রাম জিংক অক্সাইড বা ১৫ গ্রাম জিংক সালফেট এবং বারোক্স বা রোরিক অ্যাসিড ২৫ গ্রাম দেয়া প্রয়োজন । জমি তৈরির শেষ চাষের সময় গাছ প্রতি ৫ কেজি জৈব সার হিসেব করে সম্পূর্ণ জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে । বাকী গোবর বা জৈব সার এবং সম্পূর্ণটি এসপি, জিপসাম, জিংক অক্সাইড বা জিংক সালফেট ও বরিক অ্যাসিড বা বারাক্স ভিত্তি সার হিসেবে চারা রোপণের পূর্বে গর্তের উপরে ২৫ সে:মি: মাটির মধ্যে কোদাল দিয়ে মিশাতে হবে । চারা লাগানোর পর গাছে নতুন পাতা আসলে ইউরিয়া ও এমপি সার ৫০ গ্রাম করে প্রতি এক মাস অন্তর প্রয়োগ করতে হবে । গাছে ফুল আসলে এ মাত্রা দ্বিগুণ করা হয় । শেষ ফল সংগ্রহের এক মাস পূর্বেও সার প্রয়োগ করতে হবে। পচা গোবর, টিএসপি, জিপসাম, বারোক্স এবং জিংক সালফেট গর্ত তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হবে ।
রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা
পেঁপে খুবই স্পর্শকতার গাছ। রোপণ পরবর্তী নিম্নলিখিত পরিচর্যা গুলি অনুসরণ করলে কাঙ্ক্ষিত ফলন নিশ্চিত করা যায় ।
অতিরিক্ত গাছ অপসারণ
চারা রোপণের ৪-৫ মাস পর থেকেই গাছে ফুল আসা শুরু করে। ফুল দেখে কোনটি স্ত্রী, কোনটি পুরুষ গাছ চেনা যায় । ফুল আসার পর এ সময় প্রতি গর্তে লাগানো ৩টি চারার মধ্যে একটি করে সতেজ, সবল সুস্থ স্ত্রী গাছ রেখে আর সব গাছ সে স্ত্রী হাকে বা পুরুষ হাক উপড়ে তুলে ফেলতে হবে । তবে প্রতি ২০টি গাছের জন্য একটি করে পুরুষ গাছ রাখতে হবে যাতে পরাগায়ণে সুবিধা হয় । পরাগায়ন ছাড়া সব স্ত্রী ফুল ঝরে পড়ে যাবে, ফল ধরবে না ।
আগাছা পরিষ্কার
বাগান সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে । গাছের গোড়ায় মাটি নিড়ানি দিয়ে ঝুরঝুরে করে দিতে হবে । আগাছা পরিষ্কারের সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন কোন সময় গভীরভাবে গাছের মাটি খোড়া না হয় । কারণ পেঁপে গাছের শিকড় মাটির গভীরে যায় না ।
সেচ ও নিষ্কাশন
শুষ্ক মৌসুমে বা খরার সময় পানি সেচ দিলে পেঁপের ফলন বৃদ্ধি পায় । শীতকালেও গ্রাম্মকালে ২০-২৫ দিন পর পর সেচ দেয়া দরকার। প্রত্যেক বার সার দেয়ার পর সেচ দিতে হয় । পেঁপে জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না । লক্ষ রাখতে হবে যেন গাছের গোড়ায় পানি জমে না থাকে ।
ফল পাতলাকরণ
পেঁপে গাছের প্রতি পর্বে ফল আসে । অনেক ক্ষেত্রে প্রতি পর্বে একটির পরিবর্তে এক সাথে বেশ কটি ফল আসে এবং এগুলো যথাযথভাবে বাড়তে পারে না । এসব ক্ষেত্রে ছোট অবস্থাতেই প্রতিপর্বে দু-একটি ফল রেখে আর সব ফল তুলে বা ছিড়ে ফেলতে হয় । এতে ফলের আকার বড় হয় এবং গুণগত মান বৃদ্ধি পায় ।
পোকা মাকড় ও রোগ দমন
ফলের মাছি পোকা কচি পেঁপের গায়ে ডিম পাড়ে। ফলে পেঁপে পচে নষ্ট হয়। এক আউন্স ডিটরেক্স ৮০ ১২ কেজি পানিতে মিশিয়ে ৮ দিন পর পর স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায়
পেঁপের মোজাইক ভাইরাসজনিত রোগ
রোগের আক্রমণে পাতা কুঁকড়ে যায় । পাতায় সাদা হলদেটে দাগ দেখা যায়। ক্লোরপ্লাস্ট নষ্ট হয়ে পাতায় ছিট ছিট হলুদ মোজাইক দাগ পড়ে এবং গাছের বৃদ্ধি থেমে যায়। গাছ ফল ধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে । রোগের আক্রমণ দেখা মাত্র গাছ ধ্বংস করতে হবে। ১১.৫ মিমি: ডায়াজিনন ৫০ ইসি, ১২ কেজি পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করলে ভাইরাস বাহক কীটপতঙ্গ ধ্বংস করে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায় ।
গোড়া পচা: এ রোগে আক্রান্ত গাছের কাণ্ড মাটি সংলগ্ন স্থানে পচে গিয়ে গাছ মারা যায় ও সেখান থেকে দুর্গন্ধ বের হয় । মাটিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হলে এই রোগ হয়। মাটি সুনিষ্কাশিত রাখা রোগ ঠেকিয়ে রাখার প্রধান উপায় । প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসেবে ডাইথেন এম-৪৫ প্রয়োগ করা যেতে পারে ।
ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ
ফল ধরার ২ মাস পরে সবজি হিসেবে পেঁপে সগ্রহ করা যায় । অর্থাৎ চারা রোপণের ৬-৭ মাস পর কঁচা পেঁপে তালো যায় । তবে পেঁপে গাছের প্রথম ফল ৯-১০ মাসের মধ্যে পাওয়া যায় । পাকা ফলের জন্য চামড়া কিঞ্চিৎ হলুদ হলে সংগ্রহ করা ভালো । ফলের গায়ে আঁচড়া দিলে দুধের মত কষ বের হয় । ফলের ঐ দুগ্ধবত কষ পাতলা ও জলীয় ধারন করলে বুঝতে হবে যে পেঁপে পরিপুষ্ট হয়েছে। প্রতিটি ফল হতে দিয়ে আলাদা আলাদাভাবে পাড়া সবচেয়ে ভাল । এতে ফলে আঘাত লাগে না। সেংগৃহীত ফল ঠান্ডা স্থানে রাখলে ধীরে ধীরে পাকে । তবে ইথিলিন গ্যাসের সাহায্যে দ্রুত পাকানো যায় । কাচা বা পরিপুষ্ট ফল ৯° থেকে ১০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ও ৮০-৮৫ ভাগ আদ্রতায় ২ সপ্তাহ রাখা যায় । গাছের যথোপযুক্ত পরিচর্যা নেয়া হলে এক গাছ থেকে ২-৩ বছর পর্যন্ত ফল পাওয়া যায় । কিন্তু পেঁপে গাছ ৩ বছরের বেশি রাখলে লাভজনক হবে না ।
পেয়ারা চাষ
বৃক্ষ শ্রেণির ফলের মধ্যে যে গাছ হতে রোপণের পর ন্যূনতম সময়ের মধ্যে ফল পাওয়া যায় তা পেয়ারা । পেয়ারা এমন একটি ফল যার মধ্যে একাধিক গুণের বিরল সমন্বয় ঘটেছে যা খুব কম ফলেই লক্ষ করা যায় । এটি দ্রুত বর্ধনশীল এবং অপেক্ষাকৃত কম যত্নেই যে কোন স্থানে জন্মানো যায়। এটি অত্যন্ত ফলনশীল এবং পুষ্টি মান ও স্বাদের দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট ।
মাটি ও জমি নির্বাচন
পেয়ারা গাছ বেশ শক্ত। সব রকম মাটিতেই পেয়ারা জন্মাতে পারে। তবে হালকা বেলে দোঁআশ হতে ভারী এটেল মাটি পেয়ারা উৎপাদনের জন্য উত্তম । তবে পানি নিকাশের সুবিধাযুক্ত উর্বর গভীর পলি মাটিও পেয়ারা চাষের জন্য উত্তম । অল্প অন্ন ও অল্প ক্ষারযুক্ত মাটিতে পর্যাপ্ত রস থাকলে পেয়ারা ভালো হয় ।
পেয়ারা গাছ সাধারণত জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না । তবে পেয়ারা গাছ স্বল্প সময়ের জন্য জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে । কিন্তু তাতে ফল ধারণে অসুবিধা হয়। পেয়ার গাছ সাধারণত লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে না । এ ছাড়া স্যাঁতসেঁতে মাটিতে পেয়ারা ভালোভাবে জন্মাতে পারে না । মাটির পি এইচ ৪.৫ থেকে ৮.২ পর্যন্ত হলেও পেয়ারা আবাদ সফল হতে পারে। পেয়ারা গাছের শিকড় মাটির মাত্র ২০ সে.মি.-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ । পেয়ারা গাছ অগভীর মূল বিশিষ্ট হওয়ায় ৯০ সে:মি: গভীর মাটিতেও চাষ করা যায়। উঁচু জমি ও খোলামেলা রৌদ্রযুক্ত স্থান পেয়ারা চাষের জন্য উপযাগী । তবে সামান্য রোদ বা আংশিক ছায়াযুক্ত স্থানেও পেয়ারা ভালো ফলন দিতে পারে । অধিক আর্দ্র এবং আংশিক ছায়াযুক্ত স্থানে জন্মানো ফলের মিষ্টতা কম হয় । পেয়ারা বড় গাছে ৪৫ সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। তবে বেশি তাপমাত্রায় ফল ঝরে যায় আবার খুব শীতে গাছ মারা যায়। সমতল ও পাহাড়ি উভয় এলাকায়ই পেয়ারা ভালো জন্মাতে পারে ।
জমি ও গর্ত তৈরি
চারা লাগানোর কমপক্ষে এক মাস পূর্বে জমিতে ২-৩ বার লাঙ্গল দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। জমি আগাছামুক্ত ও সমতল করে নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় গর্ত খনন করতে হবে । বর্গাকার প্রণালিতে ৪-৫ মিটার দূরে দূরে ৫০×৫০×৫০ সে:মি: আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে। প্রতি গর্তে ১০ কেজি গোবর, ২০০ গ্রাম টিএসপি, ১০০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ২০০ গ্রাম মিউরেট অব পটাশ প্রয়োগ করতে হবে ।
চারা রোপণের সময়
জমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা থাকলে পেয়ারা গাছ এপ্রিল মে থেকে শুরু করে সেপ্টেম্বর (আশ্বিন কার্তিক - মাস পর্যন্ত অর্থাৎ বছরের যে কোন সময়ই লাগানো যায় । তবে পেয়ারা গাছ যে- জুলাই (জ্যৈষ্ঠ - শ্রাবণ) মাসে লাগানোই উত্তম । রোপণের পরবর্তীকালে সার প্রয়োগের জন্য আগস্ট- সেপ্টেম্বর মাস উত্তম ।
রোপণ পদ্ধতি
গর্ভের মাটি আলগা করে গর্তের মাঝখানে চারা বসায়ে চারদিকের মাটি ভালোভাবে চেপে দিতে হবে । চারা লাগানোর পর কাঠি দিয়ে চারা বেঁধে দিতে হবে, যাতে গাছ সোজা থাকে। পেয়ারা গাছ বর্গাকার, আয়তকার বা ত্রিভুজাকার পদ্ধতিতে লাগানো যায় । চারা রোপণের পর বৃষ্টি না হলে পানি দেয়া অব্যাহত রাখতে হবে । যতদিন পর্যন্ত চারা গাছ লেগে না উঠে তবে সাধারণত গাছ লেগে উঠতে প্রায় একমাস সময় লাগে। চারা রোপণের পর গোড়ায় যাতে পানি জমে না থাকে সে জন্য গোড়ার মাটি কিছুটা উঁচু করে দিতে হবে ।
সার প্রয়োগ
পেয়ারা ফসল থেকে উচ্চ ফলন প্রাপ্তি অব্যাহত রাখতে হলে নিয়মিত নিম্নরূপ হারে প্রতি গাছে সার প্রয়োগ করতে হবে ।
সারণিতে উলেখিত সার দুই কিস্তিতে দিতে হবে । বর্ষা শুরুর আগে বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম কিস্তিতে সম্পূর্ণ গোবর সার ও টিএসপি এবং অর্ধেক ইউরিয়া ও এমপি সার গাছের চারদিকে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে । তবে পাহাড়ের ঢালে ডিবলিং পদ্ধতিতে সার দেয়াই ভালো । দ্বিতীয় কিস্তি সার বর্ষা মৌসুমের শেষে ভা -আশ্বিনে দিতে হয় । এ সময় বাকি অর্ধেক ইউরিয়া ও এমপি সার দেয়া হয় । নির্ধারিত মাত্রায় যথা সময়ে সার প্রয়োগ করতে হবে ।
সারণি -১ এ বর্ণিত সার ছাড়াও কখনও কখনও জিংক বা সালফার বা মলিবডেনামের অভাব দেখা দিতে পারে । এগুলোর অভাবে গাছের পাতা ছোট হতে পারে, পাতার শিরার মধ্যবর্তী জায়গার সবুজ কমে যেতে পারে । পাতা ও ফলের সংখ্যা কম হতে পারে ইত্যাদি । এক্ষেত্রে নির্ধারিত মাত্রায় জিংক সালফেট, জিপসাম বা বরিক অ্যাসিড প্রয়োগ করা যেতে পারে ।
রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা
যদিও পেয়ারা গাছ বেশ খরা সহ্য করতে পারে তথাপি আশানুরূপ ফলন পেতে হলে শুষ্ক মৌসুমে দোআশ মাটিতে ১৫ দিন পরপর সেচ দিতে হবে এবং শীতকালে ৩ থেকে ৭ দিন অন্তর অন্তর সেচ দেয়ার প্রয়োজন হবে । তবে ভারী মাটিতে ১৫-২০ দিন অন্তর সেচের প্রয়াজন হয় । পেয়ারা বাগানে গাছের সারির মাঝখান দিয়ে হালকা চাষ দিয়ে আগাছা ও ঝরাপাতা মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে । এতে মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পাবে ।
সাথী ফসল
পেয়ারা গাছ বড় হয়ে পূর্ণ ফলবান হতে ৭-৮ বছর সময় লাগে । জমির লাভজনক ব্যবহারের জন্য এ সময় পেয়ারা বাগানে বিভিন্ন শাক-সবজি, কন্দাল জাতীয় ফসল, ডালশস্য ইত্যাদি চাষ করা যায় । তবে সাথী বা আন্তঃফসল করা হলে তার জন্য অতিরিক্ত সার দেয়ার প্রয়োজন হবে ।
শাখা বিন্যাস ও ছাঁটাইকরণ
গাছ শাখা প্রশাখা ছাড়ার আগে প্রধান কাণ্ড অন্তত এক মিটার লম্বা হতে দিতে হয় । এরপর প্রধান কাণ্ডটির মাথা কেটে দিলে মাথার চারদিকে অনেক কুঁড়ি গজায় । এগুলো থেকে চারটি কুঁড়ি রেখে বাকিগুলো ভেঙে দিয়ে শুধু এ চারটিকে বাড়তে দিতে হবে ।
কুঁড়ি চারটি যেন খাড়াভাবে উঠতে না পারে সেজন্য ভার দিয়ে বা রশি বেধে মাটির সমান্তরাল করে দিতে হবে অথবা এই চারটি কুঁড়ি শাখায় রূপান্তর হয়ে যেন সোজা উপরের দিকে না উঠে চারদিকে প্রসারিত হয় সেজন্য অনেক সময় খুঁটি পুঁতে রশি দিয়ে বেধে দিতে হবে। এ শাখাগুলো যখন ৫০ সে.মি. বা এক মিটার লম্বা হবে তখন সে শাখার আবার মাথা কেটে দিতে হবে। এভাবে আর একবার শাখার মাথা কেটে দিয়ে আবার ২টি করে কুঁড়ি বা শাখা রেখে দিতে হবে। এভাবে ১৬টি শাখা হলে আর কাটার প্রয়োজন নাই। তবে গাছের গোড়া থেকে শাখা গজালে তা কেটে দিতে হবে। গাছে মরা ও রোগাক্রান্ত শাখা থাকলে তা কেটে দূরে নিয়ে নষ্ট করে দিতে হবে।
ফলন্ত গাছের পরিচর্যা
পেয়ারা গাছের শাখার অগ্রভাগে ফুল আসে না। এমনকি পুরাতন শাখায়ও ফুল আসে না। সাধারণত নতুন মুকুল বা বিটপের পত্রকক্ষে ফুল হয়। পেয়ারা গাছে বছরে দুবার ফুল আসে। মার্চ-এপ্রিল মাসে প্রথম বার এবং সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে দ্বিতীয়বার ফুল আসে। ফুলের কুঁড়ি বা মুকুল আসা থেকে ফুল বের হওয়া পর্যন্ত ২০-২২ দিন সময় লাগে। আবার ফুল হতে ফল পাড়ার উপযুক্ত হতে ১৪০-১৬০ দিন সময় লাগে । পেয়ারা গাছে বসন্তকালে এবং বর্ষার প্রারম্ভে ফুল হয়। বর্ষার সময়ের ফল বেশি মিষ্টি হয় না। তাই এ সমস্ত ফল বেশি রাখতে না চাইলে ফুল ভেঙে দিতে হবে। বর্ষার পূর্বের ফুল ভেঙে দিলে বর্ষার পরবর্তীতে বেশি করে ফল ধরে।
মার্চ মাস থেকে সেচ বন্ধ করে গাছের গোড়া হতে হালকাভাবে কিছুটা মাটি সরিয়ে দিয়ে মে মাসে আবার মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এ মাটি দেয়ার সময় জৈব সার প্রয়োগ করা হলে বর্ষায় ফুল আসবে। এ ফুল হতে যে ফল হবে তা জানুয়ারি মাসে পরিপুষ্ট হবে। এ সমস্ত ফলের আকৃতি ও গুণাগুণ ভালো হয় ।
ফল ছাঁটাই: পেয়ারা গাছ প্রতি বছর প্রচুর সংখ্যক ফল দিয়ে থাকে। গাছের পক্ষে সব ফল ধারণ করা সম্ভব হয় না। তাই মার্বেল আকৃতি হলেই ঘন সন্নিবিশিষ্ট কিছু ফল ছাঁটাই করতে হবে ।
পোকা মাকড় ও রোগবালাই দমন
পোকামাকড় দমন: পেয়ারা গাছে মিলিবাগের আক্রমণ সাধারণত বেশি দেখা যায়। পেয়ারা গাছের পাতা ও ফলে এ পোকা দেখা যায়। এগুলো এক জায়গায় একটি লাইনে অনেকগুলো থাকে। নড়াচড়া করে না। এদের গা তুলোট আবরণযুক্ত। এ পোকাগুলো রস চুষে খেয়ে কচি কাণ্ড, পাতা ও ফলের ক্ষতি করে। মিলিবাগ আক্রান্ত পাতা, কচি কাণ্ড এবং ফল থেকে মিলিবাগ সংগ্রহ করে পুড়িয়ে মারতে হবে। অথবা প্রতি লিটার পানির সাথে নগস বা ডেনকাভাপন ১০০ ইসি ২.০ মি.লি. অথবা ডাইমেক্রন ১০০ এসসিডবিউ, ১.০ মি.লি. হারে মিশিয়ে ভালোভাবে স্প্রে করে মিলিবাগ দমন করা সম্ভব।
রোগ দমন: পেয়ারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে রোগ একটি সমস্যা। বহুধরনের রোগ পেয়ারার ক্ষতি সাধন করতে পারে। নিম্নে ক্ষতিকর কয়েকটি রোগের বর্ণনা ও প্রতিকার ব্যবস্থা দেয়া হলো।
উইন্ট রোগ: এর আক্রমণে পাতা শুকিয়ে যায় এবং ছোট ডালপালাও শুকিয়ে যেতে থাকে। এমনকি হঠাৎ একদিন গাছটি মরে যায়। এ রোগ দমনের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। তবে বাগানের সঠিক পরিচর্যা এ রোগ দমনে সাহায্য করে লীফ স্পট রোগ: এর আক্রমণে পাতা ও ফলে ছোট ছোট বাদামি রঙের দাগ দেখা যায়। এ দাগ গুলোর মাঝখানে কাল দাগ হয়। এ রোগ গাছের ফলের যথেষ্ট ক্ষতি করে থাকে। যে কোন কপার ছত্রাক নাশক ১০-১৫ দিন পর পর ছিটিয়ে এ রোগ দমন করা যায় ।
ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ
সারা বছর ফল ফলানোর পর সঠিক সময়ে ও নিয়মে ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। সুষ্ঠু সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা বাণিজ্যিক ফল উৎপাদনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোৎকৃষ্ট শ্বাস পেতে হলে পরিপক্কতার সঠিক পর্যায়ে ফল সংগ্রহ করতে হবে। অতিপত্ব বা অপক্ব ফল কোনটাই ভাল নয়। পেয়ারা ফল পাকার প্রক্রিয়া অতিদ্রুত । এ জন্য ফল পাকার মৌসুমে প্রতিদিনই ফল সংগ্রহ করতে হয়। ফল পুষ্ট হলে ফলের রং সবুজ থেকে ধীরে ধীরে ফিকে সবুজ বা হলুদাভা হতে থাকে । দূরে পাঠাতে হলে একটু ডার্সা বা কঁচা অবস্থায় ফল পাড়তে হয় । ফল পাড়ার সময় বোটায় ২-১ টা পাতাসহ কেটে নেয়া ভালো। পেয়ারা পাড়ার পর সাধারণত ২-৩ দিনের বেশি রাখা যায় না। পেয়ারা পাকার পূর্বে পুষ্ট অবস্থায় পেড়ে কঁচা পাতা দিয়ে ঢেকে ছায়াময় ঠান্ডা স্থানে এক সপ্তাহ পর্যন্ত ভালোভাবে রাখা যায়। পুষ্ট ফলকে ৮৭ হতে ১০° সেলসিয়াসের তাপমাত্রায় এবং ৮৫-৯০ শতাংশ আপেক্ষিক আর্দ্রতায় একমাস পর্যন্ত রাখা যায়। পেয়ারা থেকে জ্যাম, জেলী তৈরি করে সংরক্ষণ করা যায় ।
লেবু চাষ
বিশ্বের অবউষ্ণ অঞ্চলে, বিষুবরেখার ৪০° উত্তর এবং ৪০° দক্ষিণ অক্ষাংশের যে সমস্ত দেশে সুনির্দিষ্ট শীতকাল রয়েছে যা গাছকে সুপ্ত অবস্থায় যেতে সাহায্য করে সে সমস্ত দেশে লেবুজাতীয় ফলের চাষ সবচেয়ে ভালো হয় । বাংলাদেশের জলবায়ুতে কমলা, জাম্বুরা, লেবু, কাগজী লেবু ইত্যাদি জনে । কাগজি লেবু শুষ্ক অঞ্চলে যেমন- কুষ্টিয়া, পাবনা ও রাজশাহী অঞ্চলে ভালো জন্মে । অথচ বীজহীন লেবু সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ভালো জন্মে । অধিক বৃষ্টিপাত সম্পন্ন ঢালু জমিতে যেমন- বৃহত্তর সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম কমলা উৎপাদনের জন্য অধিক উপযোগী । জাম্বুরা উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে ভালো জন্মে । পঞ্চগড় জেলায় যেখানে বৃষ্টিপাত বেশি তিতু পানি জমে থাকে না এবং মাটি কিছুটা এসিডিক আজকাল কমলা লেবু চাষের প্রসার ঘটছে।
মাটি ও জমি নির্বাচন
বেলে, বেলে-দোআশ ও লাল পাহাড়ী মাটিতে লেবুর চাষ করা যায়। মাটির উপরের দিকের স্তর দো আশ ও নিচের দিকের তর এঁটেল মাটি হলে লেবু চাষের জন্য উত্তম। লেবু অম্ল মাটি পছন্দ করে । লবণাক্ত ও ক্ষারীয় মাটিতে লেবু ভালো হয় না। স্যাঁতস্যাঁতে মাটিতে লেবু ভালো হয় না। জমি উঁচু ও পানি নিকাশের ভালো সুবিধাযুক্ত হওয়া আবশ্যক! কাদা ও এটেল মাটিতে গাছ ভাল হলেও মাধ্যমিক পরিচর্যার অসুবিধা হয় । তবে কাদা ও এঁটেল মাটিতে নিকাশ ব্যবস্থা থাকলে বিশেষ পরিচর্যার মাধ্যমে লেবু জন্মানো যায় ।
জমি ও গর্ত তৈরি
বাংলাদেশের সমতল এলাকায় বা সমভূমিতে মে-জুন মাসে ধৈঞ্চা বা শন পাটের বীজ বপন করতে হবে। এ সবুজ সারের বীজ বপনের ৫-৬ সপ্তাহ পরে গাছ গুলোকে চাষ দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলে সবুজ সার তৈরি হয় । সবুজ সার করে লেবুর চাষ করা হলে সেখানে লেবু ভাল হয় । এদেশের পার্বত্য অঞ্চলে লেবুর চাষ করলে সিড়ি বাঁধ দিয়ে জমির ক্ষয় রোধের ব্যবস্থা করতে হয় । বাঁধগুলো চালে আড়াআড়ি ভাবে তৈরি হয় ।
এ সিঁড়ি বাধের ভিতরের দিকে পাহাড়ের ঢালে ঘুরে ঘুরে গর্ত খনন করে গর্তে সার মিশিয়ে চারা রোপণ করতে হয় । চারা রোপণের ২-৩ সপ্তাহ আগে নির্দিষ্ট দূরত্বে ৭৫×৭৫× ৭৫ সে.মি. আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে। গর্তের উপরের মাটির সাথে জৈব ও আর্বজনা পচা সার মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে । গর্ত ভরাট করার পর এর উপরের ২০-২৫ সে:মি: মাটির সাথে ২৫০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫০ গ্রাম এমপি সার হালকা কোপ দিয়ে মিশিয়ে দিতে হবে ।
ছক: গর্ত প্রতি সার প্রয়োগের পরিমাণ
| ক্রমিক নং | সারের নাম | গর্ত প্রতি সারের পরিমাণ |
| ১ | গোবর/আবর্জনা পচা সার | ১৫-২০ কেজি |
| ২ | পচা খৈল | ৩০০ গ্রাম |
| ৩ | হাড়ের গুড়া | ৫০০ গ্রাম |
| ৫ | ছাই | ২ কেজি |
| ৫ | টিএসপি | ২৫০ গ্রাম |
| ৬ | এমপি | ২৫০ গ্রাম |
চারা রোপণের দূরত্বঃ লেবু ও কাগজী লেবু ৪×৪ মিটার দূরত্বে রোপণ করা যায়। কিন্তু কমলা ও জাম্বুরা ৬×৬ মিটার দূরত্বে রোপণ করাই উত্তম ।
চারা রোপণের সময় ও পদ্ধতি
বর্ষা ঋতুর প্রারম্ভে এপ্রিল মে মাসে চারা রোপণ করা উত্তম । তবে সেচ সুবিধা থাকলে সেপ্টেম্বর - অক্টোবর (ভাদ্র - আশ্বিন) মাসেও রোপণ করা যায়। এক বছর বয়সের কলমের চারা গর্তের ঠিক মাঝখানে রোপণ করতে হবে । চারা গাছ সোজা ভাবে বসিয়ে গাছের গোড়ায় মাটি ভালোভাবে চেপে দিয়ে হালকা সেচ দিতে হবে । তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন গর্তে গাছের গোড়ায় পানি দাড়ানো না থাকে । প্রত্যেক গাছে একটি করে শক্ত কাঠি দিয়ে বেধে দেওয়া দরকার। আম, কাঁঠাল, নারিকেল ইত্যাদি স্থায়ী বাগানে পঞ্চমস্থানে বা ষড়ভুজী পদ্ধতির মাঝখানে পুরক গাছ হিসাবে ও লেবু গাছ লাগানো যায় ।
সার প্রয়োগ
লেবু গাছে যে পরিমাণ সার দিতে হবে তা সারণি- ২ তে দেখানো হলো
সারণি- ২ বিভিন্ন বয়সের লেবু জাতীয় ফল গাছে সারের পরিমাণ
| ক্রমিক নং | সারের নাম | ১-২ বছর বয়স | ৩-৫ বছর বয়স | ৬ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়স |
| ১ | গোবর বা আবর্জনা (কেজি) | ১৫ | ২০ | ২৫-৪০ |
| ২ | ইউরিয়া (গ্রাম) | ২০০ | ৪০০ | ৫০০ |
| ৩ | টিএসপি (গ্রাম) | ২০০ | ৩০০ | ৪০০ |
| ৪ | এমপি(গ্রাম) | ২০০ | ৩০০ | ৪০০ |
বর্ষা মৌসুমের শুরুতে জ্যৈষ্ঠ (মে) মাসে সম্পূর্ণ গোবর সার একবারে প্রয়োগ করতে হবে । অন্যান্য সার তিন কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ (Top dressing) পদ্ধতিতে আশ্বিন (সেপ্টেম্বর), মাঘ (ফেব্রুয়ারি) এবং বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ (মে) মাসে
প্রয়োগ করতে হবে । পাহাড়ের ঢালে গোবর সার গাছের চারদিকে মাটির সাথে কোদাল দিয়ে ভালোভাবে মিশে দিতে হবে । এরপর আগাছা বা আর্বজনা দিয়ে ভালো করে ঢেকে দিতে হবে। যাতে বৃষ্টি হলে ধুয়ে না যায় । অন্যান্ন সার ড্রিবলিং (Dribbling) পদ্ধতিতে দিলেই চলবে
গাছ রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা
সারের উপরি প্রয়োগ চারা রোপণের ৩-৪ মাস পর গাছ প্রতি ২০০ গ্রাম ইউরিয়া, ২৫০ গ্রাম করে টিএসপি ও এমপি সার দিতে হবে। চারার ৯ থেকে ১০ মাস বয়সে প্রয়োজনে অতিরিক্ত ২০০ গ্রাম ইউরিয়া সার দিতে হবে । গাছের বয়স বাড়ার সাথে সাথে সারের পরিমান বাড়িয়ে দিতে হবে ।
সেচ: মাটি যদি শুকিয়ে যায় কিংবা মাটিতে রস না থাকে এবং পাতা শুকিয়ে যায় তাহলে অবশ্যই সেচ দরকার । শীত কালে ফুল আসা থেকে বর্ষা শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রয়োজনমত সেচ দিতে হবে। এতে গাছের বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে । ফল আকারে বড় হয় এবং ফলের গুণাগুণ বৃদ্ধি পায় । বর্ষাকালে অতিরিক্ত পানি হলে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে ।
অঙ্গ ছাঁটাই: হেঁটে গাছকে সঠিকভাবে বাড়তে দিয়ে সুন্দর ও শক্ত কাঠামো তৈরির জন্য অবাঞ্ছিত শাখা প্রশাখা ছাঁটাই করে দিতে হবে । তাছাড়া সব বয়সের গাছই বর্ষার পর ও আগে বিশেষভাবে ফল আহরণের পরপরই মরা ও রোগাক্রান্ত ডালপালা ছাঁটাই করে দিতে হবে ।
ফল ছাঁটাই: গাছে অতিরিক্ত ফল আসলে এগুলোর মধ্য হতে কিছু ফল ছাঁটাই করে দেয়া ভালো। এতে ফল বড় হয়, গাছ নিয়মিত ফল দেয় এই গাছ দীর্ঘজীবী হয় ।
পোকামাকড় ও রোগ দমন
পোকামাকড় ও পাতা কুন্দী (Leaf miner) পোকা ও লেবু গাছের একটি মারাত্মক পোকা। এ পোকার শুককীট চারা গাছের এমনকি বড় গাছের নরম পাতা, ডাল তাড়াতাড়ি খেয়ে গাছকে প্রায় পাতা শূণ্য করে ফেলে । আক্রান্ত গাছে রগর/রক্সিয়ন ৪০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ মি:লি: ঔষধ মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে । ফলের মাছি পোকা লেবুর ভয়ানক শত্রু । বিষটোপ ব্যবহার করে পূর্ণাঙ্গ মাছি পোকা দমন করা যায় ।
রোগ দমন: লেবু জাতীয় গাছের ডাইব্যাক একটি মারাত্মক রোগ। এই রোগের আক্রমণে গাছ শীর্ষভাগ হতে মারা যেতে থাকে এবং পরবর্তীতে সম্পূর্ণ গাছ মারা যায়। রোগ দেখা মাত্র ১০-১২ দিন পরপর বার্দে মিশ্রণ স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যায় । গামোসিস রোগের আক্রমণে বাকল ফেটে রস পড়তে থাকে এবং আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায় । এই রোগ দেখামাত্র আক্রান্ত স্থান চেঁছে দিয়ে বার্সে পেস্ট লাগাতে হবে ।
ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ
লেবু ও কাগজী লেবু গাছে জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি মাসে ফুল ও ফল আসে এবং জুন- জুলাই মাসে এগুলো সংগ্রহ করা যায় । জাম্বুরাতে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে ফুল আসে এবং সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে ফল আহরন করা হয় । কমলার গাছে মার্চে ফুল আসে এবং নভেম্বর - ডিসেম্বর ফল পাকে ।
ফল পুস্ট হলে রং বদলাতে শুরু করে। ফল যতই পুস্ট হবে চামড়ার উজ্জ্বলতা ততই বৃদ্ধি পাবে এবং চামড়া টানটান হবে । পুষ্ট লেবু কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত টাটকা থাকে। সংগ্রহের পর ফল পরিষ্কার করে বিক্রয়ের জন্য ছোট বড় গ্রেডিং করতে হয় । পরিণত ফল ১১° সেলসিয়াস তাপমাতায় ও ৮০- ৯০ শতাংশ আপেক্ষিক আর্দ্রতায় হিমাগারে দুমাস পর্যন্ত তাজা অবস্থায় রাখা যায় ।
ফলন ও কাগজী লেবু গাছ প্রতি ২০০০ - ৪০০০টি
লেবু/পাতি লেবু ও ১০০-১০০০টি
জাম্বুরা : ১০০-৩০০টি, কমলা ও ১০০-৫০০ টি
অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
১। অবৃক্ষ জাতীয় ফলের মধ্যে প্রধান প্রধান ফল কোনটি ?
২। চারা রোপণের কত দিন পূর্বে গর্ত খনন ও সার মিশ্রিত করে ভরাট করতে হয় ?
৩। পেঁপে চারা রোপণের কত দিন পর ফুল ও ফল আসে ?
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
১। কলা গাছের সাকার সম্পর্কে লেখ।
২। আনারসের কয় ধরনের সাকার পাওয়া যায় লেখ ।
৩। পেঁপে গাছে সারের উপরি প্রয়োগ সম্পর্কে লেখ ।
৪ । পেয়ারার চারা রোপণের দূরত্ব ও সময় সম্পর্কে লেখ ।
৫। পেঁপের জাতের নাম লিপিবদ্ধ কর।
৬ । কলার চারা রোপণ পদ্ধতি লেখ ।
৭ । কলার চারা শনাক্তকরণ পদ্ধতি লেখ।
৮। কলার পানামা রোগের কারণ ও লক্ষণ লেখ ।
৯ । পেয়ারার ক্যাংকার রোগের কারণ ও দমন পদ্ধতি লেখ।
রচনামূলক প্রশ্ন
১। কলা চাষের জন্য চারা নির্বাচন, চারা প্রস্তুতকরণ, চারা রোপণ, ও অন্তবর্তী পরিচর্যা সম্পর্কে লেখ ।
২ । আনারসের জন্য জমি ও মাটি নির্বাচন, চারা রোপণের দূরত্ব, চারা রোপণ পদ্দতি ও রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা সম্পর্কে লেখ ।
৩। পেঁপে চাষের জন্য জমি তৈরি, গর্ত খনন, চারা রোপণ কৌশল, চারা রোপণের দূরত্ব ও রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা সম্পর্কে লেখ ।
৪ । পেয়ারা চাষের জন্য মাটি ও জমি নির্বাচন, গাছের শাখা বিন্যাসের জন্য ছাঁটাই পদ্ধতি ও রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা সম্পর্কে লেখ ।
৫ । আনারস, কলা, পেঁপে ও পেয়ারার আহরণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি লেখ ।
৬। পেঁপের পোকামাকড় ও রোগ দমন সম্পর্কে আলোচনা কর ।
৭ । টীকা লেখ: ক) পানি চারা খ) আনারসের সাকার
প্রাসঙ্গিক তথ্য
বাংলাদেশে উৎপাদিত ফলের প্রচলন ও প্রাপ্যতার ভিত্তিতে ফলকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায় । যেমন-
(ক) প্রধান প্রধান ফল, (খ) অ-প্রধান ফল, (গ) বাংলাদেশের উপযোগী বিদেশি ফল ।
(ক) প্রধান প্রধান ফল: আম, কলা, পেঁপে, আনারস, লিচু, নারিকেল, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, আতা, শরীফা, তরমুজ, সফেদা, বেল, জাম, জামবুরা, কমলালেবু ইত্যাদি ।
(খ) অ-প্রধান ফল: আঙ্গুর, তাল, খেজুর, চালতা, আমড়া, তেঁতুল, আমলকি, জামরুল, করমচা, গোলাপ জাম, কমলালেবু, দেওফল, গাব, কামরাঙ্গা, জলপাই, ডুমুর, লটকন, ডালিম, চুকুর, তুতফল, বেতফল, ডেউয়া, পানিফল, বিলম্বী, সুপারি, অরবরই ইত্যাদি ।
(গ) বাংলাদেশের উপযোগী বিদেশি ফল: এ্যাভাকোডো, ফলসা, ল্যাংসাট, ট্রপিক্যালআপেল, স্টার ফুট, স্ট্রবেরি, রামবুটান, ডুরিয়ান, সালাক, ড্রাগন ফ্রুট ইত্যাদি ।
ছক-১
ক্রমিক নং | প্রাপ্যতার ভিত্তিতে ফলের ভাগ | ফলের নাম ও মোট সংখ্যা |
| ১ | প্রধান প্রধান ফল | ১৬ |
| ২ | অপ্রধান ফল | ২৭ |
| ৩ | বিদেশি ফল | ৯ |
সর্বমোট: | ৫২ |
আবার ফলগাছের জীবনকাল ও ফল দেয়ার সময় কালের ভিত্তিতে ফলকে তিনভাগে ভাগ করা যায় ।
যেমন - ১ । দীর্ঘমেয়াদি ২। মধ্যম মেয়াদি ৩। স্বল্প মেয়াদি ।
১ । দীর্ঘ মেয়াদি-আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল, লিচু, বেল, তেঁতুল, কামরাঙ্গা, আমড়া ইত্যাদি ।
২ । মধ্যম মেয়াদি-পেয়ারা, জামবুরা, কুল, সফেদা, আতা, শরীফা, কমলা লেবু, জামরুল, জলপাই, অরবরই, করমচা, আমলকি, এভাকোডো, লটকন, ডালিম ইত্যাদি ।
৩ । স্বল্প মেয়াদি-কলা, পেঁপে, আনারস, তরমুজ, চুকুর ইত্যাদি ।
ছক-২
ক্রমিক নং | ফল গাছের জীবন কালের ভিত্তিতে ফলের ভাগ | ফলের নাম ও মোট সংখ্যা |
| ১ | দীর্ঘ মেয়াদি ফল | |
| ২ | মধ্যম মেয়াদি ফল | |
| ৩ | স্বল্প মেয়াদি ফল | |
সর্বমোট: |
ছক-৩
ক্রমিক নং | ফলের মৌসুম | ফলের নাম ও মোট সংখ্যা |
| ১ | গ্রীষ্ম ও বর্ষা মৌসুমের ফল | |
| ২ | শীত মৌসুমের ফল | |
| ৩ | সারা বছরের ফল | |
সর্বমোট: |
প্রয়োজনীয় উপকরণ
(১) বিভিন্ন ধরনের ফল ।
(২) প্রাসঙ্গিক তথ্য মোতাবেক ফলভিত্তিক সংখ্যা নিরূপণের তালিকা/ছক ।
(৩) চিত্রসহ ফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণযুক্ত পুস্তিকা ।
(৪) কাগজ, কলম, কেল, রাবার, ক্যালকুলেটর ইত্যাদি
কাজের ধাপ
১। ফল শনাক্তকরণের জন্য ফলের বাগানে বা বাজারে যেতে হবে ।
২ । ফলের চিত্র সংবলিত তালিকার সাথে মিলিয়ে শনাক্ত করতে হবে ।
৩ । ছক মোতাবেক ফলের নাম লিখতে হবে।
৪ । বিভিন্ন মৌসুমে বাগানে বা বাজারে গিয়ে ছক মোতাবেক কোন কোন ধরনের ফল পাওয়া যায় তা লিখতে হবে এবং সংখ্যা বের করতে হবে ।
৫ । পূরণকৃত ছক থেকে কোন কোন ফলের উৎপাদন বেশি বা বাজারে কোন ফল বেশি পাওয়া যায় তা নির্ধারণ করা যায়।
৬ । ফলের শতকরা হার নিরূপণ করে ফলের অবস্থান নির্ণয় করা যাবে ।
প্রাসঙ্গিক তথ্য
ফল বাগানের জন্য জমির উপযুক্ততা বিবেচনা করতে হবে । কেননা কোন কোন ফল উঁচু জমি এবং কোন কোন নিচু জমি পছন্দ করে । আবার কোন কোন ফল শুষ্ক আবহাওয়া এবং কোন কোন ফল আর্দ্র আবহাওয়া পছন্দ করে । এছাড়া অনেক ফলের জন্য মাটির অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব বিশেষ উপযোগী । তাই ফন্তু বাগানের জন্য এ সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে ফল চাষের জন্য সুপারিশ করা যাবে ।
তথ্যভিত্তিক উপকরণ
(১) জমির অবস্থানের তথ্য ও যেমন জমির প্রকৃতি (উঁচু বা নিচু বা ব্যবসায়িকভাবে বাগান স্থাপন উপযোগী হবে কিনা, বাগানের স্থানে আলো বাতাস খোলামেলাভাবে লাগে কিনা, রাস্তাঘাটের সুবিধাদি বিদ্যমান অথবা একেবারেই নেই প্রক্রিয়াধীন)
(২) আর্থ সামাজিক তথ্য ও ঋণ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা, জমির দাম, শ্রমিক সুবিধা, সামাজিক অবস্থা, মানুষের রুচি ও চাহিদা, বাড়ির আঙ্গিনা বা বাঁধের ধারে বাগান করার জন্য জমি প্রাপ্তি ।
(৩) কারিগরি তথ্য ও ফল গাছের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উপযোগী আবহাওয়া, মাটির বুনট, মাটির গুণাগুণ, পানির উৎস, বীজ/চারা কলম প্রান্তির সুবিধা, সেচ সুবিধা ও সেচ যন্ত্রপাতি, সার, বীজ, কীটনাশকের সহজলভ্যতা ।
কাজের ধাপ
(১) উঁচু জমিতে বৃষ্টিপাত বেশি হলেও পানি জমার সম্ভাবনা থাকে না । তাই ফল গাছের জন্য উঁচু জমি চিহ্নিত করে কাগজে লিপিবদ্ধ করতে হবে।
(২) নিচু জমি এবং বৃষ্টির পানি দাঁড়ায় এমন স্থানে যে সকল গাছ দাঁড়ানো পানি সহ্য করতে পারে না সেগুলো লাগানো যাবে না ।
(৩) ভূ-গর্ভস্থ পানিতল কাছে হলেও যে সকল গাছ দাঁড়ানো পানি সহ্য করতে পারে না সে সমতু গাছ লাগানো যাবে না । কেননা সেখানে অল্প বৃষ্টিতেই পানিতল উপরে উঠে আসতে পারে ।
(৪) অধিকাংশ ফল গাছই খোলামেলা আলো বাতাস ও সূর্যালোক না পেলে ঠিকমত ফল দিতে পারে না । তাই সূর্যালোক পড়ে এবং আলো বাতাস লাগে তা দিনের বেলায় সূর্য উঠার পরে পর্যবেক্ষণ করে চিহ্নিত করতে হবে । এরপর কাগজে এলাকার মাপ লিখে নিতে হবে এবং মাপে কাঠি পুঁতে চিহ্নিত করতে হবে।
(৫) রাস্তাঘাটের ম্যাপ নিতে হবে, যা ফল উৎপাদনকালে সম্ভাব্য স্বল্প সময়ে ভালো রাস্তা দিয়ে যোগাযোগের পরিকল্পনা প্রণয়নে সুবিধা হবে। এমনকি নার্সারি হতে চারা কলম আনয়ন করাও সহজ হবে ।
(৬) সেচের সুবিধা আছে, জমির দাম কম, কাজ করার জন্য শ্রমিক পাওয়া যাবে, বাগানের ফল চুরি হবে না বা গাছ পালা নষ্ট হবে না, উৎপাদিত ফল বিক্রয় করা যাবে এমন বিষয়গুলো জরিপ করে চিহ্নিত করতে হবে ও নিশ্চিত হতে হবে ।
(৭) ইটের ভাটা বা ধোয়া নির্গত হয় এমন কারখানার কাছে ফলের বাগান করা যাবেনা ।
(৮) বর্ষায় পাবিত হয় এমন স্থান বাগানের জন্য নির্বাচন করা যাবে না। পরবর্তীতে বাগান স্থাপনের জন্য কারিগরি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। যেমন-
(ক) মাটি এঁটেল, বেলে বা বেলে দোঁয়াশ তা জেনে লিপিবদ্ধ করতে হবে ।
(খ) মাটি কাঁকর যুক্ত, মাটিতে পানি প্রবেশ ক্ষমতা, মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি জানতে হবে ।
(গ) মাটির জৈব পদার্থ ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান সম্পর্কে জানতে হবে ।
(ঘ) মাটির অম্লমান বা ক্ষারমান জেনে এলাকা চিহ্নিত করতে হবে ।
এরপর বিভিন্ন ফল চাষের বর্ণনা দেখে জমির ধান ও মাটির অবস্থা জেনে ফল গাছ নির্বাচন করে লাগানো উচিত হবে । তাতে লাভজনকভাবে ফল চাষ বা ফল বাগান করা সম্ভব হবে।
ছক: ফল বাগানের জন্য স্থান নির্বাচনী জরিপ ফরম ।
বাগানের জন্য প্রধান প্রধান বিবেচ্য বিষয় | নির্বাচিত বিষয় |
ফুল গাছের পছন্দনীয়: (ক) জমি-উঁচুনিচু (খ) জমি খোলামেলা/ছায়াযুক্ত /অন্ধকারভাব (গ) মাটির অমত্ব ক্ষারত্ব । (ঘ) মাটি এঁটেল/বেলেদোঁয়াশ পলি দোঁয়াশ/দোঁয়াশ/বেলে কাকরময় যোগাযোগ : (ক) রাস্তাঘাট--আছে/নেই (খ) যানবাহন-গ্রামীণ/আধুনিক (গ) সেচ সুবিধা আছে/নেই (ঘ) পানিতল-কাছে/গভীর অন্যান্য: (ক) বাজার ব্যবস্থা আছেনেই ( খ) শ্রমিক প্রাপ্তির সুবিধা আছে/নেই (গ) জমির মূল্য-বেশি/কম (ঘ) উপকরণ প্রাপ্তি-সহজ কঠিন (ঙ) আশেপাশে কলকারখানা-আছে নাই । (চ) অন্য কোন বিবেচ্য বিষয় (যদি থাকে) |
প্রাসঙ্গিক তথ্য
গাছের প্রায়াজনীয় খাবার সরবরাহ এবং শিকড়ের বৃদ্ধির জন্য গাছ রোপণের আগে গর্ত করা একান্ত প্ৰায়াজন । এক এক গাছের জন্য এক এক পরিমাণ দূরত্বে ভিন্ন ভিন্ন আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে । সাধারণত কোন গাছের জন্য কি আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে তা নিম্নোক্ত বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল । যথা-
(ক) গাছের আকৃতি
(খ) শিকড়ের গভীরতা
(গ) শিকড়ের বিস্তৃতি
(ঘ) চাষের মেয়াদ কাল
(ঙ) গাছের খাবারের চাহিদা ইত্যাদির উপর
উপকরণ ও যন্ত্রপাতি
১। কোদাল ২। শাবল/খন্তা ৩ । ঝুড়ি ৪ । মাপযন্ত্র ও মাপের ফিতা ৫। বাশেঁর কাঠি ৬। দড়ি/সুতলি ৭। পলিথিন সিট ৮ । কীটনাশক ও জীবাণুনাশক ঔষধ।
কাজের ধাপ
১। গর্ত খননের পূর্বে জমি ভালোভাবে চাষ দিয়ে সমতল করে আগাছা পরিষ্কার করে নিতে হবে ।
২। জমিতে গর্ত করার আগে চারা রোপণের নকশা মোতাবেক ফিতা বা কাঠির সাহায্যে মাপ দিতে হবে। মাপ দিয়ে নির্ধারিত দূরত্বে খুঁটি পুঁতে চারা রোপণের স্থান চিহ্নিত করতে হবে ।
৩ । নির্দিষ্ট দূরত্বে চিহ্নিত জায়গায় পর্ব করতে হবে । পর্ভের উপরের দিকের মাটি একদিকে এবং নিচের দিকের মাটি আর এক দিকে রাখতে হবে।
৪। চারা রোপণের ২০-৩০ দিন আগে গর্ত তৈরি করে প্রতি গর্তে পরিমাণমত সার দিয়ে মাটি ভরাট করে দিতে হবে।
৫। যে সব জায়গায় উইপোকার আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে সেখানে উইপোকা প্রতিরোধক ঔষধ ব্যবহার করতে হবে ।
৬। পর্কের মাটি জীবাণুযুক্ত করার জন্য পুরো রোগনাশক দ্রবণটি পর্বের মাটির সাথে ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে এবং একটি পলিখিন সিট দিয়ে পত্রটি ঢেকে দিয়ে ৪৮ ঘন্টা রাখতে হবে। এরপর পলিথিন সিট সরিয়ে নিয়ে কোলাল/খুরপি দিয়ে মাটি আলগা করে দিতে হবে। এ অবস্থায় ৭-১০ দিন রাখতে হবে। এ সময় গ্যাসের গন্ধ চলে যাবে, গর্ত জীবাণুযুক্ত হবে।
৭। গর্তের উপরের মাটির সাথে গোবর পঁচাসহ প্রয়োজনীয় সার মিশানোর পর গর্ত ভরাট করার সময় উপরের অংশের মাটি গর্ভের নিচের দিকে দিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে । আর নিচের অংশের আলাদা করে রাখা মাটি গর্ভের উপরিভাগে দিতে হবে। জমির উপরিভাগের মাটি বেশি উর্বর।
৮। সার মিশ্রিত মাটি গর্তে দেয়ার পর ভালোভাবে মাটি চেপে দিতে হবে। ৯। গাছের আকৃতি বিবেচনা করে গর্ভের ব্যাস ও গভীরতা নির্ণয় করতে হবে ।
| গাছের আকৃতি | চারা লাগানোর গর্তের মাপ | একটি চারা থেকে আর একটি চারার দূরত্ব |
| (ক) বড় বৃক্ষ জাতীয় পাছ (আম, কাঁঠাল, লিচু, নারিকেল, বেল ইত্যাদি) | ১ মিটার ব্যাস ১ মিটার গভীরতা বা ৯০ x ৯০ x ৯০ সে.মি. | ৭-৮ মিটার |
| (খ) মাঝারি গাছ (পেয়ারা, আতা, শরীফা, সফেদা, লেবু ইত্যাদি) | ৬০ সে.মি ব্যাস ও ৬০ সে.মি গভীর বা ৭৫×৭৫×৭৫ সে.মি.) | ৫ মিটার |
| (গ) ছোট গাছ (কলা, পেঁপে, সুপারি) | ৫০ সে.মি. ব্যাস ৫০ সে.মি. গভীর | ২ মিটার |
| (ঘ) খুব ছোট গাছ (আনারস, স্ট্রবেরী ইত্যাদি) | ১৫ সে.মি. ব্যাস ও ১৫ সে.মি গভীর) | ২ মিটার |
প্রাসঙ্গিক তথ্যঃ
মাঠ ফসলের সাথে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের মূল পার্থক্য হলো যে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের ক্ষেত্রে ভালোভাবে চাষের পর জমিতে নির্দিষ্ট আকারের গর্ত খনন করার পর সার প্রয়োগ করে গাছ লাগানো হয়। চারা রোপণের সময় চারার গোড়া পটে বা বেড়ে যতটুকু গভীরে ছিল ততটুকু গভীরে রাখতে হবে। চারা রোপণের পর ঝাড়ো বাতাস ও জীবজন্তু হতে রক্ষার জন্য খুঁটি ও বেড়া এবং আবহাওয়া শুল্ক ও রৌদ্রজ্জল হলে পাছের উপর ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে ।
প্রয়োজনীয় উপকরণ
১। কোদাল
২। খন্তা/ খাল
৩। ঝুড়ি
8। ঝরণা
৫। বাঁশের কাঠি
৬। বাঁশের খাচা
৭। দড়ি
কাজের ধাপ
১। সার মেশানো মাটি দিয়ে গর্ত পূরণ করার এক সপ্তাহ পর গর্তে চারা লাগাতে হবে ।
২। চারা যদি পটে থাকে তবে চারাটি সাবধানে পট থেকে বের করতে হবে। পলিথিন ব্যাগের চারা হলে পলিথিন একপাশ দিয়ে কেটে দিতে হবে। নার্সারি বেডে চারা থাকলে রোপণের ২-৩ সপ্তাহ আগে চারাটি খাসি করে নিতে হবে । খাসি করার এক সপ্তাহ পরে নার্সারি বেস্ত হতে চারাটি উঠায়ে পলিথিন ব্যাগ ব পটে স্থাপন করে ৪-৫ দিন ছায়ায় রাখতে হবে।
৩ । চারার গোড়ার বলের আকারে মাটি না সরিয়ে গর্ত হতে চারা লাগানোর স্থানের মাটি সরিয়ে নিতে হবে। পট হতে বা পলিখিন কেটে চারা বের করার সমর বাতে বল ভেঙে না যায় সেজন্য সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।
৪ । চারাটির কাণ্ড বাম হাতের তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের মধ্যে এবং বলটি ডানহাতের তালুতে নিয়ে চারাটি সোজা করে গর্ভে বসানোর পর গর্ত হতে পূর্বে সরানো মাটি দিয়ে বলের চারপাশ ভালো করে চেপে দিতে হবে।
৫। চারা রোপণের পর ঝড় বাতাস হতে রক্ষার জন্য একটি সোজা বাঁশের কাঠি দিয়ে শক্ত করে চারাটি বেঁধে দিতে হবে ।
৬ । চারা রোপণের পর তাতে ঝরনা দিয়ে হালকা সেচ দিতে হবে। গরু ছাগলের হাত থেকে চারা রক্ষা করার জন্য বাঁশের খাঁচা দিতে হবে। চারা বিকালে লাগানো উত্তম এবং রোপণের পর অন্তত এক মাস সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।
৭। আবহাওয়া শুকনো এবং রৌদ্রজ্জল থাকলে চারার উপর চাটাই বা নারিকেরের শুকনো ডাল দ্বারা ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
প্রাসঙ্গিক তথ্য
গাছের বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে চারার বয়স বিভিন্ন রকমের হতে পারে। যেমন-দীর্ঘমেয়াদি গাছের চারা ২-৩ বছরের নিতে হয় । সেখানে স্বল্পমেয়াদি গাছের চারার ৩-৪ মাসের নিতে হয়। এমন কি স্বল্প মেয়াদী ফলের চারা আরও কম বয়সের নেওয়া যেতে পারে।
প্রয়োজনীয় উপকরণ
(১) দীর্ঘ মেয়াদি ও স্বল্প মেয়াদি ফলের চারা (আম, কাঁঠাল, পেঁপে, লিচু, পেয়ারা, কলা, আনারস ইত্যাদি)।
(২) গর্ত তৈরির যন্ত্রপাতি (শাবল, খন্তা, কোদাল, খুরপি ইত্যাদি)
(৩) কাঠি এ সুতলি (
৪) পানি ও ঝরণা।
(৫) বাঁশের খাঁচা।
(৬) কীটনাশক ঔষধ
কাজের ধাপ
১। স্থানীয়ভাবে গুণগত মান সম্পন্ন উচ্চ ফলনশীল জাত চিহ্নিত করতে হবে। যেমন- কোন গাছে বা বিশেষ ফল পাছে নিয়মিত ফল ধরে। সাধারণ রোগ ও পোকা মাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে প্রতিকূল অবস্থায়ও ফল ধারণে তেমন কোন তারতম্য হয় না। ক্ষেত্র বিশেষে আগাম বা নাবিকল ধরে ইত্যাদি ।
২। কলম বা বীজ থেকে চারা তৈরি করার পর ২/৩ বছর নার্সারিতে পালন করার দরকার। কোন কোন ক্ষেত্রে ১ বছর নার্সারীতে পালন করলেও কোন অসুবিধা হয় না ।
৩। দুর্বল ও রোগাক্রান্ত চারা বাদ দিয়ে সতেজ চারা নিতে হবে।
৪। দীর্ঘমেয়াদি ফলের চারার গোড়ার দিকে এক মিটার কাজ পর্যন্ত কোন ডালপালা গজাতে দেয়া যাবে না।
৫। স্বল্পমেয়াদি ফলের ক্ষেত্রে চারার গোড়ার হতে উপরের দিকে পিরামিড আকৃতির হতে হবে অর্থাৎ গোড়া মজবুদ্ধ হতে হবে । পাতা চওড়া, ছড়ানো প্রকৃতির এবং চারা দূর্বল লিকলিকে হলে তা বাদ দিতে হবে ।
৬। দীর্ঘ বা স্বল্পমেয়াদি ফলের চারা নির্বাচনে চারার বয়স ফলের জাত ভেদে উপযুক্ত হতে হবে।
৭। চারা রোপণের গর্ত চারা রোপণের ২-৩ সপ্তাহ আগে তৈরি করতে হবে।
৮। প্রায় এক সপ্তাহ গর্ত করে খোলা রাখার পর সার মেশানো মাটি দিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে । গর্ত ভরাট করে এক থেকে দেড় সপ্তাহ রাখতে হবে ।
৯। চারার গোড়া হতে পট বা পলিব্যাগ সাবধানে সরাতে হবে। চারা লাগানোরে নির্দিষ্ট স্থানে চারার বলের সম পরিমাণ মাটি সরিয়ে সেখানে চারা কসাতে হবে। চারার গোড়ার কাও যতটুকু পর্যন্ত মাটিতে ঢাকা ছিল ততটুকু পর্যন্ত মাটির গভীরে ঢেকে স্থাপন করতে হবে।
১০ । চারার গোড়ায় যাতে পানি জমতে না পারে সে জন্য নালার ব্যবস্থা করতে হবে । অথবা চারার গোড়া উঁচু করে লাগাতে হবে ।
১১ । বিকেলের দিকে ও মেঘলা দিনে চারায় লাগানো উচিত। তাতে চারা সহজে লেগে যেতে পারে ।
১২ । আবহাওয়া শুকনা এবং রৌদ্রময় থাকলে চারায় সেচ প্রদান ও চারার উপরে এক থেকে দেড় সপ্তাহ পর্যন্ত ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে ।
১৩ । চারার পাশে সোজা খুঁটি পুঁতে তার সাথে চারা সোজা করে বেঁধে দিতে হবে।
প্রাসঙ্গিক
তথ্য চারায় সেচ প্রদান করতে হলে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করে তারপর সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা, চারা রোপণের নকশা এবং গাছের পানির চাহিদা, গাছের বৃদ্ধি পর্যায় ইত্যাদি বিবেচনা করে সেচ প্রদান করতে হয় । সেচের পানি বেশি হলে বা অত্যধিক বৃষ্টি পড়ে পানি জমার সম্ভাবনা থাকলে চারার গোড়া হতে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে ।
প্রয়োজনীয় উপকরণ
১। ফলের বাগান
২। সেচ যন্ত্রপাতি (পাওয়ার পাম্প, গভীর বা অগভীর পাম্প, ঝরনা, পানি সরবরাহের পাইপ ইত্যাদি)
৩ । মাপ ফিতা
৪ । কোদাল, সুতলি, খুঁটি ইত্যাদি ।
কাজের ধাপ
১। স্থায়ী বড় ফল বাগানের জন্য দুই সারির মাঝখানে নালা তৈরি করতে হবে ।
২। গাছের গোড়ায় থালার মত করে নিয়ে নালার মাঝে সংযোগ তৈরি করে পানি দিতে হবে। এতে পানির অপচয় কম হবে ।
৩। ছোট ছোট ফল গাছের জন্য প্রতি দুই সারি পর পর নালা তৈরি করতে হবে। গাছের দুসারিকে বেডের মত করে বেডের মাঝখান দিয়ে সেচ দিতে হবে । মাঝখানের নালায় পানি ভর্তি করে ২/৩ ঘন্টা রেখে দিলে সমস্ত জমি ভিজে যাবে ।
৪ । চারা রোপণ উপযোগী হলে আসতে আসতে সেচ কমাতে হবে। এতে চারা রোপণজনিত আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে । তবে চারা রোপণের পূর্বে নার্সারিতে থাকা অবস্থায় ঝরনার সাহায্যে সেচ দিতে হবে । চারার অবস্থা ভেদে ও আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে সকাল বিকাল পানি সেচ দিতে হবে ।
৫ । চারা লাগানোর সময়, গাছের বড় বাড়তি ও ফুল ফোটার সময়, ফল ধরার সময় হতে ফল বড় হওয়ার সময় কালে সেচ দিতে হবে। সেচের সঠিক সময় নিরূপণের জন্য মাঠে গিয়ে গাছের শিকড়ের গভীরতার তিনভাগের দুইভাগ গভীর থেকে মাটি সংগ্রহ করতে হবে । সংগৃহীত মাটিতে চাপা দিয়ে বল করা না গেলে বা বল করার পর প্রায় ১ মিটার উপর হতে নিচে ফেলে দিলে সহজেই ভেঙে গেলে সেচ দিতে হবে ।
৬। বিকালে পানি দিতে হবে। তাতে বাষ্পীভবন কম হবে এবং পানির অপচয় কম হবে।
৭ । পানির প্রবাহ বা নিষ্কাশনের সুবিধার জন্য জমির উঁচু দিক থেকে ঢালের দিকে নালা করতে হবে । প্রয়োজনে এর সাথে গাছের গোড়ায় ছোট ছোট বেসিন বা থালাগুলো এবং নিচু ও অসমতল স্থানের সাথে নালা যুক্ত করা যেতে পারে ।
৮। বাগানে গাছের আকৃতি ছোট হলে ফোয়ারা পদ্ধতিতে সেচ দেয়া যেতে পারে ।
৯ । পাছে ফুল অবস্থায় ফোয়ারা সেচ দিলে পরাগায়নের অসুবিধা হতে পারে । ফুল অবস্থার ফোয়ারা সেচ দেয়া যাবে না।
১০। বৃষ্টির পানি যাতে গাছের গাড়ার দাঁড়াতে না পারে সেজন্য নিকাশ নালা তৈরি করতে হবে ।
প্রাথমিক তথ্য
দু'ভাবে ফলের চারা করা হয়। বীজ থেকে এবং ফলগাছের অঙ্গ থেকে। বীজের চারা সহজেই করা যায় এবং খরচও কম। বীজ থেকে গজানো চারা বড় ও শক্ত হয় এবং ফল বেশি দেয়। নারিকেল ও তালের মত কিছু ফলের চারা কেবল বীজ থেকে করা হয়। তবে আধুনিক প্রযুক্তি টিস্যু কালচারের মাধ্যমে এসব পাছের চারা বীজ ছাড়াও করা যেতে পারে। বীজের চারার প্রধান অসুবিধা হলো মাতৃ গাছের গুণ বদলে যায় এবং গাছ দেরিতে ফল ধরে। কলা ও আনারসের মত কিছু ফলের গাছ বীজ থেকে করা যায় না। কলম বা অঙ্গজ পদ্ধতিতে মাতৃগাছের সকল ক্ষণ থাকে এবং কম সময়ে ফল পাওয়া যায় । কলমের সাহায্যে একই গাছে বিভিন্ন জাতের ফল ফলানো যায় এবং ইচ্ছে করলে মূল গাছের জাত বদলে দেয়া যায়। কলমের অসুবিধা হলো এর খরচ তুলনামুলকভাবে বীজের চারা থেকে বেশি। ক) জোড় কলম তৈরি অনুশীলন
প্রাসঙ্গিক তথ্যঃ
গাছের আদি ঘোড়া ও উপজোড়া পরস্পর সংযুক্ত হয়ে যখন একটি একক গাছ হিসাবে বৃদ্ধি লাভ করে তখন তাকে গ্রাফট জোড় কলম বলে এবং এ জোড়া লাগানো প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় গ্রাফটিং বা জোড় কলম। যে গাছের ওপর কাঙ্ক্ষিত গাছের ছোট একটি অংশ জোড়া লাগানো হয় তাকে আদিজোড়া (rootstock) এবং কাঙ্খিত গাছের এ অংশটিকে উপজোড় (scion) বলে। সহজভাবে বলা যায় জোড় কলমের জোড়ম্যানের নিচের অংশ হলো আদিজোড় ও উপরের অংশ হলো উপজোড়।
জোড় কলম প্রধানত দু'ভাবে করা হয়ে থাকে। প্রথমত উপজোড়কে মাতৃগাছে সংযুক্ত অবস্থায় রেখে জোড়া লাগানো হয়। একে সংযুক্ত জোড় কলম বলে এবং দ্বিতীয়ত উপজোড়কে মাতৃগাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে জোড়ের সাথে জোড়া লাগানো হয়, একে বিযুক্ত জোড় কলম বলে।
সতর্কতা
১। আদিজোড় ও উপজোড়ের কর্তিত স্থান মসৃণ হতে হবে ।
২। আদিজোড় ও উপজোড় একসাথে বাঁধার পর মাঝখানে যেন কোনো ফাক না থাকে ।
খ) ভিনিয়ার জোড় কলম পদ্ধতি অনুশীলন
প্রাসঙ্গিক তথ্য: ভিনিয়ার জোড় কলম এক ধরনের পার্শ্ব জোড় কলম। এ পদ্ধতিতে আদিজোড়ের এক পার্শ্বে উপজোড়ের নিম্ন প্রান্ত স্থাপন করা হয় । উপজোড়কে মাতৃগাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আদি জোড়ের সাথে জোড়া লাগানো হয়।
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যসমূহ
- আদিজোড়
- উপজোড়
- সিকেচার ও ধারালো চাকু
- নাইলন স্ট্রিপ ও
- পলিথিন ব্যাগ
- রশি
কাজের ধাপ
- নার্সারি বেড় বা টবে বীজ থেকে চারা গাছ উৎপাদন করতে হবে। ৯ মাস থেকে শুরু করে ১৮ মাস পর্যন্ত বয়সের চারা গাছকে আদিজোড় হিসাবে ব্যবহার করা যাবে ।
- নির্বাচিত মাতৃগাছ থেকে উপজোড় সংগ্রহ করতে হবে । উপজোড় পাতার বোটা ১ সে.মি. রেখে পাতাগুলো কেটে ফেলতে হবে ।
- মাটি থেকে ২৫ থেকে ৩০ সে.মি উপরে আদিজোড়ের উপর লম্বালম্বিভাবে ৫-৬ সে.মি, তেরছাভাবে কার্টুন । উক্ত কর্তনের নিম্নপ্রান্তে ছোট তেরছা কর্তনের মাধ্যমে কর্তিত কাঠ সরিয়ে ফেলতে হবে ।
- উপজোড়ার নিম্নাংশে আদিজোড়ের অনুরূপ কর্তন (চিত্র দ্রষ্টব্য) দিয়ে উপজোড়টি তৈরি করতে হবে ।
- আদি জোড় ও উপজোড় একত্রে ভালোভাবে বসিয়ে নাইলন স্ট্রিপ দ্বারা শক্ত করে বাঁধতে হবে ।
- পলিথিন ব্যাগ দ্বারা উপজোড়টি আবৃত করে আদিজোড়ের সাথে বেঁধে রাখতে হবে । আদি জোড় ও উপজোড় ভালোভাবে জোড়া লাগার পর (৫০-৬০ দিন পর) জোড়স্থানের ২-৩ সে.মি. উপরে আদিজোড়টি কেটে ফেলতে হবে ।
সতর্কতাঃ
- দুই তিন দিন পর পর পলিব্যাগ খুলে ভেতরে জমাকৃত পানি ফেলে দিতে হবে।
- আদিজোড় ও উপজোড় একসাথে বাঁধার পর মাঝখানে যেন কোনো ফাঁকা না থাকে ।
- জোড়াস্থানের নিচে আদিজোড়ে কোন শাখা প্রশাখা জন্মতে দেয়া যাবে না ।
গ) চক্ষু কলম (ৰাডিং) পদ্ধতি অনুশীলন
প্রাসঙ্গিক তথ্যঃ
বাডিং এমন এক প্রকারের জোড় কলম যাতে শাখার পরিবর্তে পল্লবের কুঁড়ি বা চোখ (ফ) উপজোড়রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । একে চোখ কলম বলে। শীতের শেষে, বসন্তে যখন গাছ বেশ সক্রিয় সম্পূর্ণ ও বর্ধনশীল হয়ে উঠে সে সময় অর্থাৎ মার্চ-এপ্রিল মাস চোখ কলমের জন্য খুবই উপযোগী। তবে ঐ সময় খুব গরম থাকলে চোখ শুকিয়ে যেতে চায়। চোখ কলমের জন্য প্রায় এক বক্সের বয়স্ক আদিজোড় নিলে ভাল হয়। বিবিধ প্রকার চোখ কলমের মধ্যে টি চোখ কলম, ভালি চোখ কলম, চক্র চোখ কলম ইত্যাদি উল্লেখ যোগ্য ।
ঘ) টি চোখ কলম পদ্ধতি অনুশীলন
প্রাসঙ্গিক তথ্যঃ
কলম এক প্রকার চোখ কলম বা বাডিং। এ পদ্ধতিতে উন্নত ডালের একটি মাত্র চোখ ব্যবহার করে নতুন গাছ উৎপাদন করা যায় । আদি জোড়ের গারে টি- কেটে সেখানে বর্ম আকৃতির বা চোখ আকৃতির কুড়ি স্থাপন করা হয় বলে এ পদ্ধতির এরূপ নামকরণ করা হয়েছে।
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি
- আদিজোড় ও উপজোড়
- বাডিং ছুরি
- দ্বিফলক বিশিষ্ট ছুরি
- নাইলন স্ট্রিপ/পলিথিন ফিতা
কাজের ধাপ
- নির্বাচিত আদিজোড়ে মাটি থেকে ২০-২৫ সে.মি. উপরে কাণ্ডের ওপর আড়াআড়িভাবে ১.৩ সে.মি পরিমাণ লম্বা কর্তন দিতে হবে। একাটা দাগের মাঝখান থেকে নিচের দিকে ৪-৫ সে.মি. পরিমাণ আরেকটি লম্বালম্বি কর্ডন দিতে হবে।
- লম্বালম্বি দাগ রাবর চাকু দ্বারা কাঠ থেকে বাকলকে আলগা করতে হবে ।
- কাঙ্ক্ষিত মাতৃগাছ থেকে সুপ্ত কুঁড়িসহ একটি বাকল কেটে নিতে হবে । বাকলটিকে ঢালের মত করে তৈরি করতে হবে ।
- কুঁড়ি সহ বাকলটি আদিজোড়ের কর্তিত অংশে ঢুকিয়ে দিতে হবে ।
- কুঁড়টিকে বাইরে রেখে পলিথিন কিতা যারা বাকলটি আদিজোড়ার সাথে ভালোভাবে বেঁধে দিতে হবে।
৩। সতর্কতাঃ বাঁধার সময় কুড়িটি যেন ঢাকা না পড়ে প্রস্ফুটিত কুঁড়ি ব্যবহার করা যাবে না
প্রাসঙ্গিক তথ্য
ফল গাছ বিভিন্ন সময় ও উদ্দেশে ছাঁটাই করা হয় । সময় ও উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করে গাছ ছাঁটাইকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় । যথা-ট্রেনিং ও প্রুনিং । ফল গাছ থেকে সঠিক ফলন ও মানসম্মত ফল পেতে হলে গাছের বৃদ্ধির প্রাথমিক অবস্থায় ট্রেনিং এবং গাছ ফল ধারনের তরে পৌছানারে পর প্রুনিং করা প্রয়োজন । ট্রেনিং ও প্রনিং করার জন্য যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকা দরকার । কারণ যথাযথ অভিজ্ঞতা না থাকলে অতিরিক্ত ট্রেনিং ও প্রুনিং করলে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি ।
ক) ট্রেনিং পদ্ধতি অনুশীলন
প্রাসঙ্গিক তথ্য
গাছে ফল ধারনের পূর্বে একটি সবল ও সুন্দর কাঠামো তৈরির জন্য ছাঁটাই করা হয়। এ কাজটি প্রধানত প্রধান কাণ্ডকে কেন্দ্র করে করা হয় বলে এ ধরনের ছাঁটাইকে ট্রেনিং বলা হয় ।
প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রপাতি
- ট্রেনিংয়ের জন্য গাছের চারা বা ছোট গাছ
- ছুরি
- কাঁচি
- সিকেচার
- প্রুনিং করাত
- ডাল কাটার দা
- বড় গাছের ডাল কাটার কাঁচি
- বোর্দোপেষ্ট বা ছত্রাকনাশক
- গরম মোমে
- পলিথিন
কাজের ধাপ
১। ট্রেনিং এর প্রয়োজনীয় উপকরণ (চারাগাছ, সিকেচার, টেপ) সংগ্রহ করতে হবে।
২। চারা গাছে ট্রেনিং করতে হবে । ঝোপালো গাছ, যেমন- পেয়ারা, বাতাবীলেবু, শরিফা ইত্যাদি গাছে মুক্ত ও নাতি উচ্চকেন্দ্র পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে । দীর্ঘ বৃহদাকার গাছ, গাছের জন্য উচ্চকেন্দ্র ট্রেনিং অনুসরণ করতে হবে ।
৩। ট্রেনিং পদ্ধতির প্রয়োগ: ট্রেনিং পদ্ধতির দুইটি ব্যবস্থা নিম্নের ক) ও খ) অংশে বর্ণনা করা হলো -
ক) উচ্চ কেন্দ্র ট্রেনিং পদ্ধতি
- নার্সারিতে ১ থেকে দেড় বছরের চারা নির্বাচন করতে হবে ।
- নির্বাচিত চারার উচ্চতা ১ মিটার হলে ভালো হয় ।
- চারাটির নিচের দিকে পাশে গজানো শাখাগুলো এমনভাবে কাটতে হবে, যেন কাটা চিহ্ন মাটির সাথে লম্বা থাকে ।
- শাখার যেখানে কাঁটা হবে তা যেন প্রধান কাণ্ড হতে কম পক্ষে ২-৬ সে.মি দূরে হয় ।
- শাখার যেখানে কাটা হবে তা ৰেম পৰ্ব সলিং বা গিরার ওপর না হয় ।
- প্রধান কাণ্ডের সাথে পদ্মাননা বা সংযুক্ত শাখা চিকন হলে প্রনিং চাকু এবং শাখা মোটা হলে সিকেচার বা প্রুনিং করাত দিয়ে কাটতে হবে
- সংযুক্ত শাখার কাটা স্থানে বোর্দোপেস্ট বা ছত্রাকনাশক লাগাতে হবে।
- ট্রেনিং এর কাজটি পরিষ্কার ও রৌদ্রজ্জল দিনে করতে হবে। খুব সকালে বা একেবারে বিকালে শাখা ছাটাই করা উচিত হবে না ।
খ) নাতি উচ্চ কেন্দ্র ট্রেনিং পদ্ধতি
- এ পদ্ধতিতে কাজের জন্য নার্সারীতে ১ থেকে ২ বছরের চারা নির্বাচন করতে হবে।
- চারাটির প্রধান কাণ্ড ১ মিটার উঁচু হওয়া পর্যনত পাশের শাখাগুলো কেটে দিতে হবে । তবে এ সময় প্রধান কাণ্ডের মাথা কাটা যাবেনা। ।
- এর পর প্রধান কাণ্ডের উপরের দিকে ৫-৬ টি শাখা রেখে বাড়তে দিতে হবে । ।
- এ সমস্ত শাখাগুলো বাড়ার সাথে সাথে প্রধান কাণ্ডটি ১.৫-২.০ মিটার উঁচু হলে প্রধান কাজের মাথা কেটে দিতে হবে ।
- প্রধান কাণ্ড ও পার্শ্ব শাখাগুলো কাটার পর পরই কাটা স্থানে বোদোপেষ্ট বা ছত্রাকনাশক লাগাতে হবে ।
গ) মুক্ত কেন্দ্র ট্রেনিং পদ্ধতি
- এ পদ্ধতিতে কাজের জন্য নার্সারীতে ১ বছরের চারা নির্বাচন করতে হবে।
- চারাটির প্রধান কাজ ০.৫ থেকে ১.০ মিটার উঁচু হলে মাথা বা শীর্ষ কুঁড়ি কেটে দিতে হবে।
- এর পাশের শাখাগুলো বাড়তে দিতে হবে।
- গাছ ঝোপালো করার প্রয়োজন হলে পাশের শাখা গুলো কিছুটা বড় হতে দিতে হবে। এরপর শাখাগুলোর মাথা কেটে দিতে হবে ।
- তবে পাশে গজানো শাখা বেশি ঘন হলে নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে কিছু কিছু শাখা কেটে দিতে হবে ।
- এ কাজ সম্পন্ন করে গাছের কাঠামো ঠিক করতে ২-৩ বছর সময় লাগবে ।
- প্রতিবারই শাখার বা কাণ্ডের কাটাস্থানে বোর্দোপেস্ট বা ছত্রাকনাশক লাগাতে হবে।
সতর্কতা
১। ছাঁটাই করতে সিকেচার ব্যবহার করুন এবং থেঁতলানো বা ফেটে যাওয়া পরিহার করতে হবে।
২। ক্ষতস্থানে পাস্টার এবং আলকাতরার প্রলেপ দেওয়া ভালো।
ঘ) পাছ ছাঁটাই এর জন্য প্রর্নিং পদ্ধতি অনুশীলন ফল গাছ সাধারণত দুটো পদ্ধতিতে প্রুনিং করা হয়। যথা-
১। অর্থভাগ ছেদন ও
২। পাতলাকরণ এ
পদ্ধতিতে গাছের উৎপাদন ক্ষমতা ও গুণগত মাণ বৃদ্ধি, পুষ্প মঞ্জুরীর অধিক প্রফুরন, গাছের পূর্ণ বিকাশ, ফলের আকার আকৃতি, রঙ ও ফল ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গাছের কোন অংশ কেটে অপসারণ করা হয়। প্রনিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রপাতি
- গাছ (চোরা বা বয়স্ক )
- সিকেচার
- প্রুনিং করাত
- প্রুনিং কাঁচি
- ডাল কাটার কাঁচি
- বড় গাছের ডাল কাটা কাঁচি বা পালে প্রনার
- আলকাতরা
- ব্রাশ
কান্দ্রের ধাপ
১। প্রনিং-এর প্রয়োজনে বয়স্ক ও চারাগাছ ছাঁটাই করতে হবে। ঝোপালো গাছ (পেয়ারা, লেচু, শরীফা) মুক্ত রাখার জন্য অর্থভাগ জোন বা হেডিং ব্যাক প্রণালি প্রয়োজন হয় না। বরং কুল গাছের ফলনের জন্য হেডিং ব্যাক বা অগ্রভাগ ছেদন করা প্রয়োজন হয়। ঝোপালো গাছ ও অতি পুরাতন গাছকে উদ্দীপ্ত করতে খিনিং আউট/পাতলাকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে।
২। প্রুনিং অনুশীলনের জন্য নিচের পদ্ধতি দুটি অনুশীলন করতে হবে।
ক) হেডিং ব্যাক বা শাখার ডাল ছেদন পদ্ধতি
এ পদ্ধতিতে কাণ্ডের বা শাখার অগ্রভাগ থেকে কিছু কেটে বাদ দিতে হবে । কর্তিত স্থানে ব্রাশ দিয়ে পরাটার এবং আলকাতরার প্রলেপ লাগিয়ে দিতে হবে। ছোট ছোট কান্ড সিকেচার ও বড় কাণ্ডসমূহ করাত দিয়ে কেটে দিতে হবে। এ পদ্ধতি অনুশীলনের জন্য ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ফল পাড়ার পর ৫-৬ বছর বয়স্ক কুল পাছ নির্বাচন করতে হবে ।
খ) থিনিং আউট (পাতলাকরণ) বা শাখা অপসারণ পদ্ধতি
এ পদ্ধতিতে কাগু বা শাখাকে সম্পূর্ণরূপে কেটে বাদ দিতে হবে। কর্তিত স্থানে ব্রাশ দিয়ে পরাটার এবং আলকাতরা লাগিয়ে দিতে হবে। ছোট ছোট শাখা সিকেচার দিয়ে ও বড় শাখাসমূহ করাত দিয়ে কাটতে হবে । ঝোপাল গাছ এভাবে ছাঁটাই করতে হবে। এ পদ্ধতি অনুশীলনের জন্য শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফল আহরণের পর ৪-৫ বছর বয়স্ক লেবু গাছ নির্বাচন করে কাজটি করতে হবে।
সতর্কতা
১। সুচিন্তিতভাবে ছাঁটাই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে ।
২। গাছ, জাত ও সময় ভেদে ছাটাই এর সময় বিভিন্ন হবে। পত্র পতনশীল গাছ শীতকালে এবং চির সবুজ গাছ গ্রীষ্মকালে (ফল সংগ্রহের পর) ছাটাই করা উচিত ।
প্রাসঙ্গিক তথ্য
আমের বংশ বিস্তার দু'ভাবে হয়ে থাকে। যেমন-
ক) বীজ দ্বারা ও খ) কলমের সাহায্যে
বীজ দ্বারা বংশবিস্তার করা হলে তাতে মাতৃ গাছের গুণাগুণ বজায় থাকে না। তাই আমের গুণাগুণ ঠিক রাখার জন্য কলমের সাহায্যে অর্থাৎ অঙ্গজ বংশ বিস্তারের মাধ্যমে চাষাবাদ করা উত্তম। ভালো জাতের চারা নির্বাচন-আমাদের উপ-মহাদেশে প্রায় এক হাজার জাতের আম চাষ করা হয়। তন্মধ্যে বাংলাদেশে প্রচলিত কয়েকটি ভালো জাতের আমের নাম উল্লেখ করা হলো। ল্যাংড়া, গোপালভাগ, খিরসাপাত, মহানন্দা, কিষাণভাগে, মিসরীভাগে, কোহিতুর, হিমসাগর, আম্রপালি ইত্যাদি আগাম জাত। ফজলী, আশ্বিনা, চৌসা, কুয়াপাহাড়ী ইত্যাদি নাৰীজাত। এছাড়া প্রত্যেক এলাকার কিছু স্থানীয় ভালো জাতের আম পাওয়া যায় ।
উপকরণ
১। বীজ বা কলম ২। সার (জৈব-রাসায়নিক) ৩। ছত্রাক নাশক ও কীটনাশক ৫। প্রেয়ার ও লাঙ্গল ও জোয়াল ৭। কোদাল ৮। মই ও মুখর। খুরপি ১০। পলিথিন ফিতা ১১। সিকেচার ১২। ঝুড়ি ১৩। রশি ১৪ । খুঁটি ১৫। জুনিং 'স' ১৬। খাঁচা ১৭। বাবারি ১৮। সিরিঞ্জ ১৯ । তুলা ২০। আলকাতরা / কেরসিন ২১ । বদন ২২। নিড়ানি ।
কাজের ধাপ
১। স্থানীয় আবহাওয়ার উপযোগী আমের উন্নত জাত নির্বাচন করতে হবে । প্রয়োজনীয় কলম বা চারা সংগ্রহ করতে হবে । প্রতি একরে ৩৫ টি কলম/চারা লাগবে (বর্গাকার পদ্ধতি, দূরত্ব ১২ মিটার)
২। আম চাষের জন্য উঁচু স্থান এবং সুনিষ্কাশিত গভীর দো-আঁশ মাটি নির্বাচন করতে হবে ।
৩ । উন্নত জাতের সায়ন গাছ হতে ভিনিয়ার কলমের মাধ্যমে কলম তৈরি করতে হবে বা সংগ্রহ করতে হবে । কলম তৈরির জন্য তত্ত্বীয় অংশ অনুসরণ করতে হবে।
৪ । জমি লাঙল দিয়ে ৩-৪ টি চাষ দিতে হবে। মুগুর দিয়ে মাটির ঢেলা ভেঙে দিতে হবে । আগাছা বাছতে হবে।
৫ । জমিতে বর্গাকার পদ্ধতিতে ১২ মি. দূরত্ব (কলমের চারার জন্য) কোদাল দিয়ে ৭৫ সে. মি. x ১ মি. ১ মি. গভীর ৩৫ টি গর্ত করতে হবে । গর্ত ১ সপ্তাহ খোলা রাখার পর তত্ত্বীয় অংশে বর্ণিত পরিমাণ সার দিতে হবে । গর্ত ভরাটের সময় উপরের মাটি নিচে ও নিচের মাটি উপরে দিতে হবে। এর ১০-১৫ দিন পর বিকেল বেলা কলম চারা রোপণ করতে হবে ।
৬ । যদি টবে উৎপাদিত কলমের চারা রোপণের প্রয়োজন হয় তবে প্রথমে টবের চারধারে ও নিচে আস্তে আস্তে আঘাত করতে হবে । টবটিকে চারা সমেত উল্টো করে চারার গোড়া দু আঙ্গুলের ফাঁকে চারাটিকে আটকিয়ে নিতে হবে । তারপর টবের কিনারা কোন খুঁটির সাথে আস্তে আস্তে আঘাত করতে হবে যেন চারাসহ সম্পূর্ণ মাটির বল খুলে আসে। এই প্রক্রিয়াকে “ডি পটিং” বলে। সাবধানে চারা বের করে চারাটি টবে যে পরিমাণ মাটির নিচে ছিলো ঠিক ততটুকুই চারার গর্তে পুঁতে দিতে হবে। তারপর চারধারে হাতে চেপে মাটি বসিয়ে, খুঁটি পুঁতে ও খাচা দিয়ে চারাকে ঘিরে শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে। রোপণের পর ৫-৭ দিন ঝাঁঝরি দিয়ে পানি দিতে হবে ।
৭ । গাছের গোড়ায় আগাছা হলে নিড়িয়ে দিতে হবে। সেচের পর জো এলে চটা ভেঙে মাটি আলগা ও নরম রাখতে হবে । বয়স্ক গাছে বর্ষার আগে ও পরে গোড়ার মাটি কুপিয়ে বা লাঙল দিয়ে আলগা করতে হবে।
৮ । চারা রোপণের পর সার প্রয়োগ করতে হবে। সারের মাত্রা তত্ত্বীয় অংশের বর্ণনা অনুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে।
৯ । সার প্রয়োগের নিয়ম হলো; ঠিক দুপুরের বেলা যে পরিমাণ স্থানে গাছের ছায়া পড়ে সে অংশ পর্যন্ত কোদাল দিয়ে মাটি আলগা করে সার প্রয়াগ করে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। গাছের গোড়ার চারদিকে (৩০-১০০ ২-৩ সপ্তাহ পর পর সেচ দিতে হবে । তবে গাছে মুকুল আসার আগে সেচ দেয়া যাবেনা । এতে করে মুকুল না এসে নতুন পাতা বের হয়ে যাবে । গাছের ফল মটর দানার আকৃতি হলে ৮-১০ দিন পর পর সেচ দিতে হবে । বর্ষায় নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে । সে.মি. জাত ভেদে) কিছু জায়গা বাদ রেখে সার প্রয়োগ করতে হয় ।
১০। গাছে বেসিন বা থালা পদ্ধতিতে সেচ দিতে হবে । চারা গাছে প্রথম বছর শুকনো মৌসুমে ৮-১০ দিন পর পর এবং দ্বিতীয় বছর থেকে পঞ্চম বছরে
১১ । কলমের চারা রোপণের পর ৩-৫ বৎসর পর্যন্ত মুকুল এলে ছিড়ে ফেলতে হবে। এতে গাছের বৃদ্ধি পরিপূর্ণ হবে এবং পরবর্তীতে ফলন ভাল হবে । গাছের গোড়া থেকে ২ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত সকল শাখা প্রশাখা ছেটে ফেলতে হবে এবং ৪-৫ টি সতেজ ও চারদিকে প্রসারিত শাখা রেখে বাকীগুলো প্রুনিং করতে হবে । মরা ও রোগাক্রান্ত ডাল ও কলমের জোড়ের নিচ থেকে বের হওয়া ডালপালা সিকেচার দিয়ে প্রুনিং করতে হবে ।
১২ । গাছে পোকামাকড় ও রোগ বালাই দমনে তত্ত্বীয় অংশে বর্ণিত ব্যবস্থাবলি গ্রহন করতে হবে ।
১৩। আম সংগ্রহ করতে বাঁশের আগায় জালি বেঁধে পরিপক্ক আম পেড়ে আনতে হবে। আম পাড়ার পর আঘাতপ্রাপ্ত, কাটা, পোকাধরা, পচাফল বাছাই করতে হবে। আকার অনুসারে বড়, মাঝারি ও ছোট ফল গ্রেডিং করতে হবে। দূরে পাঠাতে বা বাজারজাতের জন্য কেবল মাত্র ফলের গায়ে রং এসেছে এরূপ আম সংগ্রহ করতে হবে । সংগৃহীত আম বাঁশের খাচা বা কাঠের বাক্সে খড়ের মধ্যে প্যাকিং করে প্রেরন করতে হবে ।
সতর্কতা
১। শীতের প্রথমভাগে সেচ দিলে ফুল না গজিয়ে, গাছে পাতা গজাতে পারে ।
২। গাছে ফুল ফোটা থেকে শুরু করে মটর দানার মত গুটি হওয়ার সময়সীমার মধ্যে সেচ দেওয়া যাবেনা ।
৩। ফল করা বন্ধ করতে সেচ দিয়ে এবং পানাফিক্স হরমোন (২-৩ মিলি ১০ লি: পানিতে) ১-৩ সপ্তাহ পর পর প্রে করে উপকার পাওয়া যায় ।
প্রাসঙ্গিক তথ্য
কাঁঠাল বহু বর্ষজীবী দ্বিবীজপত্রী বৃক্ষ। স্ত্রী ফুল ও পুরুষ ফুল একই গাছে পৃথকভাবে ধরে। কাঁঠাল পরপরাগায়িত ফসল, বংশবিস্তার সাধারণত বীজ দ্বারা হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি গাছই একটি আলাদা জাত। টব বা পলিথিন ব্যাগে বীজ বপন করে তা থেকে আঙ্কুরিত চারার বয়স ১-২ বছর হলে রোপণের জন্য ব্যবহার করা হয় । জাতের বিশুদ্ধতা রক্ষা ও ভালো জাত সম্পন্ন ফল পেতে হলে ৮-১০ দিন বয়ক চারার ভালো কোন জাতের অঙ্কুর জোড় করে চারা উৎপাদন করা যায়।
উপকরণ
(১) বীজ/কাটিং (২) সার (জৈব ও রাসায়নিক) (৩) কীটনাশক (৪) ছত্রাকনাশক (৫) স্প্রে যন্ত্র (৬) পানি ( ৭ ) লাঙল (৮) জোয়াল (৯) মই (১০) মুগুর (১১) খুরপি (১২) পলিথিন ফিতা (১৩) সিকেচার (১৪) ঝুড়ি (১৫) খুঁটি (১৬) রশি (১৭) করাত (১৮) খাঁচা (১৯) টিন (২০) ঝাঝরি (২১) বালি (২২) বাশ (২৩) সিরিঞ্জ (২৪) তুলা (২৫) আলকাতরা/কেরোসিন (২৬) কোদাল ।
কাজের ধাপ
১। কাঁঠালের উন্নত জাত নির্বাচন করুন। প্রয়োজনীয় চারা (৩৫টি/একরে) সংগ্রহ করুন।
২। কাঁঠাল চাষের জন্য উঁচু স্থান এবং উর্বর সুনিষকাশিত গভীর পেঁআশ এঁটেল দোআশ মাটি নির্বাচন করুন ।
৩ । উন্নত জাতের গাছ থেকে ভিনিয়ার কলম করে চারা তৈরি করুন ।
৪ । কাঁঠালের জমি ভালভাবে লাঙল দিয়ে ৪/৫টি চাষ ও মই দিন । মুগুর দিয়ে ঢেলা ভেঙে দিন । আগাছা হাতে বেছে সমতল করুন ।
৫ । জমিতে গর্ত খননের জন্য (কাঁঠালের কলমের চারা ৩৫) ১২ মি: দুরত্বে কোদাল দিয়ে ১x১ মি. গভীরী চওড়া মাপের ৫টি গর্ত তৈরি করুন । গর্ভ সপ্তাহকাল খোলা অবস্থায় রেখে দিন। এরপর গর্তের মাটির সাথে জৈব সার বা গোবর ২৫ কেজি এবং ৩০০ গ্রাম টিএসপি মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে দিন । গা ভরাট করার সময় উপরের মাটি নিচে এবং নিচের মাটি উপরে দিন এবং ১০/১৫ দিনপর বিকালের দিকে চারা লাগান ।
৬। চারা রোপণের জন্য টব থেকে চারা বের করে (আম দ্রষ্টব্য) নিন । চারা গর্তে বসিয়ে চারদিকে হাতে মাটি চেপে দিন । খুঁটি পুতে রশি দিয়ে চারা শক্ত করে বেঁধে দিন। রোপণের পরপর ঝাঝরি দিয়ে পানি দিন। ৫-৬ দিন সেচ ও ছায়া দিন । প্রতিটি চারাগাছ খাঁচা দিয়ে ঘিরে শক্ত করে খুঁটিসহ খাঁচা বেধে দিন ।
৭। চারা গাছের গোড়ায় আগাছা জন্মালে নিড়িয়ে তুলে দিন। মাটি আলগা করুন। সেচের পর জমিতে জো এলে চেপে থাকা মাটি ভেঙে আলগা করে দিন । বয়স্ক গাছে বর্ষার আগে ও পরে গোড়ার মাটি কোদাল দিয়ে লাঙল দিয়ে আলগা করে দিন এবং সব সময় আগাছামুক্ত করে রাখুন ।
৮। কাঁঠাল গাছে সার দুই দফায় বর্ষার পরে ও আগে উপরি প্রয়োগ করুন ।
৯ । চারা রোপণের পরে গাছ প্রতি ১০ কেজি জৈব সার, ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৩০০ গ্রাম টিএসপি ও ৩০০ গ্রাম এমপি সার প্রয়োগ করুন। দশ বছর বয়স্ক গাছে ৮০ কেজি জৈব সার, ইউরিয়া ১ কেজি, টিএসপি ১.৫ কেজি ও এমপি১.৫ কেজি প্রয়োগ করুন। এসব সার দুই দফায় (৮নং এ বর্ণিত নিয়মে) প্রয়োগ করুন ।
১০। গাছের গোড়ার চারদিকের কিছু জায়গা প্রকার ভেদে ৩০-১০০ সে.মি বাদ রেখে দুপুরে যতটুকু স্থানে ছায়া পড়ে সে অংশের মাটি কোদাল বা লাঙল দিয়ে আলগা করে সার প্রয়োগ করে মাটিতে মিশিয়ে দিন ।
১১ । সার প্রয়োগের পর গাছে থালা পদ্ধতিতে সেচ দিন । চারা গাছে বর্ষাকাল বাদে প্রয়োজনে ৭-১০ দিন পর পর এবং বয়স্ক গাছে ১৫-২০ দিন পর পর সেচ দিন।
১২। কাঁঠাল গঠনের জন্য বয়স্ক কাঁঠাল গাছের গোড়ায় ৪-৫ মি. এর মধ্যে ডালপালা গজালে ছেটে ফেলুন । মরা রোগাক্রান্ত ডালপালা ছেটে দিন। বয়স্ক গাছে ফল সংগ্রহের পর কাণ্ডে গজানো ছোট শাখা ও ফলের বোটার অবশিষ্টাংশ ঘেঁটে দিন ।
১৩ । কুঁড়ির কীড়া ও ফলের মাজরা পোকা দমনের জন্য প্রতি ১০ লি. পানিতে ৪-৫ চা চামচ ডায়াজিনন-৬০ তরল কীটনাশন গুলে ফল, কুঁড়ি ও পাতায় ভালোভাবে স্প্রে করুন ।
১৪ । কাণ্ডের মাজরা পোকা দমনের জন্য--(১) চিকন বক্র তার ঢুকিয়ে কীড়া বের করে এনে মেরে ফেলুন (২) গর্তে সিরিঞ্জ দিয়ে কেরোসিন/ আলকাতরা ঢুকিয়ে (১ সিসি) দিন, (৩) আলকাতরা ভেজানো তুলা বা কাদা দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে দিন ।
১৫। পাতায় দাগ পড়া ও পঁচা রোগের আক্রমণে প্রতি ১০লি, পানিতে ৪০-৫০ গ্রাম ডাইথেন-এম-৪৫ পাউডার গুলে পক্ষকাল পরপর পাতা, মুচি, ফল এবং ডগায় স্প্রে করুন ।
১৬ । গাছে ফুল আসার ৫-৬ মাস পর ফল সংগ্রহ করতে পারেন। পরিপুষ্ট ফল সাবধানে পেড়ে এনে খারাপ ভাল বাছাই করে নিন । দূরে চালান দিতে হলে একটু শক্ত কাঁঠাল পেড়ে পাঠান ।
সতর্কতা
১। কাঁঠাল গাছ জলাবদ্ধতা মোটেই সহ্য করতে পারে না। তাই নিকাশের ভাল ব্যবস্থা রাখতে হবে। এবারে কাজের ধাপ অনুসরণ করে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন ।
প্রসঙ্গিক তথ্য
সাধারণত কলার যৌন পদ্ধতিতে বা বীজ হতে বংশবিস্তার করা হয় না। কলা গাছের গোড়া থেকে যে তেউর (সাকার বের হয় তা দিয়ে এর বংশ বিস্তার করা হয়ে থাকে। কলার অসি চারা ও পানি চারা এই দু'ধরনের তেউড় বা চারা পাওয়া যায়। রোপণের জন্য অসি চারা উত্তম । কারণ রোপণের পর এগুলো কম মরে এবং দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হয় । তবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উভয় প্রকার চারার মধ্যে ব্যবধান থাকে না। কলার চারা অনেক বড় হওয়ার পরও রোপণ করা চলে তবে ছোট আকারের চারা উৎকৃষ্ট। ৩৫-৫০ সে.মি. দীর্ঘ ও পুরু গোড়া বিশিষ্ট চারা রোপণের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট।
উপকরণ
(১) চারা (২) সার (জৈব ও রাসায়নিক) (৩) কীটনাশক (৪) ছত্রাকনাশক (৫) প্রে যন্ত্র (৬) পানি (৭) লাঙল (৮) জোয়াল (৯) মই (১০) মুগুর (১১) খুরপি (১২) কোদাল (১৩) ছুরি (১৪) পলিথিন (১৫) খুঁটি (১৬) রশি (১৭) ঝুড়ি (১৮) ঝাঝরি ।
কাজের ধাপ
১। কলার উন্নত জাত নির্বাচন করুন । প্রয়োজনীয় চারা (৫৩৮-১২১০ টি/একরে) সংগ্রহ করুন ।
২। কলা চাষের জন্য বন্যামুক্ত উঁচু স্থান এবং সুনিষ্কাশিত উর্বর পেঁআশ / এঁটেল দোআশ মাটি নির্বাচন করুন ।
৩ । সংগৃহীত চারা থেকে কীট/রোগাক্রান্ত বা খারাপ চারা বেছে ফেলে ৫০-৬০ সি.মি লম্বা ও ১.৫-২.৫ কেজি রাইজোম যুক্ত ভাল চারা নির্বাচন করুন । সম্ভব হলে শুধু অসি চারা নির্বাচন করুন। নির্বাচিত চারার সমস্ত শিকড় ছুরি দিয়ে কেটে চারা রোপণের জন্য প্রস্তুত করুন ।
৪ । কলার জমি উত্তমরূপে লাঙল দিয়ে ৫/৬টি চাষ ও মই দিন মুগুর দিয়ে ঢেলা ভেঙে দিন ও হাতে আগাছা বেছে ফেলুন এবং মাটি সমতল করে তৈরি করুন ।
৫ । কলার জন্য ২-৩ মি. দূরত্বে ৭৫ সে.মি চওড়া এবং ৬০ সে.মি গভীর করে কোদাল দিয়ে) একর প্রতি জাত অনুসারে (৫৩৮-১২১০টি গর্ত তৈরি করুন । গর্ত সপ্তাহকাল খোলা অবস্থায় রেখে দিন । এরপর গর্তের মাটির সাথে ১৫ কেজি জৈব সার, খৈল ৫০০ গ্রাম, টিএসপি ৩০০ গ্রাম, মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে রাখুন । গর্ত ভরাট করার সময় উপরের মাটি নিচে এবং নিচের মাটি উপরে দিন।
৬। গর্তে সার প্রয়োগের পর ঝাঝরি দিয়ে সেচ দিন। মাটি উলট-পালট করে দিন। রোপণের দুই দিন পূর্বে পুনরায় মাটি উলট-পালট করে দিন । প্রতি গর্তে একটি করে চারা রোপণ করুন । রোপণকৃত চারার রাইজোম ১০-১৫ সে.মি, মাটির গভীরে স্থাপন করুন এবং উপ-কাণ্ড মাটির বরাবর বা সামাণ্য (১.৫-২.০ সে.মি) নিচে রাখুন ।
৭। চারা রোপণের পর মাটি ভালভাবে চেপে দিন। বয়স্ক গাছে বছরে ৪-৬ বার আগাছা বেছে দিন । সেচের পর জমিতে জো এলে চটা ভেঙে দিন এবং মাটি আলগা রাখুন । এরপর প্রতিটি সারির মাঝে ৩০ সে.মি চওড়া ও ২০ সে.মি গভীর নালা (কোদাল দিয়ে তৈরি করুন । এসব নালার মাটি তুলে গাছের সারি বরাবর বেড তৈরি করে দিন । এভাবে সেচ ও নিকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করুন ।
৮। জমিতে চারা রোপণের ২ মাস পর গাছ প্রতি ৮০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১৬০ গ্রাম এমপি সার উপরি প্রয়োগ করুন এবং ৪-৫ মাসপর ১৬০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১৬০ গ্রাম এমপি পুনরায় প্রয়োগ করুন । গাছের ৩০ সে.মি জায়গায় মাটি গোলাকার (বেন্ড) করে খুরপি । কোদাল দিয়ে আলগা করুন । সার ছিটিয়ে ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিন । রসের অভাব থাকলে সেচ দিন । চারা অবস্থায় ঝাঝরি দিয়ে এবং বড় গাছে ড্রেন পূর্ণ করে পানি দিয়েই সেচের কাজ চালাতে পারেন। বর্ষাকালে অতিরিক্ত পানি নিকাশের ব্যবস্থা করুন।
৯ । চারা জমিতে রোপণের ৪-৫ মাস পর থেকেই সাকার বের হতে থাকে । এসব সাকার বের হওয়ার সাথে সাথে মাটি বরাবর (ছুরি/কান্তে দিয়ে কেটে দিন। গাছে ফল পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্ত এভাবে সাকার কাটতে থাকুন । মুড়ি ফসল করতে চাইলে গাছে ফুল আসার পর একটি অসি চারা রেখে দিন (চিত্র দ্রষ্টব্য)। গাছে কাঁদি বের হলে প্রতিটি গাছে খুঁটি পুতে রশি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিন ।
১০। গাছের পচা, রোগাক্রান্ত পাতা কেটে ফেলে বাগান পরিষ্কার রাখুন। কাঁদি বের হওয়ার পর (পুরুষ ফুলসহ) ঝুলন্ত মোচাটি কেটে ফেলুন।
১১ । বিটল পোকা দমনের জন্য (১) বাগান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও আগাছামুক্ত রাখুন, (২) প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৪-৫ চা চামচ ম্যালাথিয়ন-৫৭ তরল ডায়াজিনন ৬০ তরল কীটনাশক গুলে ১০-১৫ দিন পর পর (পাতা ও ফলে) ভালোভাবে স্প্রে করুন, (৩) ২-৩ বছর শস্য পর্যায় করুন। (৪) কাদি ব্যাগিং করুন ।
১২ । ঘোড়া পোকা ও জাব পোকা দমনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করুন ।
১৩। রাস্ট এবং থ্রিপস দমনের জন্য- (১) রঙিন পলিথিন ব্যাগে কঁদি ঢেকে দিন, (২) পক্ষকাল পরপর তামাক চূর্ণ ছিটাতে পারেন এবং (৩) ১১ (২) এর অনুরূপ ব্যবস্থা নিন ।
১৪ । কাগু/গুড়ির উইভিল পোকা দমনের জন্য (১) আক্রান্ত গাছের খালে, কাণ্ড, গুড়ি তুলে এনে ধ্বংস করুন, (২) ২-৩ বছর (অমৃত সাগর/চাঁপা কলার চাষ না করা), শস্য পর্যায় করুন, (৩) ১১ (২) এর অনুরূপ ব্যবস্থা নিন ।
১৫ । পানামা রোগ দমন- (১) আস্ত গাছ, পাতা, চারা, কাণ্ড তুলে পুড়িয়ে ফেলুন। গর্তের মাটি পাড়ান, (২) ৩-৪ বছরের জন্য (সাগর, মেহের সাগর, সবরী, চাপা কলার চাষ না করা) শস্য পর্যায় অবলম্বন করুন ।
১৬ । গুচ্ছমাথা রোগ (বানচীটপ) দমনে- (১) আক্রান্ত গাছ উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলুন, (২) ১১ (২) এর অনুরূপ ব্যবস্থা নিন ।
১৭। সিগাটোগা (পাতার দাগ) দমনে- (১) আক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলুন, (২) আধুনিক উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করুন (আগাছা বালাইনিকাশের ব্যবস্থাসহ), (৩) জৈব সার অধিক ব্যবহার করুন, (৪) প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৪০-৪৫ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ গুলে গাছে ভালভাবে স্প্রে করে দিন ।
১৮ । প্রধান কাগু পচা রোগ দমনে প্রতি ১০ লিটার বার্গান্ডি মিকচার প্রে মেশিনে ভরে (৯৬ গ্রাম তুঁতে, ১২০ গ্রাম কাপড় ধোয়ার সোডা ও ১৯ লিটার পানি) পক্ষকাল পরপর ছিটান ।
১৯। রোপণের ১০-১৪ মাস সময়ের মধ্যেই ফল সংগ্রহ করতে পারেন। ফল যখন পুষ্ট, গোলাকার (কিনারাবিহীন হয়) ও পুষ্প শুকিয়ে যায় তখন কলার কাদি কেটে সংগ্রহ করুন। সংগ্রহের পর পচা, কীট ও রোগে আক্রান্ত এবং অপুষ্ট কলা বাছাই করে ফেলুন । দূরে পাঠাতে অর্থ পত্ব এবং কাছে পাঠাতে বাছাই করুন । পরিপক্ক কলা খোলা ও ঠান্ডা স্থানে (কাচা কলা) কাদি ঝুলিয়ে, কাদির গোড়ায় মোমের প্রলেপ দিয়ে বা হিমাগারে (১১ সে, তাপে) কয়েকদিন সংরক্ষণ করতে পারেন ।
সতর্কতা
১। কীট ও রোগবিহীন বাগান থেকে (অসি) চারা সংগ্রহ করতে হবে ।
২। যে সমস্ত এলাকায় শীতের তীব্রতা বেশি সেখানে শীতের পূর্বে চারা লাগালে ফুল/ফুল আসতে ২-৩ মাস দেরি হতে পারে ।
৩। কলার জন্য নিকাশের ভাল ব্যবস্থা এবং নিড়ানীকালে যাতে শেকড় না কাটে সেদিক দৃষ্টি রাখতে হবে । এবারে কাজের ধাপ অনুসরণ করে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন ।
প্রাসঙ্গিক তথ্য:
আনারস দ্বিবর্ষজীবী এবং একটি গাছ একবার মাত্র একটি ফুল দিয়ে থাকে । বাংলাদেশে ৩ জাতের আনারস চাষ হয় ।
যথা- (ক) হানিকুইন (খ) জায়েন্ট কিউ ও (গ) ঘোড়াশাল ।
ভালোজাতের চারা নির্বাচন: আনারস অঙ্গজ পদ্ধতিতেই বংশ বিস্তার করে থাকে। এর চারাকে সাকার বলে
আনারসের ৫ ধরনের সাকার হয়। যথা-
১) ক্রাউন সাকার বা কিরিট
২) ফ্লিপ সাকার বা বোটার চারা ৩। কান্ড সাকার বা কাণ্ডের কেকরী
৪) প্রাভ/সাকার বা গোড়ার ফেকরী
৫) স্টাম্প সাকার বা পাড়া
উপকরণ
১) চারা (২) সার (জৈৰ + রাসায়নিক) (৩) কীটনাশক (৫) স্প্রে যন্ত্র (৬) পানি (৭) লাঙল (৮) জোয়াল (৯) মই (১০) মুগুর (১১) খুরপি (১২) কোদাল (১৩) তুমি (১৪) ঝুড়ি ।
আনারস চাষ করার জন্য নিম্নের কাজ/ধাপ অনুসরণ করতে হবে:
১। আনারসের উন্নত জাত নির্বাচন করুন। প্রয়োজনীয় চারা (প্রায় ১৬-১৮ হাজার একরে) সংগ্রহ করুন।
২। আনারস চাষের জন্য উঁচু স্থান এবং সুনিষ্কাশিত উর্বর দোআশ মাটি নির্বাচন করুন।
৩। সংগৃহীত চাৱা থেকে বেছে নিয়োগ পার্শ্ব চারা নির্বাচন করুন। নির্বাচিত চারার নিচের দিক থেকে করেকটি পাভা (৫-৭টি) খুলে ফেলুন। চারাগুলো ১-২ সপ্তাহ রোেদ শুকিয়ে নিন । এছাড়াও প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২.০-২.৫ চা চামচ এরাটন-৬ ছত্রাকনাশক ফলে চারার গোড়া শাখেন করে নিন। এভাবে চারা প্রস্তুত করে জমিতে লাগান ।
৪। আনারসের জমি উত্তমরূপে লাগল দিয়ে ৪/৫টি চাষ ও মই দিন। মুগুর দিয়ে চেলা ভেঙে ফেলুন। আগাছা হাতে বেছে ফেলুন। ক্ষমি সমতল করে তৈরি করুন। শেষ চাষের সময় একর প্রতি ৮ টন গোবর ও ৮০-১০০ কেজি টিএসপি জমিতে প্রয়োগ করে মাটিতে মিশিয়ে দিন।
৫। আনারসের জন্য প্রথমে বেড তৈরি করে নিন। ৯০ সে.মি. (৩) পরপর ৯০ সে.মি (৩") বেড তৈরি করুন। দুটি পাশাপাশি বেডের মাঝে ৯০ সে.মি (৩) চওড়া ও (১০/১৫ সে.মি (৪"/৬") গভীর নালা তৈরি করুন। নালার মাটি কোদাল দিয়ে তুলে দিন এবং বেড তৈরি করুন। এবারে ঘোড়া সারি পদ্ধতিতে প্রতি বেডে ৬০ সে.মি (২") পরপর সারি করে ২৫-৩০ সে.মি (১০"-১২") দূরে দূরে চারা রোপণ করুন ।
৬। এরপর প্রতিটি গর্তে একটি করে শোধন করা সতেজ চারা রোপণ করুন। চারা এমনভাবে রোপণ করুন যাতে ভেতরের কচি অংশ ২-৩ সে.মি মাটির উপরে থাকে । চারা লাগিয়ে গোড়ার মাটি হাতে ভালোভাবে চেপে শক্ত করে দিন ।
৭ । গাছ সবল হয়ে উঠলে প্রয়োজনে সেচ দিয়ে নিড়িয়ে আগাছা বেছে দিন এবং মাটি নরম ও আলগা রাখুন । সেচের পর জো এলে জমির চটা ভেঙে দিন । এছাড়াও মাঝে মাঝে নিড়িয়ে আগাছা তুলে ফেলুন । মাটি আলগা এবং ঝুরঝুরে রাখুন যাতে সহজে বাতাস চলাচল করতে পারে ।
৮ । বর্ষার পূর্বে ও পরে দুই দফায় সার উপরি প্রয়োগ করুন । প্রতিবার হেক্টর প্রতি ২৫০-৩০০ কেজি ইউরিয়া ও ৩০০-৩৫০ কেজি এমপি সার প্রয়োগ করুন। চারার ১০-১৫ সে.মি দূর দিয়ে মাটি নিড়িয়ে মাটি আলগা করে সার ভালভাবে মিশিয়ে দিন । নালা ভরে পানি রেখে সেচ দিন। শুকনো মৌসুমে ২০ দিন পরপর সেচ দিন । বর্ষাকালে অতিরিক্ত পানি নিকাশের ব্যবস্থা করুন ।
৯ । আনারসের একাধিক চারা জন্মায় । প্রতি গাছে দুটি চারা রেখে বাকীগুলো কেটে দিন ।
১০ । ছাতরা পোকা দমনে প্রতি ১০ লিটার পানিতে চা চামচের ৪-৫ চামচ ম্যালাথিয়ন-৫৭ তরল কীটনাশক গুলে গাছে ভালভাবে স্প্রে করে দিন ।
১১ । কাণ্ড পচা (হার্টরট) রোগ দমনে- (১) গাছের গোড়ায় পানি জমতে দিবেন না, (২) চারা রোপণের পূর্বে শাধেন করে রোপণ করুন, (৩) প্রতি লিটার পানিতে ৩৫-৪০ গ্রাম কপার অক্সিক্লোরাইড-৫০ পাউডার গুলে গাছে ভালভাবে স্প্রে করে দিন ।
১২। রোপণের ১৭/১৮-২৪ মাসের মধ্যে ফল পাকে। ফল যখন পরিপক্ক হয় (কিছু হলুন রং এর হয়) তখন কেটে সংগ্রহ করুন । সংগ্রহের পর ছোট-বড়, ভালো-খারাপ বাছাই করে ফেলুন । দূরে চালান দিতে হলে একটু অধপক্ক ফল সংগ্রহ করুন । ফ্রিজে পাকা ফলকে ৪°-১০° সে. (৪০/৫০° ফা.) তাপে এক মাস সংরক্ষণ করতে পারেন। আনারস থেকে জুস, কোয়াস, জেলি, ভিনিগার তৈরি করেও সংরক্ষণ করতে পারেন। এ ছাড়াও লবণ/চিনি যোগে টিনজাত করেও রাখতে পারেন ।
সতর্কতা
১। ভারী মাটিতে আনারসের আকার বড় হয় কিন্তু হালকা মাটিতে ফলন ভালো হয়ে থাকে ।
২। বর্ষায় নিকাশের ভাল ব্যবস্থা রাখতে হবে ।
৩। পরিচর্যা কালে যাতে গাছের পাতা না ভাঙে তারদিকে খেয়াল রাখতে হবে ।
৪ । ফলে আঘাত লাগলে সহজেই নষ্ট হয়ে যায়, তাই সাবধানে পরিবহণ করতে হয় ।
প্রাসঙ্গিক তথ্য
পেঁপের পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদা গাছে থাকে । পেঁপে পরপরাগায়িত এবং বীজ দ্বারা বংশ বিস্তার করে থাকে বলে অসংখ্য প্রকার পেঁপে দেখা যায়। বিশেষ কোন পেঁপের জাত আবাদ ও সংরক্ষণ করতে হলে নিয়ন্ত্রিত পরাগায়ণের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন করা উচিত । ভালো জাতের চারা নির্বাচন-পেঁপের চারা তিন ভাবে উৎপাদন করা যায় । যথা- বেড়ে, পটে ও সরাসরি জমিতে। আদর্শ পেঁপে গাছের কতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার । যথা- গাছ বেটে জাতের হতে হবে । তাড়াতাড়ি ফল ধরতে হবে । একটি কক্ষে একটি করে ফল থাকবে । গাছে সমান ভাবে ফল হবে ।
বাংলাদেশে কয়েকটি অনুমোদিত বিদেশি পেঁপের জাত পাওয়া যায়। যেমন- (ক) বেঁটে-ওয়াশিংটন থাইডোয়ার্ফ হানিডিউ, রাচি, পুষা, শিমলা ইত্যাদি । (খ) লম্বা জাত- সেলো, বাংলাদেশে পেঁপের একটি মাত্র জাত আছে যার নাম শাহী পেঁপে ।
উপকরণ
(১) বীজ (২) সার (জৈব-রাসায়নিক) (৩) কীটনাশক (৪) ছত্রাকনাশক (৫) স্প্রে যন্ত্র (৬) পানি (৭) লাঙ্গল (৮) জোয়াল (৯) মই (১০) মুগুর (১১) খুরপি (১২) ছুরি (১৪) ঝুড়ি (১৫) কলার খোল (১৬) রশি (১৭) বেড়া (১৮) কাতে ।
পেঁপে চাষ করার জন্য নিম্নের কাজ /ধাপ অনুসরণ করতে হবে।
১। পেঁপের উন্নত জাত নির্বাচন করুন । প্রয়োজনীয় বীজ (৭০-৮০ গ্রাম/ একরে) সংগ্রহ করুন ।
২। পেঁপে চাষের জন্য উঁচু স্থান এবং সুনিষ্কাশিত দোঁআশ মাটি নির্বাচন করুন ।
৩। সংগৃহীত চারা থেকে বেছে নিরোগ এবং সুস্থ সবল চারা নির্বাচন করুন । চারা তৈরির জন্য প্রথমে বীজকে কাপড়ের পুটুলিতে বেঁধে ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে নিন। ১৩ মি. মাপে (৩-৪ টি) বীজতলা তৈরি করুন। প্রতি বীজতলায় ২০-২৫ গ্রাম বীজ বুনে দিন। বীজ বপনের পূর্বে বীজকে শোধন করে নিন । বীজ বপনের পর বীজ তলা গুড়া মাটি বা জৈব সার ও খড়কুটা দিয়ে বীজতলা ঢেকে দিন । বীজ গজালে খড়কুটা সরিয়ে ফেলুন ।
৪ । বীজ গজানোর পর মাঝে মাঝে সেচ (৩-৪ দিন পর পর বিকেলে) দিন । আগাছা হাতে তুলে ফেলুন । বীজতলায় মাটি নিডিয়ে ঝরঝরে ও নরম রাখুন। এভাবে ৬-৭ সপ্তাহ পর্যন্ত চারাকে যত্ন করে বড় (২০-২৫ সে.মি) করুন। এছাড়াও ভাল জাতের পুরানো গাছ থেকে মাউন্ড দাবা কলম করেও চারা সংগ্রহ করতে পারেন ।
৫। পেঁপে জমি লাঙ্গল দিয়ে ভালভাবে ৫/৬টি চাষ ও মই দিন । আগাছা বেছে ফেলুন। মুগুর দিয়ে ঢেলা ভেঙে ফেলুন । জমি সমতল করুন ।
৬ । জমি তৈরির পর ২.৫ মি. দূরত্বে কোদাল দিয়ে ৯০ সে.মি চওড়া ও ৬০ সে.মি গভীর করে (৭৭৪টি) গর্ত তৈরি করুন । গর্ত সপ্তাহকাল খোলা অবস্থায় রেখে দিন। এরপর প্রতি গর্তে ২০ কেজি জৈব সার, ৫০০ গ্রাম খৈল, ৪০০ গ্রাম টিএসপি ও ১০০ গ্রাম এমপি সার মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে মাদা তৈরি করে রাখুন । গর্ত ভরাট করার সময় উপরের মাটি নিচে এবং নিচের মাটি উপরে নিন । এর ১০-১৫ দিন পর গর্তে চারা রোপণ করুন ।
৭ । বীজতলা থেকে সুস্থ সবল ও বেশি পাতাযুক্ত চারাগুলো সাবধানে মাটি/শিকড়সহ তুলে আনুন । প্রতি মাদায় ২০ ২৫ সে.মি ব্যবধানে (ত্রিভুজাকারে) ৩টি চারা রোপণ করুন । চারা বীজতলায় যতটুকু মাটির নিচে ছিল ঠিক ততটুকুই পুঁতে দিন । চারার পাশের মাটি হাতে হালকাভাবে চেপে বসিয়ে দিন । প্রতিটি চারা ছোট কাঠি পুতে রশি দিয়ে (আলাদা ভাবে) বেঁধে দিন । ঝাঝরি দিয়ে সেচ দিন । চারার গোড়ার দিকে কিছু পাতা ছেটে ফেলুন । ৩-৪ দিন পর্যনত কলার খালে দিয়ে ছায়া ও সকাল বিকাল ঝাঝরি দিয়ে হালকা সেচ দিন। এরপর ৭ দিন বিকেলে সেচ দিন।
৮ । চারার আশেপাশে আগাছা জন্মালে নিড়িয়ে তুলে ফেলুন। জমির মাটি নরম ও আলগা রাখুন। সেচের পর জো এলে চটা ভেঙে দিন । বয়স্ক গাছ নিড়িয়ে আগাছা মুক্ত রাখুন । প্রতি দুইটি সারির মাঝে কোদাল দিয়ে ৩০ সে.মি চওড়া ও ২০ সে.মি গভীর করে নালা তৈরি করে মাটি দুই দিকে তুলে দিন । গাছে ফুল দেখা দিলে প্রতি মাদায় একটি করে সতেজ উভয় লিঙ্গ/স্ত্রী গাছ রেখে বাকি দুটি চারা গাছ মাটি বরাবর কেটে ফেলুন । তবে প্রতি ২০-২৫ টি গাছের জন্য একটি করে পুরুষ গাছ রাখুন ।
৯ । সার উপরি প্রয়োগ দু'দফায় করুন । প্রথমবার চারা রোপণের ৪-৫ সপ্তাহ পর এবং দ্বিতীয়বার গাছে ফুল ধরা (৩ মাস) শুরু করলে প্রয়োগ করুন। প্রতিবারে ২০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ২৫০ গ্রাম এমপি প্রয়োগ করুন ।
১০ । সার প্রয়োগের জন্য চারার গোড়ার (৩০ সে.মি দূরে) চারদিকে দুপুরে যতদূর ছায়া পড়ে সে অংশের মাটি নিড়িয়ে আলগা করুন । সার ছিটিয়ে ভালোভাবে মাটিতে মিশিয়ে দিন। রস কম থাকলে সেচ দিন। নালা ভরে পানি দিয়ে সেচের কাজ সমাধা করতে পারেন। বর্ষায় অতিরিক্ত পানি নিকাশের দিকে খেয়াল রাখুন ।
১১ । পেঁপে গাছে অনেক ফল ধরে । কিছু কিছু ফল ছিড়ে পাতলা করে দিন । বর্ষাকাল শুরুর সাথে সাথে গাছের গোড়ায় কোদাল দিয়ে মাটি তুলে দিন ।
১২ । ফলের মাছি দমনে- (১) আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলুন, (২) প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৩০ গ্রাম ডিপটেরেক্স -৮০ গুলে ৮-১০ দিন পরপর ফলে স্প্রে করুন ।
১৩। কাও/গোড়া পচা রোগ দমনে- (১) পানি নিকাশের ব্যবস্থা করুন, (২) উঁচু জমিতে চাষ করুন, (৩) আক্রান্ত গাছ ধ্বংস করে ফেলুন, ৪) সুস্থ গাছে ও রোগের প্রাথমিক দিকে প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৩০-৩৫ গ্রাম কপার অক্সিক্লোরাইড-৫০ পাউডার গুলে পক্ষকাল পরপর গাছে স্প্রে করুন, (৫) বীজ শোধন করে বপন করুন।
১৪ । পাতা ও ফল পর্চা রোগ দমনে- (১) ফল ও কাণ্ড রোদ থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করুন । মরচে ধরা রোগ দমনে-(২) রোগাক্রান্ত ফল পাতা তুলে পুড়িয়ে ফেলুন ।
১৫ । পাতার দাগ পড়া দমনে কপার অক্সিক্লোরাইড স্প্রে করুন।
১৬ । পেঁপে মোজাইক (ভাইরাস) দমনে- (১) আক্রান্ত গাছ উপড়ে পুড়ে ফেলুন, (২) ভাইরাসমুক্ত বীজ সংগ্রহ করুন। দীর্ঘ শস্য পর্যায় অবলম্বন করুন ।
১৭ । গাছে থাকা অবস্থায় পেঁপে হলুদ রং ধরলে (বা আঠা ঘন ভাব ধরলে ফল পেড়ে নিন । রোপনের ১০-১২ মাস পর সংগ্রহ করতে পারেন। সংগ্রহের পর পঁচা, ভাল, খারাপ, ছোট-বড় বেছে নিন । ঝুড়িতে খড়/পাতা বিছিয়ে সাবধানে পেঁপে বাজারে পাঠান বা দূরে চালান দিন । হালুয়া, মোরব্বা, জ্যাম, জেলি তৈরি করে সংরক্ষণ করতে পারেন । চিত্র ফুল/ফল ও রোপণ পদ্ধতি দ্রষ্টব্য ।
সতর্কতা
১ । শীতের সময় বীজ গজাতে ৪/৫ সপ্তাহ লাগতে পারে । সদ্য সংগৃহীত বীজ থেকে গজানোর হার দ্রুততর ও গজানোর সংখ্যা বেশি হয় ।
২। উত্তম নিকাশের ব্যবস্থা উত্তম ফল দানে সহায়ক ।
৩। কলমের চারা/এফ-১ (হাইব্রিড) (উভয়লিঙ্গ) প্রতি গর্তে একটি চারা দেওয়া চলে ।
৪ । ইউরিয়া সার বেশি প্রয়োগ ভাল নয় । লাল মাটিতে ২৫০ গ্রাম/গর্তে চুন দেয়া ভাল ।
প্রাসঙ্গিক তথ্য
পেয়ারা এমন একটি ফল যার মধ্যে একাধিক গুণের বিরল সমন্বয় ঘটেছে যা খুব কম ফলেই লক্ষ করা যায় । ইহা দ্রুত বর্ধনশীল এবং অপেক্ষাকৃত কম যত্নেই যে কোন স্থানে জন্মানো যায় । সাধারণত বীজ ও কলম দিয়ে বংশ বিস্তার করা হয় । বীজের গাছের ফলের গুণগত মাণ ঠিক থাকে না, বিধায় কলমের চারাই উত্তম । গুটি কলম, জোড় কলম, চোখ কলম দিয়ে বাগান করাই উত্তম ।
উপকরণ
(১) বীজ/চারা (২) সার (জৈব ও রাসায়নিক) (৩) কীটনাশক (৪) ছত্রাকনাশক (৫) স্প্রে যন্ত্র (৬) পানি ( ৭ ) লাঙল (৮) জোয়াল (৯) মই (১০) মুগুর (১১) খুরপি (১২) ছুরি (১৩) পলিথিন (১৪) সিকেচার (১৫) খুঁটি (১৬) রশি (১৭) করাত (১৮) ঘেরা ও খাচা (১৯) টিন (২০) ঝাঝরি (২১) বালি ২২) বাঁশ (২৩) ঝুড়ি (২৪) সিরিঞ্জ (২৫) তুলা (২৬) জাল (২৭) আলকাতরা / কেরোসিন (২৮) কোদাল ।
পেয়ারা চাষ করার জন্য নিম্নের কাজ। ধাপ অনুসরণ করতে হবে
১। পেয়ারার উন্নত জাত নির্বাচন করুন। প্রয়োজনীয় বীজ/চারা (কলমের চারা ১৯৪টি / একরে) সংগ্রহ করুন।
২। পেয়ারা চাষের জন্য উঁচু স্থান এবং উর্বর সুনিষ্কাশিত গভীর বেলে-দোঁআশ মাটি নির্বাচন করুন ।
৩ । উন্নত জাতের গাছ থেকে থাকলে গুটি কলম করে চারা তৈরি করুন ।
৪ । পেয়ারার জমি ভালভাবে লাঙল দিয়ে ৪/৫টি চাষ ও মই দিন । মুগুর দিয়ে ঢেলা ভেঙে ফেলুন। হাতে আগাছা বেছে ফেলুন। জমি সমতল করুন।
৫ । কলমের চারা ৫মি. (১৫) দূরত্বে রোপণ করুন। জমিতে ৫ মি. দূরত্বে ৬০ সে.মি চওড়া ও ৬০ সে.মি গভীর করে (১৯৪টি গর্ত তৈরি করুন ও গর্ত সপ্তাহকাল খোলা অবস্থায় রেখে দিন । এরপর গর্তে জৈব সার ১০ কেজি, খৈল ৫০০ গ্রাম, টিএসপি ৫০০ গ্রাম, ছাই ৪ কেজি মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে রাখুন । গর্ত ভরাট করার সময় উপরের মাটি নিচে এবং নিচের মাটি উপরে দিন। এর ১০-১৫ দিনপর গর্তে চারা রোপণ করুন ।
৬ । চারা রোপণের জন্য মাটির বলটি আস্ত রেখে সাবধানে টব থেকে চারা বের করুন । চারা পূর্বে যতটুকু মাটির নিচে ছিল ঠিক ততটুকুই পুঁতে দিন। চার পাশে হাতে চেপে মাটি বসিয়ে দিন। ঘেরা ও বেড়া দিয়ে বেঁধে দিন ।
৭ । চারা গাছের গোড়ায় আগাছা জন্মালে নিড়িয়ে তুলে ফেলুন। গোড়ার মাটি আলগা রাখুন । সেচের পর জো এলে চটা ভেঙে দিন । বয়স্ক গাছের ক্ষেত্রে বর্ষার আগে ও পরে কোদাল / লাগুল দিয়ে মাটি আলগা করে দিন । এছাড়াও মাঝে মাঝে নিড়িয়ে মাটি নরম ও আলগা রাখুন ।
৮। পেয়ারা গাছে সার উপরি প্রয়োগ দু'দফায় করুন। অর্ধেক সার বসন্তকালে ও বাকি অর্ধেক শরৎকালে প্রয়োগ করুন।
৯ । চারা রোপণের পরের বছর গাছ প্রতি গোবর ১০ কেজি, ইউরিয়া ২০০ গ্রাম, টিএসপি ১৫০ গ্রাম ও এমপি ২০০ গ্রাম প্রয়োগ করুন । এরপর প্রতি বছর গোবর ২০ কেজি, ইউরিয়া ৫০০ গ্রাম, টিএসপি ৪৫০ গ্রাম ও এমপি ৩৫০ গ্রাম প্রয়োগ করুন। পাঁচ বছর পর বা তদূর্ধ বয়ক গাছে গোবর ৪০ কেজি, ইউরিয়া ১.৫ কেজি, টিএসপি ১ কেজি ও এমপি ১ কেজি প্রয়োগ করুন। এসব সার দু' দফায় (৮ নং বর্ণিত নিয়েমে) প্রয়োগ করুন।
১০ । গাছের গোড়ার (৩০-৪০ সে.মি) কিছু দূর থেকে শুরু করে দুপুরে যতটুকু ছায়া পড়ে সে অংশের মাটি কোদাল/লাঙল দিয়ে আলগা করুন। সার ছিটিয়ে ভালভাবে মাটিতে মিশিয়ে দিন। সার মাটি চাপা দিন ।
১১। সার প্রয়োগের পর গাছে থালা পদ্ধতিতে সেচ দিন। চারা গাছে সপ্তাহে ২ বার, বয়স্ক গাছে বর্ষাকাল বাদে ১৫ দিন পরপর এবং ফল আসার সময় ৮/১০ দিন পর সেচ দিন। বর্ষায় পানি নিকাশের ব্যবস্থা করুন।
১২। গাছের কাঠামো গঠনের জন্য গোড়ার ১ মি. এর মধ্যে কোন ডালপালা গজালে হেঁটে ফেলুন। এরপর চারিদিকে প্রসারিত ৩/৪ টি ডালপালা রেখে বাকিগুলো হেঁটে দিন । এছাড়াও গাছের ফেকরি, শুকনো, মরা, রোগাক্রান্ত ডালপালা হেঁটে দিন। ডালসহ ফল সংগ্রহ করতে পারেন।
১৩ । কাণ্ডের মাজরা পোকা দমন-লিচুর বর্ণিত উপায়ে দমন করুন ।
১৪ । ফলের মাছি দমনের জন্য- (১) আক্রানত ফল এবং ফলের গায়ে লেগে থাকা ডিম ধ্বংস করুন, (২) প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৩০ গ্রাম ডিপটেরেক্স-৮০ গুলে ৮-১০ দিন পর পর ফলে স্প্রে করুন।
১৫ । শোষক ও জাব পোকা দমন প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৪/৫ চা চামচ ম্যালাথিয়ন-৫৭ কাটনাশক গুলে গাছে স্প্রে করুন ।
১৬ । ফলের ক্ষত ও ফোস্কা (এনথ্রাকনাসে) রোগ দমন- (১) আক্রান্ত ফল ধ্বংস করে ফেলুন, (২) প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৪০/৫০ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ পাউডার গুলে পক্ষ কাল পরপর ফলে/ঘাতে প্রে করুন ।
১৭ । গাছের মড়ক (উইন্ট) দমন- (১) আক্রান্ত গাছ ধ্বংস করুন, (২) বেশি করে জৈব সার প্রয়োগ করুন, (৩) নিকাশের ভালো ব্যবস্থা করুন, (৪) আক্রমণের প্রাথমিক স্তরে ডাইথেন এম-৪৫ স্প্রে করুন (১৬ নং বর্ণিত উপায়) ।
১৮ । ফল পরিপক্ক হওয়ার পর (হালকা হলুদ বা ফিকে সবুজ রং ধরার পর) ছিড়ে সংগ্রহ করুন । সংগ্রহ করে ভালো খারাপ বাছাই করুন ঝুড়িতে খড়/পাতা বিছিয়ে পেয়ারা স্তরে স্তরে সাজান। প্রতি সতরের মাঝে খড় বিছিয়ে দিন এবং ঝুড়িতে ভরে বাজারজাত করুন। জ্যাম, জালি তৈরি করে সংরক্ষণ করতে পারেন ।
সতর্কতা
১। পেয়ারা শুষ্কতা সহ্য করতে পারে কিন্তু জলাবদ্ধতা সহ্য করে না ।
২। ফল বৃদ্ধি হওয়ার সময় জমিতে রসের অভাব ফল বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ।
৩ । গাছের বয়স ২৩ বছর হলে, নতুন গাছ লাগানোই উত্তম ।
প্রাসঙ্গিক তথ্য
বাংলাদেশে অসংখ্য জাতের কুল পাওয়া যায় । তবে অধিকাংশ জাতই নিকৃষ্ট মানের খুব কম সংখ্যক কুলের ভালো জাত পাওয়া যায় । সুপরিচিত উন্নত জাতের মধ্যে রয়েছে- নারিকেলী, কুমিলা, আপেল ও বাউকুল । বীজ, অঙ্গ সংযোজন ও কুঁড়ি সংযোজনের মাধ্যমে কুলের বংশ বিস্তার করা যায়। বীজের গাছের গুণাগুণ অনিশ্চিত বলে কখনো তা লাগানো উচিত নয় । কুড়ি সংযাজনই কুলের বংশ বিস্তারের সবচেয়ে উপযোগী পদ্ধতি ।
উপকরণ
(১) বীজ/চারা (২) সার (জৈব+রাসায়নিক) (৩) কীটনাশক (৪) ছত্রাকনাশক (৫) স্প্রে যন্ত্র (৬) পানি (৭) লাঙল (৮) জোয়াল (৯) মই (১০) মুগুর (১১) খুরপি (১২) কোদাল (১৩) করাত (১৪) চাকু (১৫) পলিথিন (১৬) টব (১৭) সিকেচার (১৮) ঝুড়ি (১৯) ঘেরা ও বেড়া ।
কুল চাষ করার জন্য নিম্নের কাজধাপ অনুসরণ করতে হবে।
১। কুলের উন্নত জাত নির্বাচন করুন । প্রয়োজনীয় বীজ/চারা (১৭০ টি/ হেক্টরে) সংগ্রহ করতে হবে ।
২। কুল চাষের জন্য উঁচু স্থান এবং উর্বর দোআশ মাটি নির্বাচন করতে হবে ।
৩। সংগৃহীত বীজ/চারা, নার্সারি বেডটবে রোপিত বীজ/চারার ১০/১২ মাস বয়স হলে (মাঘ-ফালগুনে) মাটি বরাবর কেটে দিন । কাটার পর গাছ থেকে বেশ কিছু ডাল গজাবে তা থেকে সতেজ দুটি ডাল রেখে বাকিগুলো কেটে দিন । এরপর গজানো ডাল ২৫-৩০ সে.মি লম্বা হলে মাঝামাঝি অংশে তালি কলম করে নিতে হবে ।
৪ । তারপর ঐ ডাল দুটিতে ১-১.৫ সে.মি চওড়া ও ২-২.৫ সে.মি লম্বা করে ছাল বাকল কেটে উঠিয়ে নিন । এবার একই মাপের কুঁড়িসহ উন্নত গাছের ছাল কেটে এনে ঐস্থানে বসিয়ে দিন। কুঁড়ির মুখটি খোলা রেখে পলিথিন ফিতা দিয়ে বেধে দিন । ৮/১০ দিনপর কুঁড়িটি বড় হওয়া শুর করলে জোড়ার ২/৩ সেমি উপরে (স্টক) ডাল দুটির আগা সিকেচার দিয়ে কেটে ফেলুন। এভাবে চারা তৈরি করে নিন । ২/১ মাস পরেই গাছটি জমিতে রোপণ করতে পারবেন । জোড়ার নিচ থেকে কোন ডাল বের হলে কেটে দিতে হবে ।
৫ । কুলের জমি ভালভাবে লাঙল দিয়ে ৩/৪টি চাষ ও মই দিন। হাতে আগাছা বেছে ফেলুন । জমি সমতল করতে হবে।
৬ । কুলের চারা ৮ মি. (২৫) দূরত্বে রোপণ করুন । জমিতে ৮ মি. দূরত্বে ৯০ সি.মি চওড়া ও ৯০ সে.মি গভীর করে কোদাল দিয়ে গর্ত তৈরি করুন । গর্ত সপ্তাহকাল খোলা অবস্থায় রেখে দিন। এরপর প্রতি গর্তে জৈব সার ১০ কেজি, খৈল ২৫০ গ্রাম, টিএসপি ১৫০ গ্রাম, ছাই ৫ কেজি মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে রাখুন । গর্ত ভরাট করার সময় উপরের মাটি নিচে এবং নিচের মাটি উপরে দিন। এর ১০-১৫ দিনপর প্রতি গর্তে চারা রোপণ করতে হবে।
৭। মাটির বলটি না ভেঙে টব থেকে সাবধানে চারা বের করে রোপণ করুন। চারা পাশে হাতে চেপে মাটি বসিয়ে দিন । একটি খুঁটি পুঁতে চারাটি বেঁধে দিন। ঝাঝরি দিয়ে সেচ দিন। চারাটি বেড়া দিয়ে ঘিরে দিন । চারা মাটির সাথে না লাগা পর্যন্ত ৪/৫ দিন মাঝে মধ্যে সেচ দিতে হবে ।
৮ । চারা গাছের গোড়ায় আগাছা হলে নিড়িয়ে তুলে ফেলুন। গোড়ার মাটি আলগা রাখুন । সেচের বৃষ্টির পর মাটিতে দিন। সপ্তাহে একবার নিড়ান। বয়স্ক গাছ মাঝে মধ্যে নিভিয়ে দিন । বর্ষার আগে ও পরে কোদাল (লাঙ্গল দিয়ে জমির মাটি আগলা করে দিতে হবে । অতিরিক্ত পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে ।
৯ । কুলের চারা রোপণের পরের বছর গাছ প্রতি ১০ কেজি গোবর সার, ইউরিয়া ২০৫ গ্রাম, টিএসপি ২৫০ ও এমপি ২৫০ গ্রাম প্রয়োগ করুন । পাঁচ বছর পর বা বয়স্ক গাছে জৈব সার ৩০ কেজি ইউরিয়া ১ কেজি, টিএসপি ১.৫ কেজি ও এমপি ১ কেজি প্রয়োগ করুন। এসব সার প্রতি বছর বর্ষার আগে অর্ধেক ও বর্ষার পরে অর্ধেক পরিমাণ প্রয়োগ করতে হবে।
১০ । গাছের গোড়া থেকে (চারিদিকে ৩০-৬০ সে.মি বাদ রেখে যতদূর পর্যন্ত দুপুরে রৌদ্রের ছায়া পড়ে সে অংশের মাটি কোদাল /লাগুল দিয়ে আলগা করুন। সার মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে ।
১১ । সার প্রয়োগের পর গাছে থালা পদ্ধতিতে সেচ দিন । চারা গাছ সপ্তাহে ১ বার, বয়স্ক গাছে ফুল /ফল ধরার সময়ে ১৫/২০ দিন পরপর সেচ দিন। বর্ষায় নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।
১২। কলমের গাছের জোড়ার নিচের অংশ থেকে যত ডাল পালা গজাবে তা হেঁটে দিন । চার পাঁচটি প্রসারিত ডালপালা রেখে বাকিগুলো হেঁটে দিন। ফল সংগ্রহের পর বসন্তকালে) ২ সে.মি ব্যাসযুক্ত ডালপালা হেঁটে দিন । এছাড়াও শুকনো, মরা, রোগাক্রান্ত ডালপালা হেঁটে দিতে হবে ।
১৩ । কুলের ছিদ্রকারী পোকা, উইভিল, মিলিবাগ ও বিছা পোকা দমনের জন্য প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৪/৫ চা চামচ ডায়াজিনন-৬০ তরল/ মেটাসিসটকস-২৫ তরল কীটনাশক গুলে গাছে, ফলে ও পাতায় ভালোভাবে (১০/১২ দিন পরপর ২/১ দফায়) স্প্রে করতে হবে ।
১৪ । পাউডারী মিলডিউ দমনের জন্যপ্রতি ১০ লিটার পানিতে ৩৫/৪০ গ্রাম থিওভিট-৮০ পাউডার গুলে পক্ষকাল পরপর ফলে ও গাছে স্প্রে করতে হবে ।
১৫ । শোষক ও জাব পোকা দমন- প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৪/৫ চা চামচ ম্যালাথিয়ন-৫৭ কীটনাশক গুলে গাছে স্প্রে করতে হবে।
১৬। ফল পরিপক্ক হওয়ার পর (হালকা হলুদ রং ধরার পর) পেড়ে সংগ্রহ করুন । সংগ্রহের পর পোকা ধরা, পঁচা, খারাপ, ফল বাছাই করুন । ঝুড়িতে খড় বিছিয়ে সাবধানে ফল বাজারে বা দূরে চালান দিন । ফল থেকে আচার, চাটনী ইত্যাদি তৈরি করে সংরক্ষণ করতে পারেন । স্বাভাবিক তাপমাত্রায় (২৫°- ৩০° সে.) সপ্তাহ কাল এবং হিমাগারে (৪° সে.) ৩৪ সপ্তাহ কাল সংরক্ষণ করতে পারেন ।
সতর্কতা
১। ফুল ও ফলন বাড়াতে অতিরিক্ত ডাল ছাঁটাই, সার প্রয়োগ ও সেচ অবশ্য করণীয় ।
২। উন্নত জাতে পাউডারি মিলডিউ এর উপদ্রব বেশি তাই সতর্ক থাকতে হবে এবং নিরোধমূলক স্প্রে করতে হবে ।
প্রাসঙ্গিক তথা
নারিকেল একটি বহুবর্ষজীবী, একবীজ পত্রী, এক কাণ্ড বিশিষ্ট গুচ্ছমূল উদ্ভিদ। নারিকেলের জাত গুলোকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয় । যথা- (১) টিপিকা জাত (লম্বা শ্রেণি) (২) জাভানিকা জাত (মাঝারী লম্বা শ্রেণি) এবং (৩) বামন বা নানা জাত (খাটো শ্রেণি) । নারিকেলের বংশ বিস্তারের জন্য উৎকৃষ্ট গুণাবলি সম্পন্ন মাতৃগাছ নির্বাচন করা উচিত । নারিকেলের বংশ বৃদ্ধি বীজ দ্বারা হয়ে থাকে । নারিকেলের বীজ থেকে উন্নতমানের চারা উৎপাদন করে বাগানে রোপণ করতে হয় ।
উপকরণ
(১) বীজ (২) সার (জৈব ও রাসায়নিক) (৩) কীটনাশক (৪) ছত্রাকনাশক (৫) প্রে যমত্র (৬) পানি (৭) ঝাঝরি (৮) লাঙল (৯) জোয়াল (১০) মই (১১) মুগুর (১২) খুরপি (১৩) কোদাল (১৪) ঝুড়ি (১৫) দা (১৬) রশি (১৭) বস্তা (১৮) বেড়া ।
নারিকেল চাষ করার জন্য নিম্নের কাজ/ ধাপ অনুসরণ করতে হবে।
১। নারিকেলের উন্নত জাত নির্বাচন করুন। নির্বাচিত মাতৃগাছ থেকে সতেজ, সুপক্ক, খোসাসহ, শাস পুরু, বড়, যথেষ্ট পানি আছে, কীট/রোগ মুক্ত এমন ফল (১৫০টি/হেক্টরে) সংগ্রহ করুন ।
২। নারিকেলের জন্য উঁচু স্থান এবং সুনিষ্কাশিত উর্বর দোঁআশ/এঁটেল দোআশ/বেলে দোআশ মাটি নির্বাচন করুন।
৩ । চারা তৈরির জন্য সেচ নিকাশের সুবিধাযুক্ত স্থানে বেলে দোঁআশ ধরনের মাটিতে গভীরভাবে চাষ করে ২মি (৬) প্রস্থ ও ৩ মি. (১০) লম্বা ও ১৫-১২ সেমি. উঁচু করে (২/৩টি) বীজতলা তৈরি করুন। প্রতি বীজতলায় ৭৫/৯০ গ্রাম টিএসপি ও ১০০-১২০ গ্রাম এমপি সার প্রয়োগ করে ভালভাবে মিশিয়ে দিন। সংগৃহীত বীজ এক মাসের মধ্যেই রোপণ করুন । বীজের মুখের খোসাটি খুলে ফেলুন। প্রতি বীজতলায় ৩০ সে.মি দূরত্বে সারি টেনে ৩০ সে.মি পরপর পার্শ্ব ভাবে চিত্র (দ্রষ্টব্য) বীজ বপন (৪০/৫০ টি) করুন। বীজ সম্পূর্ণ মাটি দিয়ে না ঢেকে পিঠের সামাণ্য খোলা রাখুন । বীজ বপনের পর বীজতলা খড়কুটা/নারিকেলের পাতা/ ছোবড়া দ্বারা ঢেকে দিন । বৃষ্টি না হলে একদিন পরপর ঝাঝরি দিয়ে সেচ দিন । বীজতলায় আগাছা জন্মালে নিড়িয়ে তুলে ফেলুন । এভাবে যত্ন করে ৩/৪ মাসের মধ্যে চারা না গজালে তা বাতিল করে তুলে ফেলুন । ৯-১২ মাস বয়ক সুস্থ সবল চারা জমিতে রোপণের জন্য বাছাই করুন ।
৪ । নারিকেলের জমি লাঙল দিয়ে ভালভাবে ৩/৪ টি চাষ ও মই দিন । মুগুর দিয়ে ঢেলা ভেঙে দিন । আগাছা বেছে ফেলুন । জমি সমতল করে নিন ।
৫। জমিতে ৯ মি. (২৭) দূরত্বে কোদাল দিয়ে ১ মি. চওড়া ও ১ মি গভীর করে গর্ত তৈরি করুন। গর্ত সপ্তাহকাল খোলা রেখে দিন। গর্তের তলায় ১০/১৫ সে.মি পুরু করে নারিকেলের ছোবড়া/তুষ বিছিয়ে দিন। এরপর প্রতি গর্তে ১৫ কেজি জৈব সার, ৪৫০ গ্রাম টিএসপি, ৩০ গ্রাম এমপি ও ৫ কেজি ছাই মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে রাখুন। গর্ত ভরাট করার সময় উপরের মাটি নিচে এবং নিচের মাটি উপরে দিন। এর ১০/১৫ দিন পর চারা রোপণ করে দিন ।
৬। রোপণের জন্য বীজতলা থেকে সুস্থ ও সতেজ, পাতা গাঢ় সবুজ, বোটা খাট ও প্রশস্ত এমন অঙ্কুরিত চারা নির্বাচন করুন । বীজতলা থেকে দুহাতে ধরে চারা সাবধানে তুলে আনুন । প্রতি গর্তের মাঝখানে বীজের পিঠের কিছু অংশ খোলা রেখে চারা পুতে দিন। চারা স্থানান্তরের জন্য ঝুড়ি ব্যবহার করুন। হাতে চেপে মাটি বসিয়ে দিন । একটি চারা পুঁতে রশি দিয়ে বেঁধে দিন। চারা বেড়া দিয়ে ঘিরে দিন । চারা লেগে না উঠা পর্যন্ত রসের অভাব হলে সপ্তাহে ঝাঝরি দিয়ে ২/১ টি সেচ দিন। রোপণের পর ছায়া দানের ব্যবস্থা করুন ।
৭ । চারা গাছের গোড়ায় আগাছা জন্মালে নিড়িয়ে তুলে ফেলুন। চারা বাড়ার সাথে নিড়ানি এলাকার পরিসরও বাড়ান । সেচের পর মাটিতে জো এলে মাটির চটা ভেঙে দিন। মাটি আলগা রাখুন। বয়স্ক গাছ মাঝে মাঝে নিড়িয়ে আগাছা মুক্ত করুন ।
৮। নারিকেলের চারা রোপণের পর প্রতি বছর ৫ কেজি জৈব সার, ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০০ গ্রাম টিএসপি ও ৫০০ গ্রাম এমপি সার প্রয়োগ করুন । ৫ বছর ও তদুর্ধ বয়স্ক গাছে ১০ কেজি জৈব সার, ইউরিয়া ৮৭০ গ্রাম, টিএসপি ৩২৫ গ্রাম ও এমপি ১.১৪ কেজি প্রয়োগ করুন ।
৯ । এসব সার বছরে দুই দফায় অর্ধেক বর্ষার আগে ও অর্ধেক বর্ষার পরে গাছে প্রয়োগ করুন। গাছের গোড়া (৪০-৬০ সে.মি বাদ রেখে) থেকে ১.০-১.৫ মি দূর পর্যন্ত (দুপুরে যতটুকু স্থানে রৌদ্রের ছায়া পড়ে) মাটি লাঙ্গাল/কোদাল দিয়ে আলগা করে সারগুলি ভালোভাবে মিশিয়ে দিন। সার প্রয়োগের পর গাছে পাবন/থালা সেচ দিন । চারা গাছে সপ্তাহে ঝাঝরি দিয়ে ২/১ টি সেচ দিন এবং বয়স্ক গাছে বর্ষার পরে ১০/১৫ দিন পরপর পাবন/থালা পদ্ধতিতে সেচ দিন। বর্ষায় নিকাশের ব্যবস্থা করুন।
১০ । মরা, রাগাক্রান্ত, ভেঙে যাওয়া ডালপালা কেটে ফেলুন। হলুদ হয়ে শুকিয়ে যাওয়া ডাল কেটে ফেলুন । বছরে ২/১ বার গাছ খুব সাবধানে পরিষ্কার করে দিন। শুষ্ক মৌসুমে মাটির রস সংরক্ষণ ও পরিবেশ ঠান্ডা রাখার জন্য গাছের গোড়ার চারদিকে যতদূর ছায়া পড়ে ততটুকু কচুরিপানা/নারিকেলের পাতা বা ছোবড়া দিয়ে ঢেকে দিন । বর্ষাকালে কোদাল দিয়ে গাছের গোড়ায় কিছু মাটি তুলে উঁচু করে দিন ।
১১ । গন্ডার পোকা দমনে পোকার গর্তে তার ঢুকিয়ে দিয়ে পোকা বের করে এনে মেরে ফেলুন। (২) আক্রান্ত মরা গাছ ধ্বংস করুন । (৩) সিরিঞ্জ দিয়ে (১ সিসি) কীটনাশক (ডায়জিনন/ মেটাসিসটক্স) গর্তে ঢুকিয়ে পোকা মারুন । (৪) আলকাতরা / তারপিন তেল/ কেরোসিন তেল গর্তে ঢুকিয়ে দিন । কাদা দ্বারা গর্তের মুখ বন্ধ করে রাখুন । (৫) বাগানে গোবর/আবর্জনা জমতে দিবেন না ।
১২। লাল পোকা উইভিল দমনে পঁচা খৈলের ফাদ পেতে পোকা ধরে মারার জন্য একটি খোলা পাত্রে পচা খৈল গর্তের মুখের কাছে রেখে দিন। পোকা বের হয়ে আসলে ধরে মেরে ফেলুন। ২/২০ গ্রাম সেভিন পাউডার ১ লিটার পানিতে গুলে সিরিঞ্জ দিয়ে গর্তে ঢুকিয়ে দিয়ে পোকা মেরে ফেলুন ।
১৩ । কালোমাথা শুয়া পোকা দমনে- (১) আক্রান্ত পাতা ধ্বংস করুন, (২) প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৪ চা চামচ ডায়াজিনন ৬০ তরল কীটনাশক গুলে গাছের পাতায় ভালোভাবে স্প্রে করে দিন ।
১৪ । উইপোকা দমনে প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৪/৫ চা চামচ ডায়াজিনন ৬০ তরল গুলে মাটি আলগা করে গাছের গোড়াসহ মাটিতে ভালোভাবে স্প্রে করে দিন ।
১৫ । ইদুর দমনে- (১) আশে-পাশে গর্ত থেকে ইঁদুর বের করে মেরে ফেলুন, (২) টিনের তৈরি প্রতিন্ধক তৈরি করে গাছের কাণ্ডে লাগিয়ে ইদুরের গাছে উঠা বন্ধ করে দিন ।
১৬ । কুঁড়ি পচা রোগ দমনে- (১) আক্রান্ত মরা গাছ ধ্বংস করে ফেলুন, (২) প্রাথমিক অবস্থায় প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৪০/৪৫ গ্রাম ডাইথেন-এম-৪৫/ কুপ্রাভিট পাউডার গুলে নিয়ে গাছ, পাতা, কুঁড়িতে ভালোভাবে স্প্রে করে দিন ।
১৭ । ফল পচা ও ভূয়ো নারিকেল দমনে- (১) প্রতি বছর নিয়মিত সার ব্যবহার করুন, (২) প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১ চা চামচ পানোফিক্স গুলে গাছে ভালোভাবে স্প্রে করে দিন ।
১৮ । পাতায় দাগ দমনে-১৬ (২) নং অনুরূপ ব্যবস্থা নিন ।
১৯ । ছোট পাতা রোগ দমনে নিয়মিত ও পরিমিত সেচ সার প্রয়োগ করুন ।
২০ । কাণ্ডের রস ঝরা রোগ দমনে ক্ষতস্থান বেছে পরিষ্কার করে আলকাতরা / বোর্দোপেষ্ট লাগিয়ে দিন ।
২১ । শিকড় পচা রোগ দমনে (১) নিয়মিত ও পরিমিত সেচ সার প্রয়োগ করুন এবং নিকাশের ব্যবস্থা নিন, (২) গাছের গোড়া থেকে কিছু মাটি সরিয়ে ১৬ (২) এর অনুরূপভাবে প্রে করুন ।
২২ । ডাব হিসেবে ব্যবহারের জন্য কচি ফল আরোলা দা দিয়ে কেটে সংগ্রহ করুন। এছাড়া সম্পূর্ণ পরিপক্ক ঝুনা নারিকেল সংগ্রহ করুন। সংগৃহীত ফল ভাল-মন্দ, ছাট-বড় বাছাই করে নিন । নারিকেল তৈল/কাপরা করে সংরক্ষণ করতে পারেন । এছাড়া ঝুনা নারিকেল ঘরে সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন বহুদিন ।
সতর্কতা
১। বীজের মুখের খোসাটি সরিয়ে ফেলা কর্তব্য । তাতে গজানো সহজ হয় ।
২। পাঁচ মাস পরে না গজানো চারা বাতিল করে নতুন বীজ লাগানো ভালো ।
৩। রোপণের এক বছর পর যদি কোন চারা না বাড়ে তবে তা তুলে ফেলে নতুন চারা রোপণ করা উচিত।
৪ । অন্য সব পরিচর্যা ঠিক থাকলেও (সেচ / সার কীট ও রোগ দমন শুধু পরাগায়ণের অভাবেও ফল ঝরে পড়তে পারে।
৫। গল্ডার ও লাল পোকা থেকে সতর্ক থাকতে হবে ।
প্রাসঙ্গিক তথ্য
ফসলের নানাবিধ রোগের লক্ষণ প্রতিদিনই আমাদের দৃষ্টিগাচের হয় । এই লক্ষণগুলো প্রকাশ পায় গাছ ও রোগ উৎপাদকের মধ্যে অবিরাম মিথষ্ক্রিয়ার ফলে যতক্ষণ রোগে গাছটি মরে না যায় বা গাছের প্রতিক্রিয়ার ফলে রোগ উৎপাদক নিষ্ক্রিয় না হয়ে পড়ে ততক্ষণ উভয়ের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া চলতে থাকে এবং রোগের বিভিন্ন লক্ষণ ক্রমান্বয়ে প্রকাশ পেতে থাকে ।
প্রয়োজনীয় উপকরণ
আক্রান্ত ফল গাছ ও ফল, ভাসকুলাম, মাটি খোড়ার যন্ত্র, ডালপালা ছাঁটাই এর কাঁচি, চোষ কাগজ বা খবরের কাগজ, ছোট করাত, হালকা প্রেস, হারবেরিয়াম শিট, ছোট আকারের কাগজের বাক্স, আঠা, গামটেপ, লেবেল, নোটবুক, স্টেলোপেন, পেনসিল, পারমানেন্ট কালি, নমুনা সংরক্ষণের বিভিন্ন আধার, রোগ শনাক্তকরণের বিভিন্ন পুস্তক, ছবি, চার্ট ইত্যাদি ।
কাজের ধাপ
১। নমুনার জন্য সর্বদা সদ্য আক্রান্ত বা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত গাছ বা তার অংশ বিশেষ ও যফল সংগ্রহ করতে হবে।
২। রোগ বৃদির অবস্থায় রোগের লক্ষণ কেমন হয় তা দেখার জন্য রোগের বিভিন্ন অবস্থার একাধিক নমুনা সংগ্রহ করতে হবে।
৩ । গাছের পাতা, শিকড়, কান্ড প্রভৃতির নমুনা সংগ্রহ করার সঙ্গে সঙ্গে চোষ কাগজ বা খবরের কাগজের মধ্যে নিয়ে হালকা প্রেসের মধ্যে চাপ দিয়ে রাখতে হবে ।
৪ । নমুনা বড় হলে তা সংগ্রহ করে ভেজা কাপড় বা কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে ভাসকুলামে রাখতে হবে ।
৫। ফল সংগ্রহ করে সেলােেফন ব্যাগে মুখ বন্ধ করে রাখতে হবে ।
৬ । বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করে ব্যবহারিক শ্রেণিকক্ষে নিয়ে আসতে হবে ।
৭। ব্যবহারিক শ্রেণিকক্ষে রোগ শনাক্ত করার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন পুস্তক, ম্যানুয়াল, আলোকচিত্র ও ছবি এবং হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত ও ভেজা নমুনার লক্ষণ মিলিয়ে রোগ সনাক্ত করতে হবে।
৮। সংগ্রহের পরপরই রোগ শনাক্ত করতে না পারলে নমুনাকে ফ্রিজে বা অন্য কোন ঠান্ডাস্থানে রেখে দিয়ে এবং সময় ও সুবিধা মতো শনাক্ত করার চেষ্টা করতে হবে ।
৯ । বিভিন্ন পুস্তক, ছবি, হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত নমুনার সঙ্গে মিলিয়ে রোগকে নিশ্চিত ভাবে সনাক্ত করতে না পারলে নমুনার রোগাগ্রত অংশ হতে প্যাথজেন বা রোগের জন্য দায়ী জীবাণুকে পৃথক করে বা আবাদ মাধ্যমে চাষ করে মাণক্রোস্কোপে দেখে জীবাণু সনাক্ত করতে হবে।
১০ । পুস্তক, ছবি, হারবেরিয়াম শিট ও কাচের আধারে রক্ষিত নমুনার বৈশিষ্ট্য ও জীবাণুর বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে রোগকে নিশ্চিতভাবে শনাক্ত করতে হবে ।
১১ । ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য শনাক্তকৃত রোগের নমুনা সমূহ তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী শুকিয়ে হারবেরিয়াম শিটে অথবা ভিজা অবস্থায় বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের দ্রবনে ডুবিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে ।
প্রাসঙ্গিক তথ্য
ব্যবহারিক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের অনুশীলনের জন্য সংরক্ষিত নমুনা অত্যান্ত কাজে লাগে। এ কারণে বিশ্বের বহু দেশে গাছ গাছড়া ও রোগাক্রান্ত গাছের নমুনার জাদুঘর (Plant desease her barium) প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। ফলের বিভিন্ন রোগের লক্ষণ সনাক্তকরণের একটি সহজ উপায় হলো হারবেরিয়াম তৈরিকরণ । হারবেরিয়ামে ফলের বিভিন্ন রোগের শুষ্ক নমুনা সংগৃহীত থাকে এবং তারপাশে রোগের লক্ষণসহ শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য দেয়া থাকে । এতে বিভিন্ন ফলের রোগের নাম জানা, চেনা ও শনাক্তকরণ অতি সহজে এবং অল্প সময়ে সম্ভব হয় ।
প্রয়োজনীয় উপকরণ
১। রোগাক্রান্ত গাছ, ফুল ও ফলের নমুনা
২। একটি ভারি ও মজবুত প্রেস অথবা চোষ কাগজ বা খবরের কাগজ
৩। হারবেরিয়াম শিট বা নমুনা স্থাপনের কাগজ
৪ । কাগজের ছোটবাক্স, আঠা, গামটেপ, তুঁতে বা মারকিউরিক ক্লোরাইড
৫। লেবেল, কলম, সুতা ইত্যাদি ।
কাজের ধাপ
১। বাগান হতে রোগাক্রান্ত নমুনা ডাটা ও পাতাসহ ফুল সিকেচার বা চাকু দ্বারা কেটে সংগ্রহ করতে হবে।
২। সংগৃহীত নমুনাগুলো প্রথমে একটি চোষ কাগজে রেখে তার উপর আর একটি চোষ কাগজ রাখতে হবে । এ কাগজের ওপর আবার একটি নমুনা রেখে আগের মত তার উপর একটি কাগজ থাপন করতে হবে। এভাবে পর রাখতে রাখতে একটি নমুনার গাদা তৈরি হবে। এখন গাদাটিকে একটি ভারি প্রেসের দুডালার মধ্যে রেখে যথাসম্ভব জোরে চাপ দিয়ে ফিতা আটকিয়ে রাখতে হবে। প্রেস না থাকলে বিছানার তোষকের নিচে সমাণ স্থানে রাখতে হবে।
৩। প্রেসের মধ্যে ২৪ ঘণ্টা রাখার পর নমুনাগুলো বের করে শুকাতে হবে । আবার বিছানার তোষেকের নিচে তুলে কয়েক দিন রেখে নমুনাগুলো শুকাতে হবে ।
৪ । নমুনা গুলো শুকানোর কয়েক দিন পর চোষ কাগজ বা খবরের কাগজের মধ্য হতে বের করে নিতে হবে।
৫ । এরপর নমুনাগুলো সংগ্রহ করে (শুকানোর পর) হারবেরিয়াম সিটে স্থাপন করতে হবে ।
৬। নমুনা স্থাপনের জন্য ২৯০৪২ সে.মি. সাইজের হারবেরিয়াম সিট ব্যবহার করতে হবে। সিটে নমুনা আটকানোর জন্য আঠা, গামটেপ, সূতা প্রভৃতি ব্যবহার করতে হবে । আঠা লাগানোর জন্য প্রথমে একটি গাস শিটের উপর পাতলা করে আঠা লাগান এবং তার উপর নমুনাকে কিছু উপর থেকে হালকাভাবে ফেলতে হবে । এর ফলে নমুনার নিচের দিকে আঁঠা লেগে যাবে ও পরে হারবেরিয়াম সিটে রাখলে আটকে যাবে। আঠা লাগানো অবস্থায় সিটে স্থাপন করার পর নমুনা কখনও নড়াচড়া করানো যাবে না। কারণ, তাতে নমুনার নিচের আঁঠা সিটের বিভিন্ন স্থানে লেগে সিটকে নষ্ট করে ফেলবে ।
নমুনা সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় তথ্য সকলের অবগতির জন্য তার পাশে সিটের এক কোনায় নমুনার সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ একটি লেবেল নিম্নোক্তভাবে লিখতে হবে ।
সংগ্রহ নম্বর-
প্রতিষ্ঠান-
রোগের নাম-
পোষাকের নাম-
পরজীবী-
প্রাপ্তিস্থান -
স্থানীয় অবস্থা-
অনুসন্ধানকারী-
তারিখ-
প্রাসঙ্গিক তথ্য
১। যে ফসলের ক্ষেতে কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে সে ফসল অনুযায়ী স্প্রে মেশিন নির্বাচন করতে হবে । যেমন মাঠ ফসলের জন্য হ্যান্ড প্রেয়ার, শক্তি চালিত ন্যাপসেক স্প্রেয়ার, ব্রোয়ার এবং বৃক্ষজাতীয় ফসল বা ফল বাগানের জন্য ফুট পাম্প ইত্যাদি ।
২। আক্রমণকারী পোকার ধরন ও ফসল ক্ষেতের আকার ও ফসলের প্রকৃতি অন্যায়ী প্রেমেশিন নির্বাচন করতে হবে । ছোট বাগান হলে পদপৃষ্ঠ স্প্রেয়ার (Foot pump) বড় বাগান হলে ব্রোয়ার ফুট পাম্প ইত্যাদি ।
৩। কীটনাশকের গঠনের ওপর ভিত্তি করেও সিঞ্চন যন্ত্র নির্বাচন করতে হবে। যেমন-পাউডার জাতীয় কীটনাশকের জন্য ডাষ্টার এবং তরল কীটনাশকের জন্য হ্যান্ড প্রেয়ার, পাওয়ার প্রেয়ার, বোয়ার ফুট পাম্প ইত্যাদি ।
প্রয়োজনীয় উপকরণ
১। হ্যান্ড স্পেয়ার/পাওয়ার প্রেয়ার/পদ পৃষ্ঠপ্রেয়ার
২। কীটনাশক
৩ । নাড়ন কাঠি
৪ । কীটনাশক প্রতিরোধক পাষোক
৫ । ফসলের ক্ষেত্র (শস্য মাঠফল/ বাগান)
৬। সাদা কাগজ, পেনসিল, রাবার ইত্যাদি
কাজের ধারা
১। ব্যবহারের জন্য নির্বাচিত সিঞ্চন যন্ত্রটি ব্যবহারের উপযোগী আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে । প্রধানত: নিম্নলিখিত বিষয় পরীক্ষা করার প্রয়োজন হবে । (ক) পাম্প করলে যন্ত্রে বাতাস আটকে থাকে কিনা (খ) নজেল দিয়ে পানি সঠিকভাবে নির্গমন হয় কিনা
২। এখন ব্যবহার উপযোগী সিঞ্চন যত্রটির চারভাগের একভাগ পরিষ্কার পানি দ্বারা ভর্তি করতে হবে ।
৩। তারপর সিঞ্চন যন্ত্রে একবারে যতটুকু নির্বাচিত কীটনাশক প্রয়োজন তার চারভাগের একভাগ সিঞ্চন যনেত্রর পানির মধ্যে ঢালতে হবে এবং নাড়ন কাঠি দ্বারা ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মিশাতে হবে।
৪ । এরপর আবার চার ভাগের একভাগ পানি ও পূর্বের সমপরিমাণ কীটনাশক মেশিনে ঢালতে হবে এবং নাড়ন কাঠি দ্বারা নাড়াচাড়া করে ভালোভাবে মিশাতে হবে ।
৫ । এবার সিঞ্চন যনেত্র নির্ধারিত দাগ পর্যন্ত সর্বশেষ পানিটুকু ও কীটনাশকটুকু ঢালতে হবে এবং নাড়ন কাঠি দ্বারা ভালোভাবে মিশাতে হবে ।
৬ । অতঃপর কীটনাশক ঢালার পথ অর্থাৎ সিঞ্চন যন্ত্রের মুখ ভালোভাবে বন্ধ করতে হবে ।
৭ । এখন হাতলের সাহায্যে পিস্টনের উঠানামা করিয়ে প্রয়োজন মাফিক পাম্প করতে হবে/ফুট পাম্পের ক্ষেত্রে পায়ের সাহায্যে চাপ দিয়ে পাম্প করতে হবে । যতক্ষণ পর্যন্ত পাম্প করতে খুব জোর না লাগে ততক্ষণ পর্যন্ত পাম্প করতে হবে ।
৮ । এবার কীটনাশক প্রতিরোধক পোকাক পরিধান করতে হবে এবং সিঞ্চন যন্ত্রটি কাঁধে তুলে নিতে হবে ।
৯ । যে জমিতে কীটনাশক ছিটাতে হবে সে জমির একপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়াতে হবে । ঘাসের টুকরো, পাতা উড়িয়ে বা ধুয়ার সাহায্যে বায়ু প্রবাহের দিক জেনে নিতে হবে।
১০। এখন সিঞ্চন যন্ত্রের ট্রিগারে চাপ দিয়ে বাতাসের অনুকূলে সমগতিতে এগিয়ে যেতে হবে এবং স্প্রে করতে হবে । সতর্ক থাকতে হবে যাতে কীটনাশক গায়ে না পড়ে ।
১১ । এভাবে জমি/বাগানের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে পৌছানারে পর প্রথম বার স্প্রে কৃত স্থান বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যাস মোতাবেক দূরত্ব নিয়ে আবার জমির পূর্বের প্রান্তের দিকে ফিরে আসতে হবে। এভাবে জমিতে প্রে শেষ করতে হবে । সিঞ্চন যন্ত্রের মিশ্রণ শেষ হয়ে গেলে পূর্বের ন্যায় পুনরায় মিশ্রণ তৈরি করে যন্ত্রটি ভরে নিতে হবে এবং পূর্বের পদ্ধতিতে জমিতে স্প্রে করা শেষ করতে হবে।
১২ । পাতার আক্রমণকারী পোকার জন্য গাছের উপর এবং কাণ্ডে বা নিচের দিকে আক্রমণকারী পোকার জন্য পাতার নিচে স্প্রে করতে হবে।
১৩। ফলের বাগানে/উচু বৃক্ষের ক্ষেত্রে পদপৃষ্ঠ প্রেয়ার ব্যবহারের সময় প্রয়োজনীয় কীটনাশক ও পানি অনুমোদিত মাত্রায় পৃথক কন্টেইনার বালতিতে মিশিয়ে নিতে হবে এবং প্রেয়ারের সাকসন পাইপের নিম্ন প্রান্ত কনটেইনার বা বালতির ভেতর মিশ্রিত কীটনাশকে ডুবিয়ে প্রের কাজ সম্পন্ন করতে হবে ।
সাবধানতা
১। সিঞ্চন যন্ত্র ব্যবহারের কলাকৌশল অনুশীলন কালে কোনরূপ ধূমপান করা যাবে না বা অন্য কোন খাদ্য গ্রহণ করা যাবে না ।
২। কলাকৌশল অনুশীলনের পর হাত ভালোভাবে সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে ।
৩। স্প্রে কার্যক্রম শেষে পরিধেয় সকল কাপড় এবং স্প্রে মেশিন ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে ।
আরও দেখুন...
Promotion